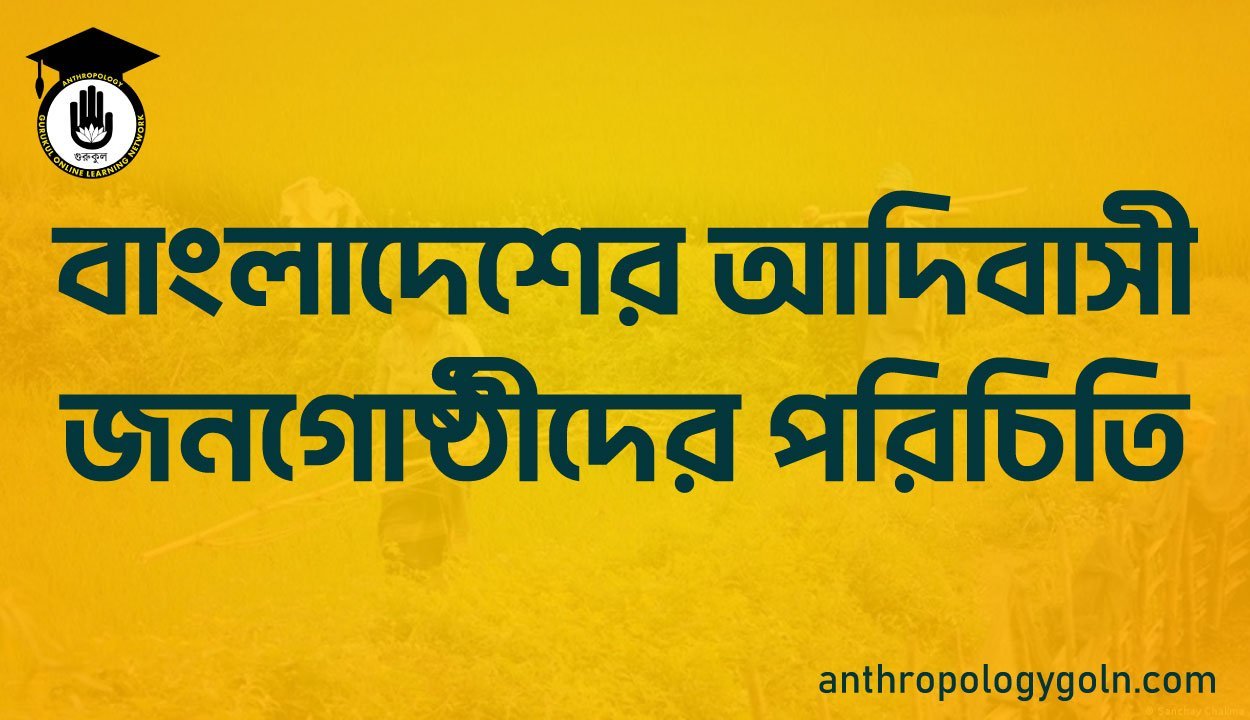আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি । বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট কিন্তু জনবহুল রাষ্ট্র। বাংলাদেশ ভূখন্ডের জনসংখ্যার অধিকাংশ হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহৎ নৃগোষ্ঠী বাঙালি। এছাড়া অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ; সমগ্র জনগোষ্ঠির প্রায় এক শতাংশের মতো (১.১১%) ।
বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি

‘আদিবাসী’ পরিচয়ের তাৎপর্য
বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ মানুষ বাঙালী হিসাবে পরিচিতি, তবে বাঙালীদের পাশাপাশি এদেশে বেশ কিছু ক্ষুদ্র জাতিসত্তারও (ethnic minority) বসবাস রয়েছে যেমন চাকমা, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি – যারা সচরাচর উপজাতীয় বা আদিবাসী হিসাবে পরিচিত। এইসব জনগোষ্ঠীর পরিচয় সম্পর্কে সাধারণ কোন আলোচনায় যেতে হলে সর্বাগ্রে যে প্রশ্নটা চলে আসে তা হল, তাদেরকে উপজাতীয়, আদিবাসী বা অন্য কোন নামে অভিহিত করার তাৎপর্য কি?
বাংলাদেশে ‘উপজাতীয়” বা ‘আদিবাসী’ হিসাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীরা বাঙালীদের তুলনায় সংখ্যায় খুবই অল্প, তবে সংখ্যাল্পতার কারণে যে তাদের ক্ষেত্রে এই পরিচয়গুলি ব্যবহার করা হয়, তা বলা যায় না। বাংলায় ‘উপজাতি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় ইংরেজী ‘tribe’-এর প্রতিশব্দ হিসাবে। নৃবিজ্ঞানে ‘tribe’ ধারণা ব্যবহৃত হয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ও প্রসারের পূর্বে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে সংগঠিত বিশেষ ধরনের সমাজকে বোঝাতে।
লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান বিশ্বে সকল জনগোষ্ঠীই কোন না কোন রাষ্ট্রের আওতায় বাস করে, কাজেই এই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত বিশেষ অর্থে কোন জনগোষ্ঠীকে ‘উপজাতীয়’ হিসাবে চিহ্নিত করা সমস্যাজনক। কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপীয়রা তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহ বিস্তারের সময় পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ছিল যারা নিজেরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত ছিল না বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত বৃহত্তর কোন সমাজের অংশ ছিল না।
এ ধরনের জনগোষ্ঠীই ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে ‘উপজাতীয়’ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। তবে ‘উপজাতীয়’ হিসাবে চিহ্নিত সকল জনগোষ্ঠীই প্রকৃতপক্ষে প্রাক- রাষ্ট্রীয় স্তরের সমাজ ছিল কি না, এ নিয়ে খোদ নৃবিজ্ঞানেই বিতর্ক রয়েছে।
অন্যদিকে ঔপনিবেশিক বা উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আওতায় চলে আসার পরে এসব জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিতভাবে আর সে অর্থে ‘উপজাতীয়’ সমাজ বলা যায় না। এ ধরনের তাত্ত্বিক সমস্যার পাশাপাশি প্রচলিত ব্যবহারে ‘উপজাতীয়’ শব্দের নেতিবাচক ব্যঞ্জনাও তৈরী হয়েছে। ‘উপজাতীয়’ হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীদের সচরাচর ‘আদিম’ ‘বর্বর’ ইত্যাদি আখ্যায়ও ভূষিত করা হয়েছে। এসব কারণে ‘উপজাতীয়’ পরিচয়টা অনেকের কাছে এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে এই নামে পরিচিত মানুষদের কাছে।
বাংলায় অবশ্য আদিবাসী শব্দটিরও একই ধরনের নেতিবাচক ব্যঞ্জনা রয়েছে। তথাপি সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ইংরেজী indigenous people-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর একটা কারণ হল, ‘উপজাতীয়’ হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীদের পক্ষ থেকেই এই দাবী উঠেছে যে তাদেরকে “আদিবাসী’ (indigenous people) হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।
এই দাবীর তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের দেখতে হবে আন্তর্জাতিক পরিসরে indigenous people বলতে কি বোঝানো হচ্ছে। আভিধানিকভাবে ‘indigenous’ কথাটির অর্থ হচ্ছে স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত। কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাসরত একাধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীকে ‘আদিবাসী’ হিসাবে শনাক্ত করার অর্থ দাঁড়ায় এই, তারা জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে সেখানকার প্রাচীনতম অধিবাসীদের উত্তরসূরী। বলা বাহুল্য, এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ স্থান ও কালের সীমানা কিভাবে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করছে কোন্ প্রেক্ষিতে কাদের আমরা ‘আদিবাসী’ বলতে পারি।
সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ‘indigenous people’-এর ধারণা ব্যবহার করা হচ্ছে মূলতঃ বিগত পাঁচশ বছরের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়েই। উত্তর ও দক্ষিণআমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মত জায়গায় সেখানকার মূল অধিবাসীদের | নিধন, উচ্ছেদ বা সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংস করে কিভাবে ইউরোপীয়রা এই ভূখন্ডগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছিল, সে ইতিহাস আপনার কমবেশী জানা আছে নিশ্চয়।

এসব জায়গার আদি অধিবাসীদের ‘উত্তরসূরী যেসব জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখে টিকে আছে, তাদেরকে সাধারণভাবে বোঝানোর জন্যই সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ‘indigenous people’ ধারণার ব্যবহার শুরু হয়। এ ধরনের জনগোষ্ঠীদের ঐতিহাসিক বঞ্চনার প্রেক্ষিতে তাদের অনেক দাবীকে আইনগত অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগও জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে ‘উপজাতীয়’ হিসাবে অভিহিত জনগোষ্ঠীরা ‘আদিবাসী’ পরিচয়ের স্বীকৃতি চাচ্ছে।
বাংলাদেশসহ আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশের সরকার অবশ্য নিজেদের দেশে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীকে indigenous people হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আসছে। এর একটা কারণ হল, বর্তমানে সাধারণভাবে এসব দেশের ক্ষমতাসীন শ্রেণীর মানুষরাও নিজ নিজ দেশে দীর্ঘকাল যাবত বসবাসরত জনগোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত। একই দেশে দীর্ঘকাল যাবত বাস করে আসা জনগোষ্ঠীদের মধ্যে কারা সেদেশের আদি বাসিন্দাদের উত্তরসূরী আর কারা নয়, আক্ষরিক অর্থে তা নির্ধারণ করা অনেকক্ষেত্রেই অসম্ভব বা দুঃসাধ্য।
তবে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ‘জাতীয়তা’র বিশেষ কোন ধারণার ভিত্তিতে, যা অনেকক্ষেত্রে একই দেশের সকল জনগোষ্ঠীর পরিচয়কে সমানভাবে ধারণ করতে পারেনি। অধিকন্তু, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়া এসব নবীন রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী ও সংখ্যাগুরু জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেরাই নিজ নিজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ অব্যাহত রেখেছে।
কাজেই এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মত জায়গায়ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে ‘উপজাতীয়’ বা অনুরূপ কোন বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত হয়ে আসা বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে indigenous people হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা দরকার বলে অনেকে মনে করেন।
উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত Indigenous People-এর ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার | আগে থেকেই বাংলা ভাষায় ‘আদিবাসী” শব্দটির চল ছিল। যেমন, পাকিস্তান আমলে লেখা আবদুস সাত্তারের ‘আরণ্য জনপদে’ নামক গ্রন্থে চাকমা, সাঁওতাল, গারো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে ‘আদিবাসী’ |হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও ‘আদিবাসীরা কেউ এদেশের ভূমিজ সন্তান নয়’–এ ধরনের | বিভ্রান্তিকর বক্তব্যও একই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে ‘আদিম’ অর্থেই যে ‘আদিবাসী’ কথাটি ব্যবহৃত হয়, তা বলা বাহুল্য।
তবে বাংলাদেশে ‘আদিবাসী’ বা ‘উপজাতীয়’ হিসাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মত দেশের এমন কিছু বিশেষ অঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবত বাস করে আসছে যেসব জায়গায় বাঙালী জনবসতি গড়ে উঠেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে। এসব ক্ষেত্রে ‘আদিবাসী’রা বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠীর চাপের মুখে অনেক ক্ষেত্রেই বহুমাত্রিক অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হয়েছে, যে সংকট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।
এই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিকভাবে indigenous people হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে শামিল হওয়ার লক্ষ্যেই বাংলাদেশে ‘আদিবাসী” শব্দটির পুরানো নেতিবাচক ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও indigenous people এর সমার্থক হিসাবে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। (বাংলাসহ উপমহাদেশের একাধিক ভাষায় ‘আদিবাসী’ শব্দটির প্রচলন শুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ ইংরেজী aboriginal-এর প্রতিশব্দ হিসাবে, যা ব্যুৎপত্তিগতভাবে indigenous-এর সমার্থক, তবে অপেক্ষাকৃত আগে থেকে প্রচলিত এই শব্দটি বর্তমানে প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়।)
উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ‘আদিবাসী’ পরিচয়ের কোন সর্বজনস্বীকৃত বা সরকারী সংজ্ঞা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নেই। সে যাই হোক, সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা রেওয়াজ অনুসারে বাংলাদেশে ‘উপজাতীয়’, ‘সংখ্যালঘু জাতিসত্তা’ প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত জনগোষ্ঠীদের সাধারণভাবে বোঝানোর জন্য এই ইউনিটে আমরা ‘আদিবাসী’ কথাটা ব্যবহার করছি।
বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের তালিকা, সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান
বাংলাদেশে মোট কয়টি আদিবাসী জাতিসত্তা রয়েছে, তার কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায় না। সরকারীভাবে অবশ্য ‘আদিবাসী’র পরিবর্তে ‘উপজাতীয়’ পরিচয়ের আওতায় কিছু পরিসংখ্যান রয়েছে। যেমন, ১৯৯১ সালের আদমশুমারী প্রতিবেদনে ২৭টি ‘উপজাতীয়’ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের মোট জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছিল ১২,০৫,৯৭৮। তবে উক্ত প্রতিবেদনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে তালিকা দেওয়া রয়েছে, তা অসম্পূর্ণ এবং কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ।
এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী জরিপের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে ‘উপজাতীয়’দের মোট জনসংখ্যা সরকারী হিসাবের চাইতে বেশী হবে। আর সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন হিসাব মিলিয়ে দেখলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে মোট ৪৫টির মত আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোন জরিপ ছাড়া নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের কোন জরিপ চালানোর ক্ষেত্রে কোন জনগোষ্ঠীকে ‘উপজাতীয়’ বা ‘আদিবাসী’ হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কি মাপকাঠি ব্যবহার করা হবে, তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে জরিপের ফলাফল।
এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে–যেমন, বর্মন, বেদে প্রভৃতি–যারা ক্ষেত্রবিশেষে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের অংশ হিসাবে পরিচিত বা পরিচিত হতে আগ্রহী, আবার ক্ষেত্রবিশেষে তাদের আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে বা করা হয়ে থাকে। আবার এমনও দেখা গেছে যে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটি জনগোষ্ঠীকে একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের দুটি আলাদা ভাগ হিসাবে কেউ কেউ দেখছেন, আবার কেউ কেউ তাদেরকে আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করছেন।
যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক সময় তঞ্চঙ্গ্যাদের চাকমাদের একটি শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, তবে বর্তমানে তারা একটি আলাদা ‘উপজাতি’ হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত। স্পষ্টতই, বাংলাদেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা কয়টি, তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে।
বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তবে সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেই তাদের ঘনত্ব বেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য পাহাড়ি এলাকা, গড়াঞ্চল, উপকুলীয় এলাকা ও উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের বসবাস রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বর্তমানে মোট ১১টি ‘উপজাতীয়’ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকৃত, যেগুলি হল (নামের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে), খিয়াং, খুমি, চাক, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাঙ্খো, বম, মারমা, ম্রো ও লুসাই।
ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অংশবিশেষ অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, রাজবাড়ি প্রভৃতি জেলায়ও রয়েছে। এরকম আরো কিছু জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি একাধিক বিভাগ জুড়ে রয়েছে। যেমন, রাখাইনদের বসবাস রয়েছে কক্সবাজার, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলাসমূহে।
গারো ও হাজংরা ঢাকা ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে। গারো ও হাজংরা ছাড়াও ঢাকা বিভাগের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও অন্যান্য জেলায় কোচ, ডালু, বর্মন (ক্ষত্রিয়), বানাই, রাজবংশী, হদি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী, এবং সিলেট বিভাগে খাসিয়া, পাত্র, মণিপুরী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে (রাজশাহী বিভাগ) উরাও, কোল, পাহাড়িয়া, মালো, মাহাতো, মাহালী, মুন্ডা, রাজবংশী, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী রয়েছে। জনসংখ্যার বিচারে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তো বটেই, সমগ্র বাংলাদেশেরও বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ১৯৯১ সালের আদমশুমারীতে যাদের সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষের উপরে।
উক্ত আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমাদের পরেই রয়েছে যথাক্রমে সাঁওতাল (দুই লক্ষাধিক), মারমা (এক লক্ষ সাতান্ন হাজার), ত্রিপুরা (একাশি হাজারের উপরে), গারো (চৌষট্টি হাজারের উপরে), মণিপুরী (প্রায় পঁচিশ হাজার), ম্রো (বাইশ হাজারের উপরে, যারা ‘মুরং” নামেও পরিচিত), তঞ্চঙ্গ্যা (প্রায় বাইশ হাজার), রাখাইন (সতের হাজার), কোচ (সাড়ে ষোল হাজার), বম (সাড়ে তের হাজার), খাসিয়া (বার হাজারের উপরে), হাজং (সড়ে এগার হাজার), উরাও (আট হাজারের উপরে) রাজবংশী (সাড়ে সাত হাজার), মাহাতো (সাড়ে তিন হাজার), পাঙ্খো (তিন হাজারের বেশী)।
আদমশুমারীতে খিয়াং, চাক, মুন্ডা, খুমি, লুসাই প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর তালিকাও রয়েছে যাদের জনসংখ্যা দুই-আড়াই হাজারের মত বা আরো কম। এছাড়া ‘বুনো” ও ‘উরুয়া’ নামে দুইটি জনগোষ্ঠীর উল্লেখও রয়েছে যাদের সম্পর্কে অন্যত্র তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।
নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ না করে ‘অন্যান্য’ হিসাবে আড়াই লাখের বেশী উপজাতীয়ের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে থাকতে পারে কোল, খন্ড, খারিয়া, ডালু, তুরী, পাহান, বানাই, সিং, পাত্র, বর্মন, বাগদি, বেদিয়া, মালো, মাহালি, মুরিয়ার, মুসহর, রাই, রাজুয়াড়, হদি, হো প্রভৃতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন বইপুস্তকে যাদের উল্লেখ রয়েছে, যদিও তাদের সকলের পরিচয় বা সংখ্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দুর্লভ।
ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি
বাংলাদেশের লিখিত ইতিহাসে এদেশের আদিবাসীদের প্রসঙ্গ তেমন একটা জায়গা পায়নি, যেটুকু পেয়েছে তাও অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বা অস্পষ্ট ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সামন্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন- শোষণের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এদেশের ইতিহাসকে যখন ‘বাঙালীর হাজার বছরের ইতিহাসের আলোকে দেখা হয়, তখন সেখানে আদিবাসীরা আড়ালে চলে যায়।
একইভাবে বাংলা ভাষা, বাঙালী সংস্কৃতি বা বাঙালী জনসমষ্টির অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের পূর্বসূরীদের কি অবদান ছিল, সে প্রসঙ্গ তেমন আলোচিত হয় না। সাধারণভাবে বলা যায়, গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালীদের দৃষ্টিকোণ থেকে আদিবাসীদের যে ভিন্নতাগুলো নজর কাড়ে – চেহারার পার্থক্য থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য – সেগুলোর উল্লেখ পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন বইপত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাঙালী ও আদিবাসীদের মধ্যেকার গভীরতর সম্পর্ক ও যোগসূত্রসমূহ দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।
উদাহরণ হিসাবে এখানে ভাষার প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাই বাংলা থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত। শব্দভান্ডারের তুলনামূলক অধ্যয়নের ভিত্তিতে একই উৎস থেকে উদ্ভূত বলে বিবেচিত ভাষাসমূহকে একই ‘ভাষা পরিবার’-এর অন্তর্ভূক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়।

সে হিসাবে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষাসমূহকে চারটি ভাষাপরিবারে শ্রেণীভুক্ত করা যায়, সেগুলো হল: ইন্দো-ইউরোপীয় বা ‘আর্য’, দ্রাবিড়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও তিব্বতী- বর্মী। ১) আর্য: বাংলাসহ অহমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় নামে পরিচিত ভাষা | পরিবারের অন্তর্গত হিসাবে গণ্য করা হয়, যা ‘আর্য” নামেও পরিচিত।
বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে চাকমা, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহকে ‘আর্য’ পরিবারের অন্তর্গত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২) দ্রাবিড়: তামিল, মালয়ালম, তেলুগু প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাকে ‘দ্রাবিড়’ পরিবার-ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে ওরাঁও ও পাহাড়িয়াদের ভাষাসমূহ এই পরিবারের অন্তর্গত।

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ সূচিপত্র:
বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ নিয়ে সকল আর্টিকেল এর লিংক এইখানে পেয়ে যাবেন যা প্রতিনিয়ত আপডেট হতে থাকে। বাংলাদেশে উপজাতীয় বা আদিবাসী নামে পরিচিত বেশ কিছু ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে যারা দীর্ঘকাল যাবত এ ভূখন্ডে বসবাস করে এসেছে। এদেশের ইতিহাসে বাঙালীদের পাশাপাশি গারো, সাঁওতাল, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের ঐতিহ্য মিশে আছে।
প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা তথা বাঙালী সংস্কৃতি এবং বাঙালী জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পেছনে রয়েছে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পূর্বসূরীদের অনেকের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সংশ্লেষণ। তবে সমকালীন প্রেক্ষিতে গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের সংস্কৃতিকে ‘জাতীয় মূলধারা’র বাইরে বলেই গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি
আদিবাসী পরিচয়ের তাৎপর্য
বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের তালিকা, সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান
ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি
বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি অধ্যায়ের সারাংশ
চাকমা জনগোষ্ঠী
চাকমাদের সাধারণ পরিচিতি
চাকমাদের ইতিহাস
চাকমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি
চাকমাদের সমাজ কাঠামো
চাকমা জনগোষ্ঠী অধ্যায়ের সারাংশ

গারো জনগোষ্ঠী
গারো জনগোষ্ঠী পরিচিতি
গারোদের ইতিহাস
মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি ব্যবস্থা
সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক অবস্থা
গারো জনগোষ্ঠী অধ্যায়ের সারাংশ
সাঁওতাল জনগোষ্ঠী
সাঁওতাল জনগোষ্ঠী পরিচিতি
ভাষা ও সংস্কৃতি: বাঙালীদের সাথে যোগসূত্র
বিদ্রোহ ও সংগ্রামের ইতিহাস
বাংলাদেশের সাঁওতালদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা
সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অধ্যায়ের সারাংশ

রাখাইন জনগোষ্ঠী
রাখাইন জনগোষ্ঠী সাধারণ পরিচিতি
রাখাইন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস
আর্থসামাজিক অবস্থান
রাখাইন জনগোষ্ঠী অধ্যায়ের সারাংশ

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি অধ্যায়ের সারাংশ – যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি এর অর্ন্তভুক্ত, ‘আদিবাসী’ পরিচয়ের কোন সর্বজনস্বীকৃত বা সরকারী সংজ্ঞা বাংলাদেশে নেই, তবে সাম্প্রতিককালে এদেশে ‘উপজাতীয়’, ‘সংখ্যালঘু জাতিসত্তা’ প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত জনগোষ্ঠীদের সাধারণভাবে বোঝানোর জন্য ‘আদিবাসী’ কথাটা ব্যবহারের রেওয়াজ গড়ে উঠেছে।

সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন হিসাব মিলিয়ে দেখলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে মোট ৪৫টির মত আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে। বাংলা ভাষা তথা বাঙালী সংস্কৃতি এবং বাঙালী জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পেছনে রয়েছে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পূর্বসূরীদের অনেকের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সংশ্লেষণ।

সামন্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। এসব সত্ত্বেও অবশ্য বাংলাদেশের লিখিত ইতিহাসে এদেশের আদিবাসীদের প্রসঙ্গ তেমন একটা জায়গা পায় নি, যেটুকু পেয়েছে তাও অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বা অস্পষ্ট ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকতার পাশাপাশি এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা অর্থনৈতিকভাবেও প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে আদিবাসীরা ছিল ভূমির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার হরণের প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। আদিবাসীদের সম্পর্কে জানা এবং তাদের পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি শুধুমাত্র তাদে স্বার্থের বিষয় নয়, বরং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীর মূল্যায়নের জন্যও তা অপরিহার্য।
আরও দেখুনঃ