আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় আলেকজান্ডারের বিজয়ের তাৎপর্য। আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট ইতিহাসে এক বহুল আলোচিত নাম। সেই সুদূর গ্রিস থেকে একের পর এক দেশ জয় করে তাঁর বাহিনী চলে এসেছিল ভারত অবধি। পারস্যের কাছে তিনি পরিচিত ইস্কান্দার বাদশাহ হিসাবে আর ভারতবর্ষে ইস্কান্দারের অপভ্রংশ সেকান্দার বাদশাহ হিসাবেও বহুল পরিচিত তিনি। দুই সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেলেও আলেকজান্ডারকে নিয়ে বিশ্ববাসীর আগ্রহ একটুও কমেনি। আর কমবেই বা কেন? ৩২ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি জয় করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাম্রাজ্য।
আলেকজান্ডারের বিজয়ের তাৎপর্য
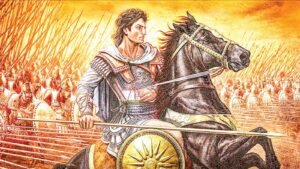
আলেকজান্ডারের বিজয়ের তাৎপর্য
পারস্য সাম্যজ্যের বিরুদ্ধে অলেকজাণ্ডারের সহজ বিজয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল পারসিকদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য ছিল বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত, আর তাদের মধ্যে কোনো ঐক্যবোধ ছিল না। পারসিক সেনাবাহিনীও ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ও উপজাতির লোক এবং ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে গঠিত। আলেকজাণ্ডারের সুসংগঠিত গ্রীক বাহিনীর সর্বাধুনিক রণকৌশলের কাছে তাই পারসিক বাহিনী সহজেই পরাস্ত হয়েছিল।
কিন্তু বাহুবলে পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাভূত করতে পারলেও আলেকজাণ্ডার কোন সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যবোধ ছিল না। তাই ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হওয়ামাত্র তাঁর সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের তিনজন প্রধান সেনাপতিই তাঁর সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন।
অবশ্য এ সকল ভাগাভাগির কাজ সমাধা করতে ত্রিশ-চল্লিশ বছরের যুদ্ধ বিবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের শেষে দেখা যায় যে, আলেকজাণ্ডারের সুবিশাল সাম্রাজ্যের স্থলে উদিত হয়েছে তিনটি বড় বড় সাম্রাজ্য। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরের একাংশ নিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য গঠন করেন। অর্থাৎ সেলুকাসের সাম্রাজ্য হেলেসপন্ট থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পার্থীয়গণ ইরান এবং আরো কিছু ভূখণ্ড সেলুকাস রাজবংশের কবল থেকে মুক্ত করে। অবশ্য তার পরেও পশ্চিম এশিয়ায় সেলুকাসদের সাম্রাজ্য আরো একশো বছর টিকে ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত সে অংশও রোমের কবলিত হয়। সিরিয়ার এন্টিঅক নগরী ছিল সেলুকাসদের এ সাম্রাজের রাজধানী। এ নগরী ক্রমশ প্রাচীনকালের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।
আলেকজাণ্ডারের অপর এক সেনাপতি প্রথম টলেমী মিশর অধিকার করে সেখানে টলেমী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ফিনিশিয়া এবং প্যালেস্টাইনও টলেমীর সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল আলেকজান্দ্রিয়া নগরী। আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচীনকালের একটি বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর এবং গ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

আলেকজাণ্ডারের অপর এক সেনাপতি এ্যান্টিগোনাস ম্যাসিডোনিয়া এবং গ্রীক নগররাষ্ট্র সমূহ করায়ত্ত করে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। অবশ্য অধিকাংশ গ্রীকরাষ্ট্রই জোট গঠন করে এবং বিদ্রোহ করে কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। কালক্রমে ১৪৬ থেকে ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত ভূ-ভাগই রোমক সাম্রাজের করতলগত হয়। আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তাঁর দিগ্বিজয়ের ফলাফল সুদূর-প্রসারী হয়েছিল।
আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের আগে গ্রীক সংস্কৃতি কেবলমাত্র গ্রীসের সীমান্তবর্তী জাতিসমূহকে প্রভাবিত করেছিল। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পর গ্রীসীয় সংস্কৃতি ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। টলেমী রাজ বংশ এবং সেলুকাস রাজবংশের অধীনে রাজ সরকারে এবং সেনাবাহিনীতে চাকরি নেয়ার জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাজের মাধ্যমে সম্পদশালী হওয়ার জন্যে দলে দলে গ্রীক নাগরিকরা মিশরে ও মধ্যপ্রাচ্যে আসতে শুরু করে।

এর ফলে ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরের বিস্তৃত অঞ্চলের শুধু রাজসভাতেই নয় বরং সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে গ্রীক ভাষা এবং গ্রীক সংস্কৃতির প্রচলন ঘটে। বস্তুত মিশরে গ্রীক ভাষার এত ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল যে, ইহুদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পুরাতন টেস্টামেন্টকে জনসাধারণের বোধগম্য করার জন্যে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করতে বাধ্য হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলে গ্রীক ও প্রাচ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল।
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ সংস্কৃতির নাম দেয়া হয়েছে ‘হেলেনিস্টিক” বা ‘আলেকজান্দ্রীয়’ সভ্যতা। হেলেনিস্টিক সভ্যতার অনেক প্রগতিশীল দিক ছিল। এ যুগে বহুসংখ্যক নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল। এ যুগে আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রীয় যুগেই ইউক্লিড, এরাটোস্থেনিস, আর্কিমিডিস, হিপার্কাস, হিরো প্রমুখ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

এ যুগে যদিও গ্রীক ভাষা এবং গ্রীক ব্যক্তিরাই সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তথাপি এ যুগের প্রধান প্রবণতা ও মনোভঙ্গি নিরূপিত হয়েছিল প্রাচ্য মানস দ্বারা। মিশরীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রভাবেই হেলেনিস্টিক যুগের গ্রীক চিন্তাধারায় কিছু কিছু অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ছিল গ্রীক স্বর্ণযুগের তুলনায় নিকৃষ্ট।
সাবেক গ্রীক গণতন্ত্রের আদর্শের স্থলে এ যুগে উদিত হয় স্বৈরতন্ত্রের, এবং এ স্বৈরতন্ত্র ছিল মিশরীয় বা পারসিক স্বৈরতন্ত্রের মতোই কঠোর। হেলেনিস্টিক যুগের সম্রাটরা নিজেদের স্বর্গীয় বা আধাস্বর্গীয় বলে দাবি করতেন। সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে মিশরে ঐশ্বরিক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল— একথা আগেই বলা হয়েছে। আর পশ্চিম এশিয়ায় সেলুকাস রাজবংশ এং মিশরে টলেমী রাজবংশ নিজেদের ওপর নিজেরাই দেবত্ব আরোপ করেছিলেন আরও সুচারুরূপে।

এঁরা রাজকীয় সনদে স্বাক্ষর করতেন “ঈশ্বর” নামে। ইতিহাসের ধারার পরিপন্থী এ সকল চিন্তাধারার উদয় যে এশীয় এবং প্রাচ্য প্রভাবেই ঘটেছিল, তা বলাই বাহুল্য। তবে মনে রাখা দরকার যে, হেলেনিস্টিক যুগ সর্বাংশে প্রগতিবিরোধী ছিল না। এ যুগে প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যবিলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলন ঘটায় হেলেনিস্টিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল।
হেলেনিস্টিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি, শিল্প, কৃষি এবং অর্থনীতিরও বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। পরের অনুচ্ছেদে গ্রীক সংস্কৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।
আরও দেখুন :
