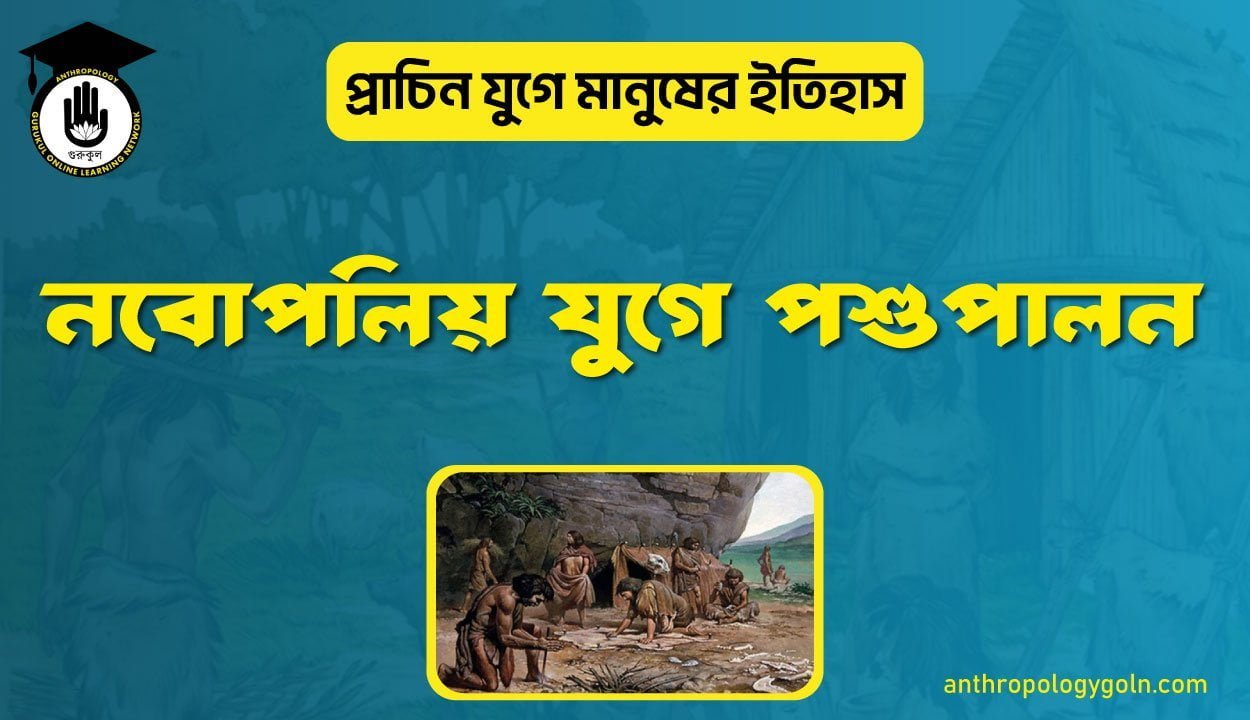আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নবোপলিয় যুগে পশুপালন
নবোপলিয় যুগে পশুপালন
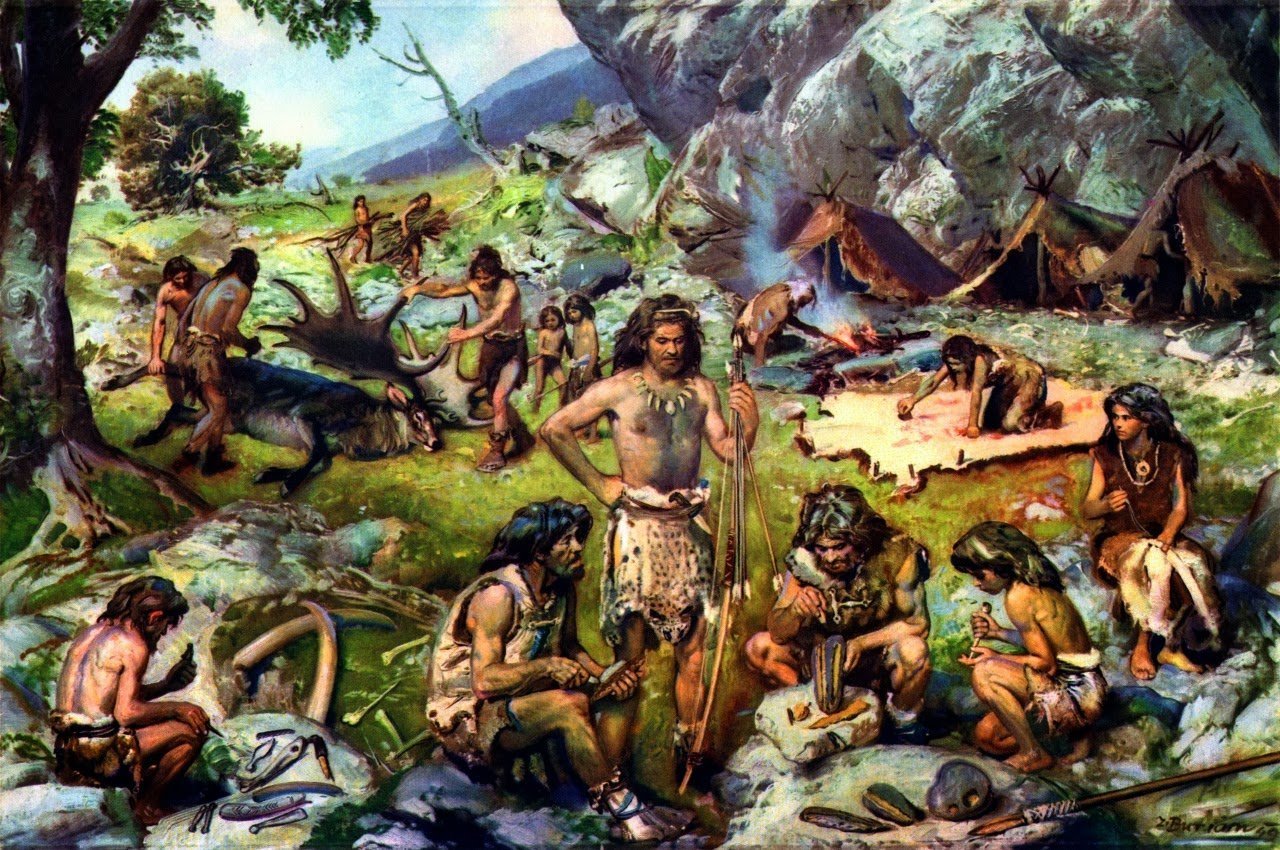
নবোপলিয় যুগে পশুপালন
নবোপলীয় যুগে মানুষ কৃষি আবিষ্কারের সাথে সাথে পশুপালনের কৌশলও আবিষ্কার করেছিল,একথা আগেই বলা হয়েছে। মানুষ কৃষিকাজ শুরু করার পরে হয়তো শস্যের লোভে নিরামিষভোজী প্রাণীরা শস্যখেতের দিকে আকৃষ্ট হত। এ ভাবে মানুষের সান্নিধ্যে থেকে থেকেই হয়তো ভেড়া, ছাগল, শূকর, গাধা, গরু প্রভৃতি মানুষের পোষ মেনেছিল।
পোষ মানানোর পর মানুষ দেখেছিল যে, তার থেকে মাংস, দুধ, চামড়া, লোম ইত্যাদি তো পাওয়া যায়ই, মাঠে পশু চরালে তার গোবর থেকে জমির উর্বরাশক্তিও বাড়ে। পশুশিকারের চেয়ে পশুপালন স্বভাবতই বেশি লাভজনক। কারণ জীবন্ত পশুর দুধ ও দুগ্ধজাত পদার্থকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে এবং পশুর বংশবৃদ্ধি ঘটলে প্রয়োজন মত তাদের মাংসও খাওয়া চলে।
পশুপালনের আবিষ্কার হওয়ার পর তাই আগেকার শিকারী মানুষের দলও পশুপালক দলে পরিণত হল এবং অনেক অঞ্চলে জমি চাষাবাদের উপযুক্ত না হওয়ায় অনেক নবোপলীয় কৃষিজীবীও পশুপালনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে সব কৃষিনির্ভর নবোপলীয় মানুষই আংশিকভাবে পশুপালনেও মনোনিবেশ করেছিল। পশুপালক দলের মানুষরা কিন্তু সাধারণত যাযাবর ছিল না। তারা দীর্ঘকাল একস্থানে বাস করত। চারণভূমি নষ্ট হয়ে গেলেই কেবল তারা অন্যত্র গিয়ে বাস স্থাপন করত।
নবোপলীয় অর্থনীতি বা উৎপাদন ব্যবস্থার দুটো প্রধান শাখা হল কৃষি এবং পশুপালন। এ দুই উৎপাদন প্রথা মিলে নবোপলীয় অর্থনীতির সৃষ্টি করেছিল এবং এরা ছিল পরস্পরের পরিপূরক। একদিকে নবোপলীয় কৃষিজীবী বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ও খাদ্যশস্য আবিষ্কার করেছে এবং উন্নত ধরনের শস্যবীজের মিশ্রণের মাধ্যমে নতুন জাতের শস্যের সৃষ্টি করেছে, অপরদিকে পশুপালক মানুষেরা যুগের পর যুগ পরিশ্রম করে, সাধনা করে নতুন প্রাণীকে পোষ মানিয়েছে, উন্নত গুণের প্রাণীদের সংমিশ্রণের মাধ্যমে উত্তম গুণসম্পন্ন প্রাণীর সৃষ্টি করেছে।

নবোপলীয় যুগে মানবসমাজ কৃষিজীবী ও পশুপালক— এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ায় সমগ্রভাবে মানুষের উন্নতি হয়েছে। নিজ নিজ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার দরুন কৃষক ও পশুপালকরা নতুন কর্মকৌশল ও পদ্ধতি আবিষ্কার করতে থাকে, পাশাপাশি অবস্থানরত পশুপালক ও কৃষক মানুষদের মধ্যে এ সকল অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটতে থাকে। এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার দরুনই মানুষ কালক্রমে গাধা, গরু, ঘোড়া, উট প্রভৃতিকে ভারবাহী পশু হিসাবে ব্যবহার করতে শেখে।
এ সব পশুকে কৃষিকাজে নিয়োগ করার চেষ্টা থেকে ৩০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়াতে বা ইরানে কাঠের লাঙল প্রভৃতিরও আবিষ্কার হয়। এর ফলে আবার কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। পশুপালক ও কৃষিজীবীদের সামাজিক শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে পণ্য বিনিময় প্রথা জন্মলাভ করে। কারণ পশুপালক সমাজের হাতে পশু, চামড়া, মাংস, লোম প্রভৃতি সব সময়েই উদ্বৃত্ত থাকত কিন্তু তাদের ছিল খাদ্যশস্য প্রভৃতির প্রয়োজন।
আর কৃষকদের হাতে খাদ্যশস্য প্রভৃতি উদ্বৃত্ত থাকত, কিন্তু তাদের ছিল মাংস ইত্যাদির অভাব। তাই এ দুই সমাজের মধ্যে বস্তু বিনিময়ের রেওয়াজ হয়। প্রথম প্রথম সাধারণত গরুর সঙ্গে গম, ধান প্রভৃতি বিনিময় করা হত। কালক্রমে হাতিয়ার, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতির বিনিময় বা কেনাবেচা শুরু হয়। ক্রমশ একটা নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে জিনিস কেনাবেচার রেওয়াজ হয়।

কোথাও গরু, কোথাও পশুর মূল্যবান চামড়া, কোথাও নুন এ রকম বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়। গরু, নুন, চামড়া এগুলোকে তাই বলা চলে আদিমকালের টাকা বা মুদ্রা। ধীরে ধীরে অবশ্য কড়ি বা সোনা, রূপা বা অন্যান্য ধাতু মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত হয়, তবে তা অনেক পরের কথা।
আরও দেখুন :