“নৃবিজ্ঞান পরিচিতি” পাঠটি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ/বিএসএস শ্রেণীর “সমাজতত্ত্ব – ২ (সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান পরিচিতি)” এর একটি পাঠ। এখানে নৃবিজ্ঞান কী, এর পরিধি ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে নৃবিজ্ঞান মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনের সামগ্রিক অধ্যয়ন হিসেবে কীভাবে কাজ করে এবং কেন এটি সমাজতত্ত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।
নৃবিজ্ঞান পরিচিতি
নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা
“নৃবিজ্ঞান’ হল ইংরেজী ‘এ্যাগ্রোপলজি’-র (anthropology) বাংলা প্রতিশব্দ। এ্যান্থোপলজি কথাটির মূলে রয়েছে একটি গ্রীক শব্দ এ্যাক্সোপস’ ( anthropos), যার অর্থ মানুষ। সংস্কৃত শব্দ ‘নৃ’ মানেও তাই। কাজেই ‘নৃবিজ্ঞান’ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় মানব বিষয়ক বিজ্ঞান’ (উল্লেখ্য, বাংলায় এ্যাগ্রোপলজির প্রতিশব্দ হিসাবে মানব বিজ্ঞান কথাটি কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা বহুল প্রচলিত নয়)।
নৃবিজ্ঞান কি ধরনের বিজ্ঞান?
ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্রসহ আরো অনেক শাস্ত্র বা জ্ঞানকান্ড রয়েছে, যেগুলোও কোন না কোনভাবে মানব বিষয়ক বিজ্ঞান বটে। কাজেই শুধুমাত্র ‘মানব বিষয়ক বিজ্ঞান’ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করলে নৃবিজ্ঞানকে আলাদা করে চেনা যায় না। নৃবিজ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, মানব বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় এর বিষয়বস্তু ব্যাপকতর পরিধিসম্পন্ন ও অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ।
নৃবিজ্ঞানে একাধারে মানব সত্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়, এবং তা করতে গিয়ে এর অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে এক বিশাল পটভূমি জুড়ে, যার আওতায় পড়ে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক | অতীত থেকে শুরু করে এ যাবত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যত ধরনের মানবগোষ্ঠী বাস করে গেছে বা করছে, সবাই।
‘নৃবিজ্ঞান’-এর পরিবর্তে ‘নৃতত্ত্ব’ কথাটি আপনাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হতে পরে। ‘এ্যাগ্রোভসজি’র প্রতিশব্দ হিসেবে শেষোক্ত শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু রয়েছে দীর্ঘতর সময় ধরে (ক্ষেত্রবিশেষে ‘নৃবিদ্যা’ শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে)।
আপনি হয়তবা লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলা ভাষায় রচিত অনেক বইপুস্তক বা পত্রপত্রিকায় বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য’ বা ‘নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস’ ইত্যাদি কথা ব্যবহার করা হয়, যেগুলি দিয়ে সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা প্রাগৈতিহাসিক অতীত সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনায় নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে ‘নৃতাত্ত্বিক’ বিশেষণটা এমন সব বিষয়কে |
নির্দেশ করে যেগুলো নিয়ে নৃবিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় বিশেষ করে দৈহিক নৃবিজ্ঞান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে–হয়ত একসময় ব্যাপক গবেষণা বা লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র এসব বিষয় দিয়ে নৃবিজ্ঞানের পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে ‘নৃতত্ত্ব’ পদটি, বা এর বিশেষণরূপ ‘নৃতাত্ত্বিক’, যেভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, তা সমকালীন প্রেক্ষাপটে যথার্থ নয়।
এ্যান্ড্রোপলজির অপেক্ষাকৃত পুরানো প্রতিশব্দ ‘নৃতত্ত্ব’ বাংলা ভাষায় যে সময় চালু হয়েছিল, তখন ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এমন একটা ধারণা ব্যাপকভাবে চালু ছিল যে এটি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে মূলতঃ মানব জাতির উৎপত্তি ও বিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের মানবগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য, এবং “আদিম’ সমাজ বা সংস্কৃতি অধ্যয়ন করা হয়।
এ ধরনের ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না, কারণ বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত মূলতঃ উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপরই ‘নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও লেখালেখির ঝোঁক বেশী। ছিল।। তবে সময়ের সাথে সাথে এই প্রবণতা পাল্টে গেছে, এবং নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুকে অনেকটাই ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে নৃতত্ত্ব মানেই মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস বা আদিম সমাজ অধ্যয়ন, একথা আর বলা যায় না।
এখনকার নৃতত্ত্ববিদদের অনেকেই অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের মতই সমকালীন বিভিন্ন ধরনের সমাজ, তাদের সংস্কৃতি-অর্থনীতি- রাজনীতি ইত্যাদি নানান বিষয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করছেন। আর এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ‘নৃতত্ত্ব’র বদলে ‘নৃবিজ্ঞান’ই ‘এ্যান্থ্রোপলজি’র প্রতিশব্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ বিষয় পড়ানো শুরু হওয়ার সময় থেকে। একইভাবে নৃবিজ্ঞান চর্চার সাথে যুক্ত শিক্ষক-গবেষকরা ‘নৃতত্ত্ববিদ’-এর বদলে ‘নৃবিজ্ঞানী’ হিসাবেই নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন।
সাধারণভাবে বলা যায়, সমকালীন প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান হচ্ছে বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বলিত এমন একটি জ্ঞানকান্ড যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ‘মানুষ’কে অধ্যয়ন করে। আগেই বলা হয়েছে, নৃবিজ্ঞানে একাধারে মানব সত্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়।
একটি প্রজাতি হিসেবে মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস থেকে শুরু করে অতীত ও বর্তমানকালের বিভিন্ন ধরনের মানব সমাজের সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন নৃবিজ্ঞানে করা হয়। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশাল পরিধির অধিকারী এই জ্ঞানকান্ডের স্বভাবতই রয়েছে বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ক্ষেত্র। তবে দেশ-কাল ভেদে এই উপবিভাগগুলোর নামকরণ ও শ্রেণীকরণে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।
মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞানে সচরাচর চারটি প্রধান উপবিভাগ চিহ্নিত করা হয়, এগুলি হল, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান ও দৈহিক নৃবিজ্ঞান। অনেকে অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেরই দুটি শাখা হিসাবে গণ্য করেন এবং ethnology বা জাতিতত্ত্ব নামে এর আরেকটি শাখা চিহ্নিত করেন।
ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় ধারার নৃবিজ্ঞানে ‘সংস্কৃতি” ধারণার চাইতে ‘সমাজ’ ধারণার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলে এই প্রেক্ষিতে ‘সামাজিক নৃবিজ্ঞান’ কথাটি অধিকতর প্রচলিত। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বরাবরই বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ছিল, কাজেই স্থান- কাল ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা-উপধারার মধ্যে সবক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না।
সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের অনেক স্থানেই মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে মূলতঃ একই বৃহত্তর ধারার অন্তর্গত হিসাবে গণ্য করা হয়, যাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসাবে অনেকে অভিহিত করে থাকেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান তথা নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য উপবিভাগের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বিষয়-ভিত্তিক গবেষণার অনেক বিশেষায়িত ক্ষেত্র, যেমন, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, ধর্মের নৃবিজ্ঞান, প্রতিবেশগত নৃবিজ্ঞান, চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান, ফলিত নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি।
নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী
বিভিন্ন নামে অভিহিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ধারার মধ্যে সাধারণভাবে কিছু অভিন্ন যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি ধারণার ব্যবহার, সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, মাঠকর্ম ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এসব মিল নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোকে একত্রে একটি সমন্বিত ও স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে পরিচিতি দিয়েছে।
এছাড়া অনেক জায়গায়, বিশেষ করে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, নৃবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নৃবিজ্ঞানের একাধিক শাখার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। ফলে এখনো অনেক নৃবিজ্ঞানীই তাঁদের গবেষণা ও লেখালেখিতে এক ধরনের সমন্বিত ‘নৃবৈজ্ঞানিক’ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের চেষ্টা করেন। নীচে একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উল্লিখিত প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হল।
সংস্কৃতির ধারণার তাৎপর্য :
নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেই ‘সংস্কৃতি’ একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুধু সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে নয়, দৈহিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান ও ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানেও সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝাত–নৃত্য, সঙ্গীত | ইত্যাদি–নৃবিজ্ঞানীরা তার থেকে ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থে শব্দটি ব্যবহার শুরু করেছিলেন বেশ আগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টায়লর সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে: ‘সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল সমগ্র, যার আওতায় পড়ে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, প্রথা |
এবং অন্য যে কোন কর্মদক্ষতা ও অভ্যাস যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জন করে’। টায়লর পরে অন্য নৃবিজ্ঞানীরা মিলে সংস্কৃতির শতাধিক সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় তাদের কাছে এই ধারণা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতির ধারণার দুই ধরনের তাৎপর্য রয়েছে। একদিকে | একটি প্রজাতি হিসাবে জীবজগতে মানুষের অনন্যতা বোঝানোর জন্য সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয়: নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষেরই রয়েছে সংস্কৃতি ধারণ করার ক্ষমতা, এবং এই |
সাধারণ অর্থে মানুষ মাত্রই সংস্কৃতিসম্পন্ন (এই সাধারণ অর্থে ইংরেজীতে সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয় একবচনে, যা অনেক সময় বড় হাতের C দিয়ে লেখা হয়: Culture)। অন্যদিকে বিভিন্ন মানব সমাজের ভিন্নতার সূচক হিসাবেও সংস্কৃতির
ধারণা ব্যবহার করা হয়:
প্রতিটা সমাজেরই রয়েছে নিজস্ব কিছু রীতি-নীতি, আচার-প্রথা ইত্যাদি, অর্থাৎ সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট নিজস্ব রূপ। কাজেই সমাজ ভেদে সংস্কৃতিরও ভিন্নতা দেখা যায় (এই অর্থে ইংরেজীতে সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয় বহুবচনে, যা লেখা হয় ছোট হাতের c দিয়ে cultures) ।

সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী:
নৃবিজ্ঞানের কোন একটি বিশেষায়িত ধারায় মানব জীবনের নির্দিষ্ট কোন দিক অধ্যয়নের উপর নজর দেওয়া হলেও সাধারণত তা বিচ্ছিন্নভাবে করা হয় না, বরং মানব জীবনের একটা দিক কিভাবে অন্যান্য দিকগুলোর সাথে সম্পর্কিত, তাও দেখার চেষ্টা করা হয়। কাজেই বলা হয় যে, নৃবিজ্ঞানীরা সমগ্রবাদী বা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গী (holistic perspective) অনুসরণের চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তারা মানুষ ও তার সংস্কৃতি বা সমাজের কোন অংশকে খন্ডিতভাবে না দেখে সমগ্রের আলোকে সেটাকে অনুধাবনের চেষ্টা করেন।
মাঠকর্ম :
ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন শাখার নৃবিজ্ঞানেই মাঠকর্ম অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন, দৈহিক নৃবিজ্ঞানীরা মানব জীবাশ্মের সন্ধানে বা প্রাণীজগতে মানুষের নিকটতম প্রজাতিদের সামাজিক আচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য মাঠকর্ম সম্পাদন করেন।
প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা খননকার্যের মাধ্যমে অতীতের কোন জনপদের সন্ধান পেলে সেখান থেকে বিস্তারিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক একটা সমাজের বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করেন। এভাবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিটা শাখাতেই ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়।
তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী :
নৃবিজ্ঞানের সকল শাখাতেই বিভিন্ন কালের ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন করা হয়। বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন স্থানের মানুষদের জৈবিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করেন কি কি বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং কি কি বৈশিষ্ট্য শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডের মধ্যে একমাত্র নৃবিজ্ঞানেই দেখা যায় স্থান ও কালের দিক থেকে মানব বৈচিত্র্যের সমগ্র পরিধিকে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ কোন আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা।
উপরের আলোচনায় নৃবিজ্ঞানের সনাতনী বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এখানে একথাও যোগ করা দরকার যে, নৃবিজ্ঞানকে মানব বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলার রেওয়াজ থাকলেও বাস্তবে অবশ্য প্রায় কোন নৃবিজ্ঞানীকেই বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি এর সকল শাখায় সমান জ্ঞান বা আগ্রহ নিয়ে বিচরণ করেন।
অতীতে যখন নৃবিজ্ঞানীদের নজর কেন্দ্রীভূত ছিল তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠীসমূহের প্রতি, তখন হয়ত একই নৃবিজ্ঞানী নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে একাধারে তাদের প্রাক-ইতিহাস থেকে শুরু করে ভাষা, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি অধ্যয়ন করতেন। তবে এ ধরনের উদাহরণ বর্তমানে বিরল।
অতীতে আদিম বলে বিবেচিত বিভিন্ন সমাজ অধ্যয়নের ব্যাপারে আগ্রহের ব্যাপকতা নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে যতটা সমন্বিত রাখতে সহায়তা করেছিল, বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। কাজেই সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কিছুটা দূরত্ব বিরাজ করছে, যে কারণে ‘নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী’ বলে অভিন্ন কোন কিছু আছে, এ ব্যাপারে সকল নৃবিজ্ঞানী হয়ত সহজে একমত হবেন না।
সারাংশ
‘নৃবিজ্ঞান’ হল ইংরেজী এ্যান্ড্রোপলজি’-র (anthropology) বাংলা প্রতিশব্দ। এ্যান্ড্রোপলজি কথাটির মূলে রয়েছে একটি গ্রীক শব্দ ‘এ্যান্থো পস’ (anthropos), যার অর্থ মানুষ। সংস্কৃত শব্দ ‘নৃ’ মানেও তাই। কাজেই ‘নৃবিজ্ঞান’ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় ‘মানব বিষয়ক বিজ্ঞান’ । মানব বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় এর বিষয়বস্তু ব্যাপকতর পরিধিসম্পন্ন ও অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান হচ্ছে বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বলিত এমন একটি জ্ঞানকান্ড যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ‘মানুষ’কে অধ্যয়ন করে।
নৃবিজ্ঞানে একাধারে মানব সত্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়। একটি প্রজাতি হিসেবে মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস থেকে শুরু করে অতীত ও বর্তমানকালের বিভিন্ন ধরনের মানব সমাজের সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন নৃবিজ্ঞানে করা হয়।
বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশাল পরিধির অধিকারী এই জ্ঞানকান্ডের স্বভাবতই রয়েছে বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ক্ষেত্র। মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞানে সচরাচর চারটি প্রধান উপবিভাগ চিহ্নিত করা হয়, এগুলি হল, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান ও দৈহিক নৃবিজ্ঞান। ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় ধারার নৃবিজ্ঞানে ‘সংস্কৃতি’ ধারণার চাইতে ‘সমাজ’ ধারণার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলে এই প্রেক্ষিতে ‘সামাজিক নৃবিজ্ঞান’ কথাটি অধিকতর প্রচলিত।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান তথা নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য উপবিভাগের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বিষয়-ভিত্তিক গবেষণার অনেক বিশেষায়িত ক্ষেত্র, যেমন, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, ধর্মের নৃবিজ্ঞান, প্রতিবেশগত নৃবিজ্ঞান, চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান, ফলিত নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি। বিভিন্ন নামে অভিহিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ধারার মধ্যে সাধারণভাবে কিছু অভিন্ন যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি ধারণার ব্যবহার, সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, মাঠকর্ম ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।
দৈহিক নৃবিজ্ঞান
দৈহিক নৃবিজ্ঞান মূলত মানুষের মানুষের দৈহিক দিক বা ফিজিক্যাল ফিচার সম্পর্কে আলোচনা করে। মানুষের দৈহিক অর্থাৎ আকার-আকৃতি, বৈশিষ্ট্য, প্রাণী হিসেবে মানুষের পৃথিবীতে – উৎপত্তি, বিবর্তন। আলোচনা করে মানুষের আদিম ও আধুনিক রূপ নিয়ে।
দৈহিক নৃবিজ্ঞানের সারাংশ:
দৈহিক নৃবিজ্ঞানে যেসব বিষয় অধ্যয়ন করা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে একটি এরজাতি হিসাবে মানুষের উৎপতি ও বিবতর্নের ইতিহাস, জৈবিক বে বিচারে মানুষের নিকটতম প্রানীদের সাথে মানুষের মিল ও আমিল, এবং দৈহিক ও অন্যান্য জৈবিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে মানবজাতির মধ্যেকার বৈচিত্র্য।
দৈহিক-নৃবিজ্ঞানে সমকালীন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেকার দৈহিক পার্থক্য ও সম্পর্ক নিয়েও গবেষণা করা হয়। এ ধরনের গবেষণায় দীর্ঘকাল যাবত বাহি্যক উপরই নজর কেন্দ্রীভূত ছিল। গায়ের রং চুলের ধরন, চোখ-মুখের গড়ন প্রভৃতির ভিভিতে মানবজাতিকে বিভিন্ন race বা নরবর্ণে বিভক্ত করার রেওয়াজ ছিল।
প্রকৃতপক্ষে নরবণর্র সজ্ঞা ও শোণীকরণ নিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞান কখনো কোন সবর্জনস্কীকৃত মতামত ছিল না। অধিকন্ত সাম্প্রাতিককালের দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই নরবর্ণে্র ধারণাকে বিজ্ঞান- সম্মত নয় বলে বাতিল করে দিয়েছেন।
সমকালীন দৈহিক নৃবিজ্ঞানের নরবণর্র ধারণা কাযর্ত পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ হল, যেভাবেই নরবণর্র সংজ্ঞা ও শ্রেণীকরণ দাঁড় করানো হোক না কেন, বাস্তবে এক নরবণের্র সাথে আরেক নরবণর্র কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহি্ত করা যায় না।
বতর্মানে দৈহিক-নৃবিজ্ঞান বা বাহ্যিক দৈহিক বেশিষ্টের চাইতে মানবজাতির অন্তনির্হিত জেনেটিক (genetic অথাৎ জিন- সংক্রান্ত) বৈচিত্র্য অধ্যয়নের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। এ ধরনের পারিবতর্নের আলোকে ইদানীং দৈহিক হাবিজ্ঞানের হলে জৈবিক নৃবিজ্ঞান (biological anthropology) পরিচয়টাই অনেকের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে ।
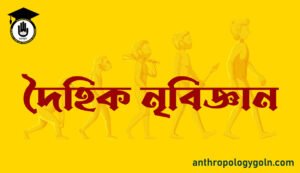
দৈহিক নৃবিজ্ঞান:
দৈহিক নৃবিজ্ঞানের সারাংশ: মানুষের দৈহিক দিক সম্পর্কে নৃ-বিজ্ঞানের যে শাখা বিস্তারিত আলােচনা করে তাকে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান বলা হয়। এই শাখা মানুষের দৈহিক আকার-আকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণী হিসেবে মানুষের পৃথিবীতে উৎপত্তি, বিবর্তন তথা আদিম ও আধুনিক মানুষের বিভিন্ন প্রকরণ সম্পর্কে আলােচনা করে। মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করতে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান- অস্থি, কংকাল, মাথা, দেহের গঠন প্রণালি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে।
এছাড়া মানুষ পূর্বে কী ছিল, বিবর্তনের মাধ্যমে সে কীরূপ ধারণ করেছে- তা তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে জীব জগতের মানুষের স্থান কোথায় তা নির্ণয় করে। এভাবে মানুষের বিবর্তনের হারানাে সূত্র (Missing link) খুঁজে পেতে চেষ্টা করে।
দৈহিক নৃবিজ্ঞানে যেসব বিষয় অধ্যয়ন করা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে একটি প্রজাতি হিসাবে মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস, জৈবিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে মানুষের নিকটতম প্রাণীদের সাথে মানুষের মিল ও অমিল, এবং দৈহিক ও অন্যান্য জৈবিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে মানবজাতির মধ্যেকার বৈচিত্র্য। বিষয়বস্তুর কারণে জীববিজ্ঞানের মৌলিক অনেক বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হয় দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের। সেসাথে মানব সন্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক উভয় মাত্রার পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ত বিবেচনায় রাখার তাগিদে নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিভিন্ন প্রত্যয় ও তত্ত সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখতে হয় তাদের।
চার্লস ডারউইন যখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই তত দেন যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমরূপান্তরের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে, তখন ধমীয়ি ব্যাখ্যার বাইরে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিসার একটা দিকনির্দেশনা পাওয়া গিয়েছিল।
ততদিনে ভূত্তকের বিভিন্ন গভীর স্তর থেকে বিলুপ্ত অনেক প্রাণী ও উভিদের জীবাশ্মের সন্ধান মিলতে শুরু করেছিল, যেগুলির মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ও মানব-সদৃশ প্রাণীদের নমুনাও যুক্ত হচ্ছিল (জীবাশ্ন বা fossil হল লক্ষ-কোটি বছর আগেকার কোন প্রাণী বা উভিদের দেহাবশেষ, যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে শিলীভূত রূপে ভূত্তকের বিশেষ কোন স্তরে সংরক্ষিত থেকে গেছে)। একটা সময়ে এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, জীবজগতের অন্যান্য প্রজাতির মত মানুষও বিবর্তনের মাধ্যমেই আজকের রূপে এসে উপনীত হয়েছে।
দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা মানব বা মানবসদৃশ প্রাণীদের জীবাশব নিয়ে কাজ করেন, তাদের লক্ষ্য হল প্রাপ্ত নমুনাসমূহের ভিত্তিতে মানব বিবর্তনের ইতিহাসের একটা চিত্র দাড় করানো। তাদের গবেষণার ভিত্তিতে বলা যায়, আজ থেকে আনুমানিক বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানবসদৃশ কিছু প্রাণীর বিচরণ ছিল যেগুলোর মগজের গড় আয়তন মানুষের চাইতে শিম্পাজী-গরিলাদের মত প্রাণীর কাছাকাছি হলেও অন্যান্য দিক থেকে তারা মানুষের মতই ছিল: যেমন তারা দু’পায়ের উপর ভর করে খাড়া হয়ে চলাফেরা করত, এবং খুব সরল ধরনের পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত।
এই প্রাণীদের নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাস (australopithecus ল্যাটিন ভাষায় australo – বলতে দক্ষিণাঞ্চলীয় এবং pithecus বলতে ৪১০ শ্রেণীর বানর অর্থাৎ শিম্পাজি, গরিলা প্রভৃতি লাঙ্গুলবিহীন বানরদের বোঝায়। অস্ট্রালোপিথেকাসদের প্রথম নমুনা পাওয়া গিয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে, তাই এই নাম করণ)। ধারণা করা হয়, অস্ট্রালোপিথেকাস বর্গের প্রাণীদেরই কোন শাখা থেকে আধুনিক মানুষের পূর্বসূরী প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি ঘটেছে। অস্ট্রালোপিথেকাসদের চাইতে বেশী আয়তনের মস্তিষ্কসম্পন্ন আদি-মানবদের উৎপত্তি ঘটে আনুমানিক দশ থেকে বিশ লক্ষ বছর আগে।
এদের মধ্যে হোমো ইরেকটাস নামে অভিহিত (homo sapiens গ্রীক শব্দ homo অর্থ মানুষ) প্রজাতির আদি-মানবদের জীবাশ্ব পাওয়া গেছে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায়। জাভা মানব, পিকিং মানব প্রভৃতি নামে খ্যাত জীবাশ্বুসমূহ হল এই বর্ণের আদি-মানবদের।
ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে হোমো ইরেকটাস মানবদের থেকেই হোমো সেপিয়েন্স (homo sapiens) নামে অভিহিত আধুনিক মানব প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে আনুমানিক চল্লিশ হাজার থেকে সোয়া লক্ষ বছর আগে। নিয়ানডার্থাল নামে অভিহিত আধুনিক মানব প্রজাতির একটি শাখা বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন, এবং তাদের থেকে আলাদা করার জন্য homo sapiens sapiens নামের একটি ভিন্ন শাখার অস্তিত ধরে নেওয়া হয়, যেটা বর্তমানে পৃথিবীর বুকে টিকে আছে।
তবে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের কারো কারো মতে নিয়ানডার্থাল ধারার মানুষরা একেবারে বিনুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং তারা মানব প্রজাতির অন্য শাখার সাথে মিশে বর্তমান যুগের মানুষদের উদ্ভবে ভূমিকা রেখেছে। যাই হোক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বর্তমান যুগের সকল মানুষই একটি একক প্রজাতির অন্তর্গত, এবং সে হিসাবে সকল মানুষের রয়েছে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেগুলির উপর দৈহিক নৃবিজ্ঞান আলোকপাত করে।
একটি প্রজাতি হিসাবে মানুষের বিশিষ্টতা বুঝতে গিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে জীববৈজ্ঞানিক বিচারে মানুষের নিকটতম সমকালীন প্রজাতিদের নিয়েও গবেষণা করেন। প্রাণীবিজ্ঞানীদের শ্রেণীকরণ অনুসারে মানুষ ‘প্রাইমেট” বর্গভুক্ত একটি প্রাণী, যে বর্গের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির বানর, ৪ বা “বনমানুষ” অর্থাৎ লেজবিহীন বানর, যথা: শিম্পাজী, গরিলা, ওরাঙ উটান, ও গিবন বা উন্লুক, যেগুলো প্রাণীজগতে মানুষের নিকটতম আত্মীয়) এবং লেমুর, ট্রি শ্রু ইত্যাদি আরো কিছু প্রাণী।
অন্যান্য প্রাইমেটদের সাথে মানুষের দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন করা হয় প্রাণী হিসাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের লক্ষ্যে। সেসাথে বানর ও “বনমানুষ’দের সামাজিক আচরণ অধ্যয়নের মাধ্যমেও বোঝার চেষ্টা করা হয় প্রাগৈতাসিক মানুষের সামাজিক সংগঠন কেমন হয়ে থাকতে পারে, এবং কোন্ কোন ক্ষেত্রে মানব আচরণ এই সব প্রাণীদের সাথে তুলনীয় বা তাদের থেকে পৃথক।
দৈহিক নৃবিজ্ঞানে সমকালীন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেকার দৈহিক পার্থক্য ও সম্পর্ক নিয়েও গবেষণা করা হয়। এ ধরনের গবেষণায় দীর্ঘকাল যাবত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহের উপরই নজর কেন্দ্রীভূত ছিল। গায়ের রৎ চুলের ধরন, চোখ-মুখের গড়ন প্রভৃতির ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভিন্ন 18০6 বা নরবর্ণে বিভক্ত করার রেওয়াজ ছিল (18০6-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে “মহাজাতি’ শব্দটিও বাংলায় প্রচলিত রয়েছে, বিশেষ করে রুশ ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত মিখাইল নেস্তুর্বের এজাতি, জাতি ও প্রগতি শীর্ষক একটি গ্রন্থে, যা বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজলভ্য ছিল)।
আপনারা মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিগ্রোয়েড প্রভৃতি শব্দের সাথে নিশ্চয় পরিচিত আছেন, এবং কোন্ নরবর্ণভূক্ত মানুষের চেহারা বা অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্য কেমন, এ সম্পর্কে আপনাদের কিছু ধারণা হয়তবা আছে। এগুলি হল একটি বহুল-প্রচলিত শ্রেণীকরণ অনুসারে প্রধান কয়েকটি নরবর্ণর নাম। এই শ্রেণীকরণে অনেকসময় অস্ট্রালয়েড নামে আরেকটি প্রধান নরবর্ণকে শনাক্ত করা হয়, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা যেটার অন্তর্গত। তবে প্রকৃতপক্ষে নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীকরণ নিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞানে কখনো কোন সর্বজনম্বীকৃত মতামত ছিল না।
অধিকন্তু সাম্প্রতিককালে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই নরবর্ণর ধারণাকে বিজ্ঞান-সম্মত নয় বলে বাতিল করে দিয়েছেন। সমকালীন দৈহিক নৃবিজ্ঞানে নরবর্ণর ধারণা কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ হল, যেভাবেই নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীকরণ দীড় করানো হোক না কেন, বাস্তবে এক নরবর্ণর সাথে আরেক নরবর্ণর কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করা যায় না।
এমন কোন মানবগোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া মুশকিল যার প্রত্যেক সদস্যের মধ্যেই সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বরং, যেভাবেই নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারণ করা হোক না কেন, অনেক জনগোষ্ঠীর দেখা মিলবে যাদের মধ্যে একাধিক নরবর্ণর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। এসব জনগোষ্ঠীকে মিশ্র” বলে চিহ্নিত করা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়, কারণ মানব ইতিহাসে কখনো পৃথক পৃথক বিশুদ্ধ নরবর্ণ ছিল, এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
নরবর্ণর ধারণা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতিগত সমস্যার পাশাপাশি আরেকটি বিপজ্জনক প্রবণতাও দেখা গেছে, সেটা হল, বিগত শতান্দীগুলোতে পশ্চিমা অনেক দেশেই নরবর্ণর ধারণার সাথে বর্ণবাদী চিন্তাচেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের ভিক্তিতে জাতিগত শেষ্ঠতু বা নিকৃষ্টতার ধারণা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হত। এ ধরনের চিন্তাধারার পরিণতি কত মারাত্বক হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল হিটলারের নাৎসী বাহিনী যখন জার্মান জাতিকে “শুদ্ধ’ করার নামে লক্ষ লক্ষ ইহুদী ও জিপসীকে হত্যা করে।
বর্তমানে দৈহিক নৃবিজ্ঞানে বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে মানবজাতির অন্তর্নিহিত জেনেটিক (genetic অর্থাৎ জিন-সংক্রান্ত) বৈচিত্র্য অধ্যয়নের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিভিন্ন জেনেটিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে বন্টিত, এবং জেনেটিক পার্থক্যগুলো কি কারণে বা কি প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে, এসব প্রশ্নের উত্তর খোজার কাজে অনেক দৈহিক নৃবিজ্ঞানীও শামিল রয়েছেন। আর এ ধরনের পরিবর্তনের আলোকে ইদানীং দৈহিক নৃবিজ্ঞানের স্থলে জৈবিক নৃবিজ্ঞান (biological anthropology) পরিচয়টাই অনেকের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।
যাই হোক, মানব বৈচিত্র্যের জৈবিক উপাদানসমূহ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দৈহিক/জৈবিক নৃবিজ্ঞানীদের নজর বাহ্যিক বা অবাহ্যিক যে ধরনের পার্থক্যের উপরই কেন্দ্রীভূত হোক না কেন, এসব পার্থক্যের মধ্য দিয়েও একই প্রজাতির সদস্য হিসাবে পৃথিবীর সকল মানুষ যেসব অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেগুলির উপর আলোকপাত করাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে। এভাবে তারা মানব অস্তিতকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবনে সহায়তা করেন।
সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান

আজকের আলোচনার বিষয় সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান। সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান দুটিই নৃবিজ্ঞানের শাখা। সামাজিক নৃবিজ্ঞান (Social Anthropology) নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনে এই বিষয়টির অধ্যয়নের সূত্রপাত হয়। এর জনক হলেন ব্রনিসলাউ মলিনস্কি। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আলোচনা মূলত মানুষের মাঝে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপরে নিবদ্ধ। এটি সামাজিক নৃবিজ্ঞানের বিপরীত। এর আলোচনা মূলত নৃতত্ত্বকে ধ্রুবক ধরে এর একটি অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আলোচনা করা। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটা সমৃদ্ধ প্রণালী রয়েছে গবেষণার।
সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান:
সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হচ্ছে নৃবিজ্ঞান চর্চার যথাক্রমে ব্রিটিশ ও মার্কিন এতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত দুটি ঘনিষ্ঠ ধারা। নামকরণের পার্থক্য সত্ত্বেও শুরু থেকেই সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন সীমারেখা ছিল না। (আপনারা যদি বাজারে প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একাধিক পাঠ্যবই মিলিয়ে দেখেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, কোন পাঠ্য বইয়ের শিরোনামে হয়ত শুধু সামাজিক নৃবিজ্ঞান, এবং আরেকটাতে হয়ত শুধু সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান রয়েছে, কিন্তু সূচাপত্রে অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলোর তালিকা কমবেশী একইরকমই পাবেন।)
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানেরই সূচনা হয়েছিল সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে উনবিংশ শতান্দীতে প্রচলিত বিভিন্ন অনুমাননির্ভর তত্তের বিরোধিতা করে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে।সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে যথাক্রমে ‘সমাজ’ ও “সংস্কৃতি প্রত্যয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হলেও উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানীরাই এই বিষয়গুলি অধ্যয়নের জন্য তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠীদের উপরই বেশী নজর দিয়েছিলেন।
প্রকৃতপক্ষে, “আদিম” বলে বিবেচিত বিভিন্ন সমাজ ও তাদের সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়নই একটা সময় পর্যন্ত সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মূল পরিচায়ক ছিল। উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানেই বিভিন্ন আদিম সমাজের জ্ঞাতিব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে।এসব কারণে, যেমনটা ইতোমধ্যে আপনারা জেনেছেন, মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে একই বৃহত্তর ধারার অন্তর্পত হিসাবে গণ্য করা হয়, যাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসাবে অনেকেই অভিহিত করে থাকেন।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কৃতির সংজ্ঞায়ন ও এই ধারণার উপর গুরুতারোপের ক্ষেত্রে মার্কিন নৃবিজ্ঞানীরা অনেকটা ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী টায়লরের এঁতিহ্য অনুসরণ করেছেন, (টায়লরের দেওয়া সংস্কৃতির সংজ্ঞা আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে পাঠ ১-এ)।অন্যদিকে জ্ঞাতিসম্পর্কের মত বিষয় অধ্যয়নের উপর নজর দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা অনেকটা মার্কিন নৃবিজ্ঞানী মর্গানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।
বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটেনে যারা সামাজিক নৃবিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন, তারা মনে করতেন যে তাদের অধ্যয়নের মূল বিষয় ছিল “সমাজ’, বিশেষ করে “আদিম সমাজ’। উল্লেখ্য, সমাজ অধ্যয়নের জন্য সমাজবিজ্ঞান (sociology) নামে একটি জ্ঞানকান্ড ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ মাত্রই যে কোন না কোন সমাজের সদস্য, এই সত্যটা উপলব্ধি করার জন্য আমাদের সমাজ বিজ্ঞান পড়ার দরকার পড়ে না।
আপনার আমার প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সমাজ সম্পর্কে এক ধরনের জ্ঞান আছে, যা আমরা সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জন করি। তবে সচরাচর আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বাইরে “সমাজ’ ধারণা নিয়ে বিমূর্তভাবে ভাবি না, বা পুরো সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে সংগঠিত, এটির বিভিন্ন অংশ কি কি এবং সেগুলি কীভাবে কাজ করে, কখন বা কেন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে, এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে সচেতনভাবে ভাবি না। এ কাজটাই করার চেষ্টা করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা।
জ্ঞানচর্চার একটি পৃথক শাখা হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত সবসময় ছিল না। এটির জন্ম হয়েছিল ইউরোপে, যখন শিল্পায়নসহ বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ইউরোপীয় সমাজসমূহ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। পথিকৃৎ সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করতেন যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে যেভাবে অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশ্ব-্রব্রহ্মান্ড ও জীবজগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজকে বস্তুনিষ্ঠভাবে জানা সম্ভব।
সেজন্য চাই যথাযথভাবে নিরূপিত প্রত্যয়, তত্ব ও গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ। এভাবে পরিবর্তনশীল ইউরোপীয় সমাজসমূহকে ভাল করে জানা ও বোঝার তাগিদ থেকে জন্ম হয়েছিল সমাজবিজ্ঞানের। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের অন্যতম ছিলেন ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ডূর্খাইম, যার চিন্তাভাবনা সরাসরি প্রভাবিত করেছিল ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা র্যাডক্লিফ-ব্রাউনকে। ফলে অনেক দিক থেকে ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল সমাজবিজ্ঞানের আদলেই।
দু”য়ের মধ্যে মূল পার্থক্য যা ছিল তা হল, যেখানে সমাজবিজ্ঞানীদের নজর ছিল শিল্পায়িত সমাজগুলোর প্রতি, সেখানে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ইউরোপের উপনিবেশগুলোতে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত সরল বা আদিম বলে বিবেচিত সমাজগুলোকে। নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এ ধরনের সমাজে ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞন গড়ে উঠেছিল সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। ফলে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমাজের সমাজবিজ্ঞানের আদলেই।
দুয়ের মধ্যে মূলের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তারা দেখার চেষ্টা করেছেন, বংশধারা নানা বেখনেহ ব্যবস্থা প্রভৃতি কিভাবে উৎপাদন, বণ্টন, ক্ষমতা, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে রোগের উপনিবেশগুলোতো ্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সূচনাকালেও গবেষকদের দৃষ্টি ছিল প্রযুক্তি বা সামাজিক কৃত সরল বা আদিম বলে[রে অপেক্ষাকৃত “আদিম” বলে বিবেচিত সেদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের প্রতি। বিবেচ্তি সমাজওলোকে।
তারা “সংস্কৃতির ধারণাকে কেন্দ্র করে তাদের গবেষণা ও লেখালেখি সংগঠিত বলে বিবেচিত সেদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের প্রতি। পার্থক্য ছিল এই যে, তাঁরা সংস্কৃতির ধারণাকে কেন্দ্র করে তাঁদের গবেষণা ও লেখালেখি সংগঠিত করেছিলেন।
করোছলেনা বলা বাহুল্য, প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তার থেকে ভিন্ন বা ব্যাপকতর অর্থে নৃবিজ্ঞানীরা শব্দটিকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, প্রচলিত ব্যবহারে সংস্কৃতি শব্দটি নৃত্য-গীত জাতীয় বিষয়কেই নির্দেশ করে। আমরা যখন কোন “সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান’-এর কথা বলি, অথবা যখন কোন ব্যক্তি বা পরিবারকে “সংস্কৃতিমনা” হিসাবে চিহ্নিত করি, তখন শব্দটিকে এ ধরনের একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করি।
ইংরেজীসহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায়ও সংস্কৃতির সমার্থক শন্দসমূহ শুরুতে মূলতঃ এরকম প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হত, ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশকে তথা বিভিন্নসমাজকে সাংস্কৃতিক মানদন্ডে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হিসাবে দেখার প্রবণতা ছিল। বিশেষ করে ও্পনিবেশিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া ইউরোপীয় বংশোভভূত শ্বেতাঙ্গ মানুষদের চোখে উপনিবেশসমূহের আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতি ছিল খুবই নিয়মানের।
সাধারণভাবে প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজের সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি আচার-প্রথা ইত্যাদি-_অর্থাৎ এক কথায় তার নিজের সংস্কৃতি-স্বাভাবিক বলে মনে হয়, এবং ভিন্ন কোন সংস্কৃতির মুখোমুখি হলে সেটার অনেক কিছুকে অস্বাভাবিক বা অদ্ভূত বলে মনে হতে পারে। এই প্রবণতাকে নৃবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন স্বজাতিকেন্দ্রিকতা (ethnocentrism)। মানুষ হিসাবে একজন নৃবিজ্ঞানীর মধ্যেও স্বজাতিকেন্দ্রি প্রবণতা থাকতে পারে, যা ভিন্ন একটি সংস্কৃতিকে জানতে বুঝতে গেলে অন্তরায় হয়ে দীড়াতে পারে, বিশেষ করে তা যদি হয়
আদিম বলে বিবেচিত কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। এই প্রেক্ষিতে আধুনিক মার্কিন নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঞ্জ বোয়াস ও তার অনুসারীরা “সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ” (cultural relativism) নামে পরিচিত হয়ে ওঠা একটি দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দিয়েছিলেন, যেটার মোদ্দা কথা হল কোন ভিন্ন সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করতে হলে এঁ সংস্কৃতির ধারক বাহকদের দৃষ্টিকোণ থেকেই সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানার এবং ভাল করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে “সমাজ ও “সংস্কৃতি” ধারণার আপেক্ষিক গুরুত নিরূপণের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থেকে থাকতে পারে, কিন্তু কোন ধারাতেই একটি ধারণাকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটির উপর জোর দেওয়া হয় নি। (মানুষ সংস্কৃতি শেখে সমাজের সদস্য হিসাবে, কাজেই সমাজের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সংস্কৃতির কথা বলা অর্থহীন। আবার সংস্কৃতির ধারণা বাদ দিলে মানব সমাজের বৈশিষ্ট্য বোঝা সম্ভব না, কারণ মানুষ ছাড়াও সমাজবদ্ধ প্রাণী আরো রয়েছে, কিন্তু একমাত্র মানবসমাজের ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির ধারণা প্রযোজ্য।)
উভয় ধারাতেই মূলতঃ আদিম বলে বিবেচিত জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একদিকে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের চাপের মুখে আদিবাসী আমেরিকানরা বিলুপ্ত বা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আগেই সেসব জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা সম্ভব বিস্তারিত ও নিখুঁত দলিল তৈরী করার ব্যাপারে মার্কিন নৃবিজ্ঞানীরা বিশেষ তাগিদ বোধ করেছিলেন।
একইভাবে ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের নৃবিজ্ঞানীরাও মনোযোগী ছিলেন ও্পনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত “আদিম” জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করার ব্যাপারে। এভাবে আটলান্টিকের উভয় পারের নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠীদের সার্বিক জীবন যাত্রার ধরন, তাদের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনৈতিক সংগঠন, ধমীয়ি বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার একটা এতিহ্য তৈরী হয়।
এভাবে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিন্তিতে বিভিন্ন সমাজ বা সংস্কৃতি সম্পর্কে আলাদা আলাদা বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে সামষ্টিকভাবে, বা এ প্রক্রিয়ায় রচিত কোন গ্রন্থকে, নৃবিজ্ঞান এথনোগ্রাফি বলা হয় (enthnography: এই শব্দের প্রথম উপাদান, ethno-, গ্রীক ভাষা থেকে উদ্ভূত, যার বাংলা অর্থ করা যেতে পারে ‘জাতি’ বা ‘জনগোষ্ঠী”; -graphy বলতে বোঝায় লিখার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি)। এখনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের কর্মকান্ডের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে এথনোগ্রাফি রচনা করা, যদিও সমকালীন এথনোগ্রাফিগুলো আগের মত শুধুই তথাকথিত আদিম সমাজগুলোকে ঘিরে তৈরী করা হয় না।
নৃবৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের একটি গুরত্তপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে এথনোগ্রাফি-চর্চার প্রসারের পেছনে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সমাজের তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের একটি ভান্ডার গড়ে তোলা। উনবিংশ শতাব্দীতেই এথনোলজি (ethonology) বা জাতিতত্ত্ব নামে পরিচিত নৃবিজ্ঞানের একটি বিশেষায়িত শাখা গড়ে উঠেছিল এ ধরনের তুলনামূলক অধ্যয়নকে ঘিরেই।
তবে তখন যে ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে জাতিততুবিদরা তুলনামূলক বিশ্লেষণের কাজ করতেন – বণিক, উপনিবেশিক প্রশাসক, পরিব্রাজক, মিশনারী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য – সেগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। এই প্রেক্ষিতে নূতন প্রজন্মের প্রশিক্ষিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের রচিত এথনোগ্রাফিগুলি জাতিতাত্তিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তথ্যের অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে।
সেই সূত্রে এথনোগ্রাফি ও এথনোলজিকে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দুইটি পরস্পরসম্পর্কিত ক্ষেত্র বা শাখা হিসাবে অনেকে চিহিতিত করেছেন, আবার অনেকে এথনোলজি কথাটা কমবেশী সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সমার্থক হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। তবে সময়ের সাথে সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সমার্থক হিসাবে বা এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে এথনোলজি নামের ব্যবহার প্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে বিষয়-ভিত্তিক বিশেষায়নের মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, ধর্মের নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি আলাদা আলাদা ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।
বিংশ শতাদ্বীর দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপীয় ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলো গুটিয়ে নেওয়া হয়েছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাগ্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসারের মুখে। এই প্রেক্ষিতে স্বাধীনতাকামী বা সদ্যস্বাধীন দেশগুলোতে নৃবিজ্ঞানীদের উপস্থিতি প্রশ্নের মুখে পড়তে শুরু করে । এমন অভিযোগ উঠতে থাকে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান আসলে উঁপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষেই কাজ করে।
অন্যদিকে, খোদ পশ্চিমা দেশগুলোতেও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, যেমন ষাট ও সত্তরের দশকে সংখ্যালঘু, নারী ও তরুণদের অধিকারের প্রশ্নে অনেকে সোচ্চার হতে শুরু করে। এই ধরনের পরিছিতিতে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের মত নৃবিজ্ঞানীরাও অনেকে নিজেদের জ্ঞানচর্চার এরতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তলিয়ে দেখতে শুরু করেন।
এই আত্মসমীক্ষার প্রক্রিয়ায় সব নৃবিজ্ঞানী সমানভাবে শামিল না হলেও ক্রমশঃ এই উপলব্ধি ব্যাপকতা পেতে শুরু করে যে, “আদিম সমাজ’- কেন্দ্রিক নৃবিজ্ঞান চর্চার দিন ফুরিয়ে গেছে। ফলে পূর্বের এতিহ্য থেকে সরে এসে অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীই গবেষণার নূতন ক্ষেত্র, নূতন বিষয়, নৃতন পদ্ধতি ও নৃতন তাত্তিক কাঠামোর অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলাফল স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা যাবে না, তবে সংক্ষেপে কিছু প্রবণতার কথা উল্লেখ করা যায়।
সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেন সম্ভাব্য সব ধরনের গবেষণাক্ষেত্রে – সেটা হতে পারে কৃষক অধ্যুষিত কোন গ্রাম, শহরের মধ্যবিত্ত-অধ্যুষিত কোন এলাকা, কোন বাণিজ্যিক কেন্দ্র বা শিল্পাঞ্চল। এগুলো হল বাহ্যিক পরিসরে নৃবিজ্ঞানীদের বিচরণের নৃতন ক্ষেত্র। গবেষণার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা তাত্বিক ও পদ্ধতিগতভাবেও সমকালীন নৃবিজ্ঞানীদের বিচরণের পরিধি অনেক বেশী উন্মুক্ত। পরিবারে লিঙ্গীয় অসমতা থেকে শুরু করে বিশ্বায়ন, সব ধরনের বিষয় নিয়ে তারা গবেষণা করেন।
তাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে কেউ নিজেকে চিহ্নিত করতে পারেন নারীবাদী হিসাবে, পরিবেশবাদী হিসাবে, বা উত্তর-আধুনিকতাবাদী হিসাবে। নৃবিজ্ঞানী পরিচয়ধারী এমন গবেষককেও আপনি খুঁজে পাবেন যিনি “মাঠে? নয়, পরতিহাসিক দলিলপত্রের সংগ্রহশালাতেই সময় কাটাচ্ছেন। মোট কথা, সমকালীন প্রেক্ষিতে একজন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী কোন্ কোন্ দিক থেকে একজন অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা ইতিহাসবিদের থেকে আলাদা, তা সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যাবে না।
সারাংশ:
সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক হবিজ্ঞান হচ্ছে নৃবিজ্ঞান চচার্র যথাক্রমে বিটিশ ও মাকিন এতিহোর সাথে সম্পকিতি দুটি ঘনিষ্ঠ ধারা।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানেরই সূচনা হয়েছিল সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বা সামাজিক এতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি সম্পকে উনবিংশ শতাব্দীতে এচলিত বিভিন্ন অনুমাননিভর তত্ত্বের বিরোধিতা করে প্রত্যক্ষ পরর্বেক্ষণের মাধ্যমে উপাত সংগ্রহের উপর জোর দেওয়ার মাধামে। সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে যথাক্রমে ‘সমাজ’ ও ‘সংস্কৃতি’ প্রত্যয়ের উপর প্রাধান দেওয়া হলেও উভয় ধারার নৃবিজ্ঞােনীরাই এই বিষয়গুলি অধ্যয়নের জন্য তথাকথিত আদিম জনগো্ঠীদের উপরই বেশী নজর দিয়েছিলেন।
মাকিনি ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে একই বৃহত্তর ধারার আন্তর্গত হিসাবে গণ্য কর৷ হয়, যাকে সামাজিক-সাংক্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসাবে অনেকেই অভিহিত করে থাকেন।
মাকিন যুক্রাে সাংস্কৃতিক হৃবিজ্ঞানের সূচনাকালেও গবেষকদের দৃষ্টি ছিল এয়ুক্তি বা সামাজিক সংগঠনের ধরন অনুসারে অপে্গকৃত ‘আদিম’ বলে বিবেচিত সেদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের এরতি।ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও মাকিন ধারার সাংস্কৃততিস নৃবিজ্ঞানে ‘সমাজ’ ও “সংস্কৃতি ধারণার আপেক্ষিক গুরণ্ত নিরূপণের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থেকে থাকতে পারে, কিত কোন ধারাতেই একটি ধারণাকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটির উপর জোর দেওয়। হয় নি। উভয় ধারাতেই মূলতঃ আদিম বলে বিবেচিত জনগোষ্ঠীদের সম্পকে ধ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব তথ্য সংগরহের উপর জোর দেওয়। হয়েছে।
সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক হৃবিজ্ঞানীর৷ কাজ করেন সম্ভাব্য সব ধরনের গবেষণাক্ষেত্রে – সেটা হতে পারে কৃষক অধ্যুষিত কোন এম, শহরের মধ্যবিত-অধ্যষিত কোন এলাকা, কোন বাণিজ্যিক কেন্দ্র বা শিল্পাঞ্চল। গবেষণার বিষয় নিধার্রণের ক্ষেত্রে বা তাতিক ও পদ্ধাতিগতভাবেও সমকালীন নৃবিজ্ঞানীদের বিচরণের পরিধি অনেক বেশী উন্মুক।
ভাষাতত্ত্ব নৃবিজ্ঞান
ভাষাতত্ত্ব নৃবিজ্ঞান নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পাঠটি “নৃবিজ্ঞান পরিচিতি”র বিষয়ের একটি পাঠ। নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান হল ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করা হয়।

ভাষাতত্ত্বঃ
ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হল, আপনি নিশ্চয় জানেন বা ধারণা করতে পারবেন,ভাষা। বলা বাহুল্য, এখানে ভাষা বলতে শুধু মানব ভাষার কথাই বলা হচ্ছে। কাব্যিক উপমা হিসাবে ‘পশুপাখির ভাষা” কথাটা আমরা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই ভাষার অধিকারী, কাজেই আলাদাভাবে “মানব ভাষা” বলার দরকার পড়ে না। ভাষা মানব সমাজে তথ্য ও ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম। পশুপাখিরাও বিভিন্ন ডাক ব্যবহার করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের যোগাযোগ ব্যবস্থার (communication sustem) সাথে মানব ভাষার কিছু মৌলিক ও গুরুত্পূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।
আপনি হয়তবা লক্ষ্য করেছেন, পশুপাখিরা পরিস্থিতি ভেদে বিভিন্ন ডাক ব্যবহার করে, মানুষের ভাষায় যেগুলোর অর্থ হতে পারে অনেকটা এধরনের: “কাছে এসো না, এটা আমার!’, “সাবধান, বিপদ!”, “আমি এইখানে, তুমি/তোমরা কোথায়?” “বাচাও!” ইত্যাদি।
পশুপাখিদের বেলায় এধরনের ডাকের সংখ্যা সীমিত এবং জৈবিকভাবে পূর্বনির্ধারিত, অর্থাৎ একই প্রজাতির কোন পশু বা পাখি সর্বত্রই সীমিত সংখ্যক কিছ অভিন্ন ডাক ব্যবহার করে। একটু চিন্তা করলেই দেখবেন মানুষের বেলায় এক্ষেত্রে রয়েছে একটা বিরাট পার্থক্য। কোন একটা নির্দিষ্ট বস্তুকে আমরা কি নামে ডাকব, কোন্ পরিস্থিতিতে কি ধরনের শব্দ বা বাক্য উচ্চারন করব, তা জৈবিকভাবে পূর্বনির্ধারিত থাকে না।
প্রতিটা মানুষই ভাষা শেখে জন্মের পর। একজন শিশু পানিকে ‘পানি’ বলতে শিখবে, না “জল” বা “ওয়াটার, তা নির্ভর করে সে কোন্ সামাজিক পরিবেশে জন্মেছে, তার উপর। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে ভাষা মানুষকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দেয়। প্রতিটা ভাষাতেই সীমিত সংখ্যক কিছু মৌলিক ধুনি ব্যবহৃত হয় (যেগুলোর সংখ্যা সাধারণত ২৫-৩০টা বা বড়জোর ৫০টা হয়)।
কিন্তু প্রতিটা ভাষাতেই এই সীমিত সংখ্যক ধুনিকে বিভিন্ন ভাবে মিলিয়ে হাজার হাজার শব্দ ব্যবহার করা হয় বা প্রয়োজনে নূতন নৃতন শব্দ তৈরী করা যায়, এবং সেই শব্দ গুলোকে নানানভাবে মিলিয়ে প্রায় অসীম সংখ্যক বাক্য তৈরী করা যায়।
ফলে ভাষার মাধ্যমে দূরের-কাছের, অতীতের-ভবিষ্যতের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ইন্দরিয়াতীত, সম্ভব-অসম্ভব অসংখ্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করার, তথ্য বিনিময়ের যে ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছে, এ ধরনের ক্ষমতা
প্রাণীজণতে অন্য কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না।
মানুষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে ভাষার স্বরূপ অধ্যয়ন ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি লক্ষ্য। এই স্তরে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাষার পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামান না, বরং সকল ভাষার অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি, সেদিকেই তাদের দৃষ্টি থাকে।
অন্যদিকে ভাষাবিজ্ঞানীরা কোন নির্দিষ্ট ভাষার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাষার সম্পর্ক ও পার্থক্যও অধ্যয়ন করেন। কোন ভাষার মৌলিক ধূনিগুলো কি কি, ধুনিগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি কি, এসব বিষয় অধ্যয়নের জন্য তৈরী হয়েছে ধৃনিতত্ব।
অন্যদিকে ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামো, ভাষার অর্থময় দিক, ইত্যাদি অধ্যয়নের জন্যও ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাদা ক্ষেত্র বা শাখা রয়েছে। ভাষার অভ্যন্তরীণ কাঠামো ছাড়াও ভাষা ব্যবহারের সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভাষার পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি, প্রভৃতি বিষয়ও অধ্যয়ন করা হয়।
ভাষাতত্ত্বের এধরনের বিভিন্ন দিক রয়েছে যেগুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা বরং যেদিকে নজর দেব তা হল নৃবৈজ্ঞানিক পরিসরে ভাষাতত্ত্ব চর্চার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট।
নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ
নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের পেছনে যে অনুসন্ধিৎসা কাজ করেছে, তা একভাবে অতি পুরাতন। ‘আমরা কোত্থেকে এলাম? এই দুনিয়ায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? কে কোথায় যাচ্ছি?’ এ ধরনের প্রশ্ন কোন না কোন আকারে সম্ভবত উচ্চারিত হয়েছে পৃথিবীর বুকে চিন্তাক্ষম মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকেই। প্রায় প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু ‘মিথ’ বা সৃষ্টিকাহিনী চালু রয়েছে।
এসব কাহিনী যে সবসময় সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে তা নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় বা পৌরাণিক ব্যাখ্যার মাধ্যমেই মানব প্রকৃতি ও উৎপত্তি-রহস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সাধারণভাবে খোঁজা হয়েছে। সেদিক থেকে নৃবিজ্ঞানের আবির্ভাবকে দেখা যেতে পারে বিজ্ঞানের আলোকে নিজের সম্পর্কে মানুষের অতি পুরাতন কিছু প্রশ্নের নূতন উত্তর খোঁজার সংঘবদ্ধ প্রয়াস হিসাবে, যা সম্ভব হয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে, পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এ ধরনের চর্চার অনুকূল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আবহ তৈরী হওয়ার পর।
নৃবিজ্ঞানকে অনেক সময় ‘অন্যকে অধ্যয়নের বিজ্ঞান’ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই ‘অন্য’ হতে পারে পুরো মানব প্রজাতির প্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রাণী, বা বর্তমান কালের মানুষদের প্রেক্ষিতে সুদূর অতীতের মানুষেরা, বা নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তকদের চোখে সভ্যতার মাপকাঠিতে তাদের নিজেদের সমাজ থেকে পিছিয়ে থাকা অন্যরা। আসলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের নিজের সম্পর্কে জানার কৌতুহল আর অন্যকে জানার কৌতুহল অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।
অন্যকে জানার মাধ্যমে, বা ‘অন্য কে?” এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমেই মানুষ সর্বত্র ‘নিজ’ সম্পর্কে ধারণা তৈরী করেছে। সকল মানব সমাজেই বিভিন্ন আকারে “আমরা” ও “ওরা” ধরনের ভিন্নতার বোধ তৈরী করা হয়। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রাচীন কালের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি।
এই প্রেক্ষিতে ‘ইতিহাসের জনক’ বলে খ্যাত খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসকে কোন কোন নৃবিজ্ঞানী নিজেদেরও পূর্বসূরী হিসাবে গণ্য করেন, কারণ গ্রীস ও পারস্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের যে ইতিহাস তিনি লিখেছিলেন, তাতে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে লব্ধ নিজের অভিজ্ঞতাসহ বিভিন্ন তথ্য তিনি যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ সহকারেই উপস্থাপন করেছিলেন। কোন কোন নৃবিজ্ঞানী আবার প্লেটো বা এ্যারিস্টটলের মধ্যে নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দার্শনিক ভিত্তির উৎস খুঁজে পান।
এমন একটা গল্প চালু আছে যে, মানুষের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে প্লেটো ও তাঁর শিক্ষার্থীরা মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, ‘মানুষ হচ্ছে একটি পালকবিহীন দ্বিপদ প্রাণী’। এ কথা শুনে অন্য এক গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস নাকি একটি মোরগের সকল পালক উঠিয়ে সেটাকে প্লেটোর সভায় হাজির করে বলেছিলেন, ‘প্লেটোর মানুষ’, যার প্রেক্ষিতে উক্ত সংজ্ঞায় সংশোধনী আনা হয় বাড়তি একটি শর্ত যুক্ত করে: ‘নখর- বিহীন’।
একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের সার্বিক প্রেক্ষাপট অবশ্য তৈরী হয়েছিল আরো অনেক পরে, যা আমরা ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মোটামুটি বিগত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের আলোকে দেখতে পারি।
আজ থেকে পাঁচশ’ বছরের কিছু আগে সংঘটিত কলম্বাসের নৌ- অভিযাত্রার মাধ্যমে ইউরোপীয়রা তখন পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণ অজানা নূতন নূতন ভূখন্ডের খোঁজ পায়– ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সহ দুইটি বিশাল মহাদেশ–যেগুলিকে তারা একত্রে ‘নূতন বিশ্ব” (New World) নামে অভিহিত করতে শুরু করে। এই ‘নূতন বিশ্বের সন্ধান লাভ ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের পথ খুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের চিন্তা-চেতনাতেও বিপুল আলোড়ন তুলেছিল।
তখন পর্যন্ত অধিকাংশ ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা বাইবেলের ভিত্তিতেই চেনা জগতকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই নূতন বিশ্বের অস্তিত্ব বা সেখানকার মানুষদের উৎস ব্যাখ্যার জন্য বাইবেল থেকে স্পষ্ট কোন সূত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। অন্যদিকে প্রায় একই সময়কালে পোলিশ জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস এ ধারণা প্রথম নিয়ে আসেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, যেটা গ্যালিলিওর মাধ্যমে আরো প্রতিষ্ঠিত হয়।
আপনি নিশ্চয় জানেন যে গ্যালিলিও তার মতামতের জন্য শাস্তি ও হয়রানির শিকার হয়েছিলেন তৎকালে ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত চার্চ কর্তৃপক্ষের হাতে, যারা গ্যালিলিওর সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকে মেনে নিতে পারে নি, কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ভাবা হত মানুষ ও পৃথিবীকেই।
তবে নানা কারণে চার্চের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না পুরাতন বিশ্ববীক্ষার আধিপত্য টিকিয়ে রাখা। কারণ সময়টা ছিল ইউরোপীয়দের জন্য নূতন করে জেগে ওঠার, বা রেনেসাঁর, যা ইতালীতে সূচিত হয় প্রাচীন গ্রীসের শিল্প, সাহিত্য ও দর্শন পুনরাবিস্কারের মাধ্যমে।
পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রণ প্রযুক্তির উদ্ভাবন সুগম করে দিয়েছিল নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার রাস্তা। রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বেরিয়ে তৈরী হয় নূতন নূতন সংস্কারবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়, যারা সামগ্রিক ভাবে প্রটেস্টান্ট নামে পরিচিত। এসব পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সংঘটিত হয় বড় ধরনের দু’টি রাজনৈতিক বিপ্লব: আমেরিকান বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব, যেগুলি যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের ভিত্তি নাড়িয়ে বা ভেঙে দেয়। ততদিনে শিল্প বিপ্লবও শুরু হয়ে গেছে, যা গোটা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনে।
অভিজাত সামন্তশ্রেণীর জায়গায় ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসে নগর-ভিত্তিক একটি শ্রেণী – বুর্জোয়া (‘শহুরে’) পুঁজিপতিরা, অর্থাৎ কল-কারখানা, ব্যাংক ইত্যাদির মালিকরা। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই চিন্তাজগতেও ঘটে যায় একধরনের বিপ্লব – এনলাইটেনমেন্ট (Enlightenment) নামে পরিচিত বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুক্তি, বিজ্ঞান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটা দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়।
অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক-লেখক-চিন্তাবিদদের মধ্যে অনেকেরই নাম উল্লেখ করা যায় যেমন, মন্তেস্থ্য, – জাঁ-জাক রুশো, ভিকো প্রমুখ – যাদেরকে নৃবিজ্ঞানীদের কেউ না কেউ তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্বসূরীদের – তালিকায় রাখেন।
এনলাইটেনমেন্ট চিন্তার একটা কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল এই যে, মানব সমাজ সময়ের সাথে সাথে ক্রমবিকশিত হয়। মানব ‘প্রগতি’র ইতিহাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে অনেকেই নজর দিয়েছিলেন সবচাইতে আদিম হিসাবে বিবেচিত ‘বন্য’ (savage) মানুষদের দিকে, অর্থাৎ যারা শুধু শিকার ও ফলমূল আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। মানব সমাজ প্রগতির পথে ক্রমান্বয়ে শিকার থেকে পশুপালন হয়ে কৃষি ও বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে, এই ধারণা বেশ ব্যাপকতা পেয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই।
‘এ্যান্থ্রোপলজি’ শব্দটা অবশ্য তখনো মূলতঃ ‘দৈহিক নৃবিজ্ঞান’ বলতে এখন আমরা যা বুঝি, সে অর্থেই ব্যবহৃত হত। অন্যদিকে এথনোগ্রাফি ও এথনোলজি বা সমতুল্য অন্য কোন নামে গড়ে ওঠা জ্ঞানচর্চার কিছু ধারার প্রসার ঘটতে থাকে (বিশেষতঃ জার্মানভাষী দেশগুলোসহ মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অন্যত্র) যেগুলোর নজর কেবল ইউরোপের বাইরের ‘আদিম’ সমাজগুলোর প্রতি নয়, ইউরোপের ভেতরকার জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিও ছিল। এই ধারাগুলোর অনেকটাই পরবর্তীতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আওতায় চলে এসেছে।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বন্য ও আদিম হিসাবে চিহ্নিত সমাজগুলোর ব্যাপারে ইউরোপীয়দের কৌতুহল শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ব্যাপার ছিল না, এর সাথে যুক্ত ছিল রোমান্টিকতার ধারাও – যার ফলে কারো কারো কাছে ‘বন্য’রা হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক সারল্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

বিবর্তনবাদ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞান
একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেই ঘটেছিল। তখনো নৃবিজ্ঞান চর্চার মূল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র ছিল ইউরোপের একাধিক দেশ ও আমেরিকায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতিতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (ethnographical museums) ও জাতিতাত্ত্বিক সমিতি (ethnological societies)। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন তথ্য ও বস্তুসামগ্রীর যে বিশাল সংগ্রহ গড়ে উঠছিল, সেগুলির শ্রেণীকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য দরকার ছিল একটা সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিবর্তনবাদী চিন্তাচেতনার প্রসার এই চাহিদা মেটায়।
বিবর্তনবাদের মূল কথা ছিল, মানব সমাজ সর্বত্রই কিছু সাধারণ ও বিশ্বজনীন নিয়ম অনুসারে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হয়ে চলছে, সরল ও আদিম রূপ থেকে ক্রমশ জটিল ও উন্নত রূপ ধারণ করছে। বিবর্তনবাদীদের লক্ষ্য ছিল সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের আদিরূপ চিহ্নিত করা, এবং তা থেকে ধাপে ধাপে পরবর্তী রূপগুলোর ক্রমবিকাশের সূত্র খুঁজে বের করা।
যদিও বিবর্তন শব্দটা শুনলে আমরা অনেকেই সর্বাগ্রে ডারউইনের কথাই ভাবি, প্রকৃতপক্ষে জৈবিক বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার আগেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারণা সংগঠিত হতে শুরু করেছিল।
তবে ডারউইন যখন ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত Origin of Species গ্রন্থের মাধ্যমে ইঙ্গিত দেন, এবং কিছু বছর পরে The Descent of Man গ্রন্থে (১৮৭১) স্পষ্ট করেই বলেন যে, বানর জাতীয় কোন প্রাণীর ক্রমবিবর্তিত রূপ হল আজকের মানুষ, এই তত্ত্বটা চিন্তাজগতে গভীর ও সুদূরপ্রসারী আলোড়ন তুলেছিল।
নৃবিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানকান্ড
নৃবিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানকান্ড নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পাঠটি “নৃবিজ্ঞান পরিচিতি” বিষয়ের একটি পাঠ। নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের যোগসূত্র সম্পর্কে আগের পাঠগুলো থেকেই কিছুটা ধারণা আপনি পেয়েছেন। পৃথিবীর সকল স্থানের ও সকল কালের মানুষদের অধ্যয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানকে সংগঠিত করার প্রয়াসে নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জ্ঞানকান্ড থেকে অনেক কিছু নিয়েছেন।

দৈহিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে প্রাগৈতাহিসক যুগের মানুষের জীবাশ্ম ও তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের বয়স নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত কৌশলগুলো এসেছে ভূতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান ও রসয়ানশাস্ত্র থেকে। প্রাগৈতাহিসক মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন চিহ্নের সাথে প্রাপ্ত অন্যান্য জৈব নমুনা বিশ্লেষণের কাজে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া হয়।
আর বলা বাহুল্য, মানব বিষয়ক যত ধরনের বিজ্ঞান আছে, তার প্রায় প্রতিটার সাথে নৃবিজ্ঞানের কোন না কোন যোগসূত্র রয়েছে। তবে মানব বিষয়ক অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সাথে নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য হল এই যে, অন্যান্য জ্ঞানকান্ড যেখানে বিশেষ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিষয়বস্তুর সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে, সেখানে নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সমন্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং বিষয়বস্তুর কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা বেঁধে দেওয়া নেই।
বাস্তবে অবশ্য নৃবিজ্ঞানকে মানব বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলার দিন আর নেই। যেমন, আজকাল দৈহিক বা জৈবিক নৃবি-জ্ঞানের সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সংযোগ খুবই ক্ষীণ হয়ে গেছে। অতীতে বিবর্তনের ধারণা বা ‘আদিম সমাজ’-কেন্দ্রিক গবেষণা বিভিন্ন শাখার নৃবি-জ্ঞানকে সমন্বিত করতে সহায়তা করেছিল, কিন্তু সে অবস্থা এখন আর দেখা যায় না। কাজেই নৃবি-জ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে দেখতে হবে আমরা কোথাকার ও কবেকার কোন ধরনের নৃবি-জ্ঞান নিয়ে কথা বলছি।
এক্ষেত্রে আমরা মূলতঃ নজর দেব সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবি-জ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সম্পর্কের উপর। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টা মনে রাখা সুবিধাজনক হবে তা হল, নৃবি-জ্ঞানের মতই অন্যান্য জ্ঞানকান্ডেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। ফলে সাধারণভাবে বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একই সাথে প্রথাগতভাবে চর্চিত বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডের রূপান্তর ও মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠছে নূতন নূতন নামে পরিচিত জ্ঞানকান্ড, যেগুলোকে সনাতনী কোন শ্রেণীকরণ অনুযায়ী সাজানো যায় না।
নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান:
সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে তিনটি সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানকান্ড হল সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যেগুলির সাথে ঐতিহ্যগতভাবে নৃ-বিজ্ঞানের পার্থক্য গড়ে উঠেছে এক ধরনের বিদ্যাজাগতিক শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজকে মোটা দাগে ভাগ করার জন্য কিছু জোড় পদ ব্যবহার করা হয়, যেমন আদিম-আধুনিক, সরল-জটিল, অসাক্ষর- সাক্ষর, প্রাক-শিল্পযুগীয়-শিল্পায়িত ইত্যাদি।
এগুলির দ্বিতীয় পদসমূহ দিয়ে নির্দেশিত সমাজগুলোর প্রতিই মূলতঃ সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নজর কেন্দ্রীভূত থেকেছে। অন্যদিকে নৃবি-জ্ঞানে বেশী নজর দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত তালিকার প্রথম পদগুলো দিয়ে চিহ্নিত সমাজগুলোর প্রতি।
এছাড়া সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধ্যয়নের মূল বিষয় হিসাবে যথাক্রমে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি ধারণা দিয়ে চিহ্নিত পৃথক পৃথক ক্ষেত্র বেছে নেওয়া হলেও নৃবি-জ্ঞানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের কোন কোন একটি দিকের উপর আলাদা করে বেশী নজর দেওয়া হয় নি।
মনে করা হয় যে, নৃবি-জ্ঞানীরা ঐতিহ্যগতভাবে যে ধরনের সমাজ নিয়ে গবেষণা করতেন, সে ধরনের সমাজে এই বিষয়গুলোকে বাস্তবে সবসময় আলাদা করেও দেখা সম্ভব ছিল না। কিছু উদাহরণ দিলেই নৃবি-জ্ঞানের সাথে আলোচ্য অন্য তিনটি সামাজিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্যগত পার্থক্যগুলো বোঝা যাবে।
নৃবি-জ্ঞানীরা সমাজের সংগঠন দেখতে গিয়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিয়ে ও বংশধারার প্রতি প্রচুর মনোযোগ দিয়েছেন, কারণ সরল বা আদিম বলে বিবেচিত যে ধরনের সমাজ সম্পর্কে নৃবি-জ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভে সচেষ্ট ছিলেন, সে ধরনের সমাজের প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলোকে দেখা হয়েছে সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি হিসাবে।
এ ধরনের সমাজে বিত্ত, ক্ষমতা বা মর্যাদার তারতম্যের ভিত্তিতে প্রকট কোন সামাজিক অসমতা নৃবি-জ্ঞানীরা দেখেন নি, ফলে সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁদের সচরাচর যেতে হয় নি। পক্ষান্তরে জ্ঞাতিসম্পর্কের মত বিষয়ের তুলনায় শেষোক্ত বিষয়াদি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের অনেক বেশী মাথা ঘামাতে হয়েছে।
নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের সমাজের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক হিসাবে আলাদা করে শনাক্ত করা যায়, এমন কর্মকান্ড বা প্রতিষ্ঠানও বিরল। বরং জ্ঞাতিসম্পর্কের মত বিষয়ের সাথেই অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিষয়াবলী ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বলে মনে করা হয়।
এ ধরনের সমাজে ‘বাজার ব্যবস্থা’ বলে কিছু ছিল না বা থাকলেও সেটাই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল নির্ধারক ছিল না। ফলে যেখানে অর্থনীতিবিদরা ব্যস্ত থেকেছেন বাজার ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বোঝার কাজে, সেখানে নৃবি-জ্ঞানীদের অনেকে দেখতে চেয়েছেন বাজার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বা এর বাইরে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের সূত্র ধরে কিভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পন্ন হয়।
একইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নজরের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্র (লক্ষ্যণীয় যে, Political Science-এর বাংলা করা হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যেনবা রাজনৈতিক কর্মকান্ড একমাত্র রাষ্ট্রকে ঘিরেই সংঘটিত হয়), সেখানে নৃবি-জ্ঞানীরা এমন সমাজের কথা বলেন যাদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা বা ক্ষমতার কোন কেন্দ্রীভূত রূপ ছিল না। এ ধরনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বা রাজনীতি বলতে কি বোঝায়? এসব প্রশ্নের উত্তর নৃবি-জ্ঞানীরা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।
পদ্ধতিগতভাবে অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের সমাজ অধ্যয়নের জন্য নৃবি-জ্ঞানীরা মূলতঃ নির্ভর করেছেন এধরনের সমাজে দীর্ঘদিন বাস করে তাদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর। পক্ষান্তরে বৃহদায়তনের জটিল সমাজ অধ্যয়নের জন্য অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে জরীপ, প্রশ্নমালা, পরিসংখ্যান প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। নৃবি-জ্ঞানীরা ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় অধ্যয়নের উপর মনোনিবেশ করতে গিয়ে গুণগত উপাত্তের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীরা বৃহৎ পরিসরে প্রচুর পরিমাণ পরিমাপযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহের উপর জোর দিয়েছেন।
উপরে আলোচিত পার্থক্যগুলো অবশ্য মোটা দাগের, যেগুলো সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে আর ততটা প্রযোজ্য নয়। বিষয়বস্তু ও গবেষণাক্ষেত্র নির্বাচন বা গবেষণাকৌশলের দিক থেকে এখন অনেক নৃবি-জ্ঞানীই অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের মত করেই কাজ করছেন। এর উল্টোটাও সত্য। সমাজবিজ্ঞানীরাও অনেকে নৃবৈজ্ঞানিক ধাঁচে ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় মাঠকর্ম করেছেন। এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও সবাই এখন আর রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য রাষ্ট্রের উপর নজর কেন্দ্রীভূত রাখে না। এদিক থেকে অর্থনীতি বা রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী সংযোজনে নৃবি-জ্ঞানীরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি
সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পঠটি “নৃবিজ্ঞান পরিচিতি” বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। প্রতিটা জ্ঞানকান্ডেই নির্দিষ্ট কিছু গবেষণা পদ্ধতি রয়েছে। ভৌত ও জৈবিক বিজ্ঞানসমূহে ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। তবে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (experimental method) প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই।

দুটো রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে কি ধরনের বিক্রিয়া ঘটে, বা কোন আণুবীক্ষণিক প্রাণী সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কতটা তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, এ জাতীয় বিষয় গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব, কিন্তু একজন সামাজিক বিজ্ঞানীর পক্ষে মানব সমাজের উপর অনুরূপ কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো ব্যবহারিক দিক থেকে যেমন সমস্যাজনক, তেমনি নৈতিকভাবেও প্রশ্নসাপেক্ষ। কাজেই সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে গবেষণা বলতে সাধারণত কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা বোঝায় না।
বিশেষ কোন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য, বা কোন তত্ত্বের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ, জরীপ প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। অধ্যয়নের বিষয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুসারে প্রতিটা জ্ঞানকান্ডে বিশেষ কিছু পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেরও রয়েছে নিজস্ব কিছু গবেষণা পদ্ধতি, যেগুলোর মধ্যে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম ও তুলনামূলক পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।
মাঠকর্ম:
সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে ‘মাঠ’ বলতে বোঝায় এমন কোন স্থান বা এলাকা যেখানে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেখানে বসবাসরত মানুষদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করার এবং তাদের সাথে মেশার, কথা বলার সুযোগ রয়েছে। এভাবে পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথন, সাক্ষাতকার প্রভৃতি কৌশল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে মাঠকর্ম বা মাঠ গবেষণা বলা হয়।
ঐতিহ্যগতভাবে অধিকাংশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীই মাঠকর্ম সম্পাদন করেছেন প্রযুক্তি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিচারে অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের সমাজসমূহের মধ্যে। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী নৃবিজ্ঞানীরা যখন মাঠ গবেষণার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কোন সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করেন, তখন সেটাকে বলা হয় ‘এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম’।
পোলিশ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি ট্রাব্রিরিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জে সম্পাদিত তাঁর মাঠকর্মের ভিত্তিতে রচিত এথনোগ্রাফিক গ্রন্থ Argonauts of the Western Pacific – এর শুরুতে নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, কিভাবে সেগুলো অর্জন করা যায়, এসব বিষয়ে যে আলোচনা করেছিলেন, তা নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত।
উক্ত আলোচনায় ম্যালিনোস্কি এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মের একটি মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন: কোন জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা বা সংস্কৃতিকে জানার জন্য তাদের মাঝে কমপক্ষে একবছর থেকে, তাদের ভাষা শিখে, তাদের সাথে মিশে, ‘স্থানীয়দের চোখ দিয়ে’ ঐ সমাজ ও সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে গবেষণা এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে সেখানকার মানুষদের সাথে মিশে তথ্য সংগ্রহের কৌশলকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলা হয় (participant observation : অন্যভাবেও এর বাংলা করা হয়েছে)। নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণা এলাকায় অবস্থান নেওয়ার পর থেকে দৈনন্দিন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সযত্নে টুকে রাখতে শুরু করেন, যেগুলো (field notes) চূড়ান্ত কোন প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।
একজন বহিরাগতকে স্থানীয় মানুষরা সহজে আপন করে নেবে, এমন কোন কারণ নেই। কিভাবে স্থানীয় মানুষদের আস্থা অর্জন করা যাবে, তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। গবেষণা এলাকায় পৌঁছে প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানী তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেন তাঁর উপস্থিতিকে যতটা সম্ভব স্থানীয় মানুষদের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক (rapport) তৈরী করতে।
শুরুতে নৃবিজ্ঞানীদের সচরাচর বেগ পেতে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে, অনেকেই মুখোমুখি হন এক ধরনের ‘সাংস্কৃতিক ধাক্কা’র (culture shock)। প্রাথমিক এসব সমস্যা কাটিয়ে উঠে নৃবিজ্ঞানী চেষ্টা করেন স্থানীয় জীবনযাত্রার সাথে মানিয়ে নিতে।
একটা পর্যায়ে স্থানীয় মানুষরাও হয়ত তাঁকে অনেকটা আপন করে নেয়, বা অন্ততঃ তাঁর উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে নৃবিজ্ঞানী গবেষণা এলাকার মানুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন। এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে নৃবিজ্ঞানীরা সচরাচর কমপক্ষে একবছর গবেষণা এলাকায় থাকার চেষ্টা করতেন, যাতে ঋতুচক্রের একটা পূর্ণ আবর্তনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষদের জীবনযাত্রার ছন্দের পরিবর্তনগুলো তাঁরা পর্যাপ্তভাবে দেখার সুযোগ পান।
অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে নৃবিজ্ঞানীরা স্থানীয় মানুষদের সাথে কথোপকথন ও আলাপচারিতার মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। বাঁধাধরা কোন প্রশ্নের তালিকা মাথায় না রেখে চারপাশে যখন যা ঘটছে, সে অনুযায়ী নিয়মিত অনেক বিষয়ে তাঁরা জানতে চান। তবে প্রয়োজনানুসারে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাতকারও গ্রহণ করা হয়।
মাঠকর্ম করতে গিয়ে অনেক নৃবিজ্ঞানীই স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এমন দু’একজন ব্যক্তির সন্ধান করেন যাঁরা গবেষণা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও ব্যাখ্যা দিয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারেন। যেমন, কোন প্রবীণ ব্যক্তি হয়ত ভাল বলতে পারেন কার সাথে কে কি ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। অথবা, ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারেন এমন কোন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ হয়ত রয়েছেন।
মাঠকর্ম চলাকালে এ ধরনের ব্যক্তিরা নৃবিজ্ঞানীদের জন্য হয়ে উঠতে পারেন প্রধান তথ্যদাতা (key informant)। এছাড়া স্থানীয় মানুষদের কারো কারো বিস্তারিত জীবন ইতিহাসও (life history) নৃবিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করতে পারেন।
সংগৃহীত জীবন ইতিহাস হতে পারে এমন কোন ব্যক্তির, যাঁকে হয়ত সমাজের একজন গড়পড়তা (typical) সদস্য হিসাবে দেখা যায়, অথবা তিনি হতে পারেন স্থানীয় প্রেক্ষাপটে ব্যতিক্রমধর্মী কোন ব্যক্তি। উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য থাকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর আলোকপাত করা। এভাবে তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশলের সমন্বয়ে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্রায়তনের কোন সমাজ বা বৃহদায়তনের কোন সমাজের ক্ষুদ্র কোন অংশ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করেন।
তুলনামূলক পদ্ধতি:
আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনা (cross-cultural comparison) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি অন্যতম গবেষণা পদ্ধতি। মানব জীবনের বিশেষ কোন দিক ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে কি রূপে বিরাজমান ও ক্রিয়াশীল থাকে, তা নৃবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে।
যেমন, নারী-পুরুষের সম্পর্ক সকল সমাজেই অসম কিনা, বা এই অসমতার মাত্রায় কতটা তারতম্য দেখা যায়, কি কি বিষয়ের আলোকে সেই তারতম্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এ ধরনের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে লিঙ্গীয় সম্পর্কের বিবিধ সাংস্কৃতিক রূপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক থেকে শুরু করে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম বিভিন্ন বিষয়ে এ ধরনের তুলনামূলক পাঠ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
জরীপ:
বৃহদায়তনের কোন সমাজে গবেষণা করতে গেলে সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রায়ই জরীপের সাহায্য নিয়ে থাকেন। বিশাল কোন জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করতে গেলে সমাজের সকল সদস্যের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, ফলে চেষ্টা করা হয় পরিসংখ্যানবিদ্যার বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে পর্যাপ্ত সংখ্যক কিছু তথ্যদাতা নির্বাচন করতে, যাদেরকে সমাজের বিশেষ কোন গোষ্ঠী, শ্রেণী বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত কোন বর্গের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল বলে গণ্য করা যেতে পারে।
ধারণাটা অনেকটা এরকম, কোন পুকুরের পানিতে দূষণের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য পুকুরের সমস্ত পানি সংগ্ৰহ করার দরকার নেই, সেখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ নমুনা (sample) সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে দেখাই বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসরণীয় পদ্ধতি। একইভাবে সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর অংশবিশেষ থেকে জরীপের সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোর ভিত্তিতে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, এরকম বিভিন্ন বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করেন।
সামাজিক- সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা ঐতিহ্যগতভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম সম্পাদনের উপর জোর দিয়ে আসাতে পরিসংখ্যানবিদ্যার বিভিন্ন বিশেষায়িত কৌশলের সহায়তা নিতে তাঁদের খুব একটা দেখা যায়নি। এর অর্থ এই নয় যে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কখনো জরীপ বা পরিসংখ্যান-নির্ভর অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেন না।
তবে অনেক ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় বা লক্ষ্য এমন থাকে যে, সেখানে এ ধরনের পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর বলে গণ্য করা যায় না। যেমন, কোন এলাকায় বিশেষ কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত দূষিত পানি কতজন কি কাজে নিয়মিত ব্যবহার করে, তা মাপা সম্ভব, কিন্তু স্থানীয় প্রেক্ষিতে ‘ভালো পানি’ বা ‘খারাপ পানি’ ধরনের কোন ধারণা বিদ্যমান থাকতে পারে যেগুলো সম্পর্কে জানতে হলে নজর দিতে হবে অন্যত্র, সেখানকার সংস্কৃতির উপর।
অবশ্য সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরাও জানতে চাইতে পারেন বিবিধ কাজে পুকুরের পানি কারা কতটা ব্যবহার করে, এমন কোন বিষয় সম্পর্কে। সেক্ষেত্রে যদি বিশাল কোন জনগোষ্ঠীর উপর তাঁরা কাজ করেন, তাহলে নমুনা-ভিত্তিক জরীপের সাহায্য দরকার হতে পারে।
নৃবিজ্ঞান বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা
এই পাঠটি “নৃবিজ্ঞান পরিচিতি” বিষয়ের “সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি” বিভাগের একটি পাঠ। সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। তাঁদের বেলায় গবেষণার অর্থ হতে পারে প্রথাগত মাঠকর্মের পরিবর্তে সরকারী মহাফেজখানাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রের সন্ধান করা এবং সেসব দলিলপত্র পর্যালোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা।
সংশ্লিষ্ট সময়কালের সরকারী নথিপত্র থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত দিনপঞ্জী, চিঠিপত্র সব ধরনের দলিলই ঐতিহাসিক গবেষণায় তথ্যের ‘উৎস’ হিসাবে গণ্য হতে পারে। তবে এসব উৎস খুঁজে বের করতে পারা গবেষণার প্রাথমিক ধাপ মাত্র, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল উৎসসমূহ ভাল করে পরীক্ষা করে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা, এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খন্ডচিত্রসমূহ মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যতটা সম্ভব একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করানো।
অতীতে যখন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথাকথিত আদিম সমাজসমূহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উপর নৃবিজ্ঞানে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত, তখন অনেক নৃবিজ্ঞানীরই লক্ষ্য ছিল আদি-অকৃত্রিম অবস্থায় রয়ে গেছে, এমন জনগোষ্ঠীর সন্ধান করা। আর ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে সূচিত কোন পরিবর্তন যদি নৃবিজ্ঞানীদের চোখেও পড়ত, সেগুলোর প্রতি তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহ বা মনোযোগ দেখান নি।
সাম্প্রতিককালের ইতিহাস-মনস্ক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা তাই অনেকেই পরীক্ষা করে দেখছেন, তাঁদের পূর্বসূরীদের বর্ণিত তথাকথিত আদিম সমাজসমূহ আসলেই কতটা আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় ছিল। এ ধরনের গবেষণা থেকে সাধারণভাবে এই উপলব্ধি ব্যাপকতা
পেয়েছে যে, প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের সনাতনী বাস্তবতা হিসেবে যেসব বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অনেকক্ষেত্রে আসলে ঔপনিবেশিক সময়কালের বাস্তবতাকেই নির্দেশ করে। এ ধরনের উপলব্ধি অনেক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীকে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে।

গবেষণার রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক:
‘গিনি পিগ’ কথাটার সাথে আপনি নিশ্চয় পরিচিত। গবেষণাগারে গিনি পিগের মত প্রাণীদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় মানুষের প্রয়োজনে। এ ধরনের গবেষণার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করার লোক একেবারে বিরল নয়, যদিও সংখ্যায় তারা কম।
কিন্তু যদি এমন কথা শোনা যেত যে সামাজিক গবেষণার নামে জীবন্ত মানুষদেরই ‘গিনিপিগ’ বানানো হয়েছে, তাহলে সেটা নিশ্চয় কারো কাছে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হত না। সামাজিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় মানব সমাজের উপর এ ধরনের কোন পরীক্ষা- নিরীক্ষা চালান না ঠিকই, তবে অনেকসময় পরোক্ষভাবে তাঁরা এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকেন। যেমন, আপনি নিশ্চয় জানেন, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু স্থানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।
এসব প্রকল্প অনেকক্ষেত্রেই হয়ে থাকে পরীক্ষামূলক, যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। এমনটা অনেক সময়ই দেখা যায় যে, সমাজের কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী চায় বিশেষ কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হোক, কারণ তারা এতে নিজেরা লাভবান হবে, অন্যদিকে সেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন অন্যদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
ধরা যাক, এ ধরনের কোন বিতর্কিত প্রকল্প মূল্যায়নের কাজে একজন সামাজিক বিজ্ঞানীকে সম্পৃক্ত করা হল। তিনি কাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন? নীতিগতভাবে সামাজিক বিজ্ঞানী অবশ্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটা বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন তুলে ধরবেন।
কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানীরাও যেহেতু সমাজেরই অংশ, তাঁদেরও বিশেষ কোন মূল্যবোধ, মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে যা গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। এ ধরনের বিষয় বিবেচনা করে অনেক সামাজিক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, বস্তুনিষ্ঠ বা মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ সামাজিক গবেষণা বলে আসলে কিছু নেই, থাকতে পারে না।
এ ব্যাপারে ভিন্নমতের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, যে বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক গবেষণা পরিচালিত হয়, তা পরীক্ষা করে দেখা সামাজিক বিজ্ঞানীদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।
সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা যেহেতু ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তিক ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীদের মাঝে গবেষণা করেছেন, উপরের প্রশ্নগুলো তাঁদের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অনেক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেন যে তাঁরা একধরনের সাংস্কৃতিক অনুবাদকের ভূমিকা পালন করেন।
ঐতিহাসিকভাবে এই ভূমিকাটা হয়েছে একমুখী, অর্থাৎ পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অপশ্চিমা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোধগম্য করে তুলেছে নিজেদের সমাজে, কিন্তু এর উল্টো ভূমিকা তাঁরা সাধারণভাবে পালন করেননি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে অনেক নৃবিজ্ঞানীই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার জন্য ফরমায়েশী গবেষণার কাজ করেছেন।
এ ধরনের গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ মনে করেন যে তাঁরা গবেষণা এলাকার জনগোষ্ঠীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন, অনেক সময় তাঁরা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীদের মুখপাত্র হিসাবেও নিজেদের গণ্য করেন। তবে ইদানীং নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে এই উপলব্ধি বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, কোন জনগোষ্ঠী, সেটা আয়তনে যত ক্ষুদ্র বা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যত সরলই হোক না কেন, আসলে সম্পূর্ণ সমরূপ না। কাজেই নৃবিজ্ঞানীরা যেটাকে স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে তুলে ধরছেন, সেটা যে অনেক সময় স্থানীয় মানুষদের শুধু একটা অংশেরই দৃষ্টিভঙ্গী হতে পারে
(স্থানীয় প্রেক্ষিতে ক্ষমতাবানদের, পুরুষদের, ইত্যাদি), এই সম্ভাবনাও তলিয়ে দেখার তাগিদ স্বীকৃতি পেয়েছে। স্পষ্টতই, নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় এধরনের অনেক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া পদ্ধতিগতভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরী, যাতে করে গবেষকের একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকে গবেষণার সার্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে।
গবেষণার সারাংশ:
প্রতিটা জ্ঞানকান্ডেই নির্দিষ্ট কিছু গবেষণা পদ্ধতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেরও রয়েছে নিজস্ব কিছু গবেষণা পদ্ধতি, যেগুলোর মধ্যে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম ও তুলনামূলক পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে ‘মাঠ’ বলতে বোঝায় এমন কোন স্থান বা এলাকা যেখানে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেখানে বসবাসরত মানুষদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করার এবং তাদের সাথে মেশার, কথা বলার সুযোগ রয়েছে।
এভাবে পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথন, সাক্ষাতকার প্রভৃতি কৌশল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে মাঠকর্ম বা মাঠ গবেষণা বলা হয়। আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনা (cross-cultural comparison) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি অন্যতম গবেষণা পদ্ধতি।
মানব জীবনের বিশেষ কোন দিক ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে কি রূপে বিরাজমান ও ক্রিয়াশীল থাকে, তা নৃবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে। বৃহদায়তনের কোন সমাজে গবেষণা করতে গেলে সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রায়ই জরীপের সাহায্য নিয়ে থাকেন।
সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। প্রথাগত মাঠকর্মের পরিবর্তে সরকারী মহাফেজখানাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রের সন্ধান করা এবং সেসব দলিলপত্র পর্যালোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া পদ্ধতিগতভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরী, যাতে করে গবেষকের একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকে গবেষণার সার্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে।