আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় পারসিক সংস্কৃতি ও তার প্রভাব
পারসিক সংস্কৃতি ও তার প্রভাব
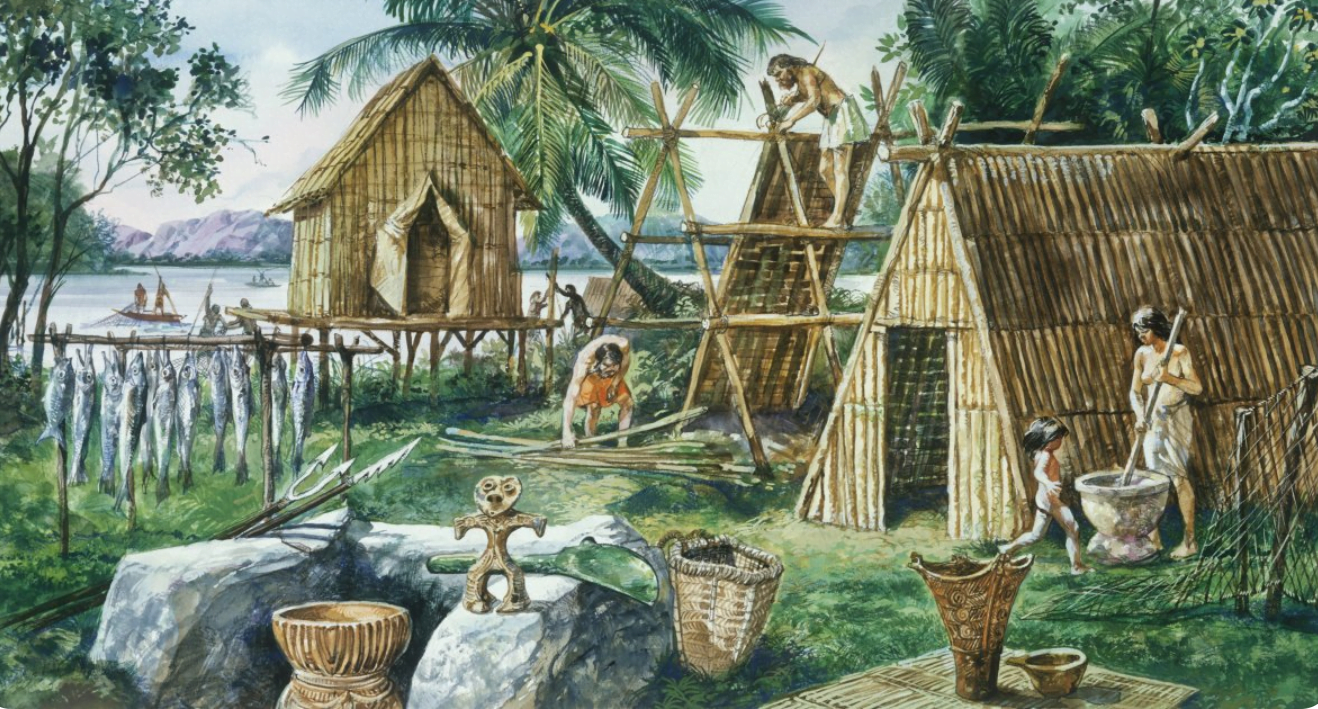
পারসিক সংস্কৃতি ও তার প্রভাব
পারসিক সংস্কৃতির অনেকগুলো উপাদানই ছিল পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর কাছ থেকে পাওয়া। মননশীলতা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। এ দু’ক্ষেত্রে পারস্য সাম্রাজ্য বিশেষভাবে মেসোপটেমিয়া, মিশর, লিডিয়া ও উত্তর প্যালেস্টাইনের কাছে ঋণী। পারসিকদের লিখনব্যবস্থা আদিতে ছিল ব্যবিলনীয় ‘কিউনিফর্ম লিখনপদ্ধতির অনুরূপ। কালক্রমে পারসিকরা আরামীয়দের বর্ণমালার ভিত্তিতে ৩১টি বর্ণবিশিষ্ট এক বর্ণমালার সৃষ্টি করে।
স্মরণ করা যেতে পারে যে, ফিনিশীয়রা সর্বপ্রথম বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতির সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারসিকদের নিজস্ব অবদান বিশেষ কিছু ছিল না, তারা মিশর ও মেসোপটেমিয়ার বিজ্ঞানকে কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেছিল। পারসিকরা অবশ্য মিশরের সৌরপঞ্জিকার কিছু সংস্কার সাধন করেছিল। লিডিয়ার আবিষ্কৃত মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনের কৃতিত্ব পারসিকদের। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন পারসিকদের মাধ্যমেই প্রথমে ঘটেছিল।
স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে পারসীকরা প্রধানত ব্যবিলনীয় ও আসিরীয় রীতি অনুসরণ করেছে, তবে এক্ষেত্রে মিশরীয় এবং গ্রীসীয় রীতির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মেসোপটেমিয়ার নির্মাণ-কৌশলের একটা মূল বৈশিষ্ট্য তথা খিলানের ব্যবহার পারসিক স্থাপত্যে দেখা যায় না। খিলানের পরিবর্তে পারসিকরা মিশরীয় রীতি অনুযায়ী স্তম্ভ ও স্তম্ভশ্রেণী ব্যবহার করেছে।
স্তম্ভের শীর্ষভাগে যে সর্পিল অলঙ্করণ পারসিক স্থাপত্যে দেখা যায় তাতে আয়োনীয় গ্রীক স্থাপত্যরীতির প্রভাব পরিস্ফুট হয়েছে। পারসিক স্থাপত্যশিল্পের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষেত্রের চেয়ে জাগতিক ক্ষেত্রেই এর বেশি প্রকাশ ঘটেছে। এ’ স্থাপত্যের প্রকাশ ঘটেছে মন্দিরনির্মাণে নয়, বরং প্রাসাদ নির্মাণে। পারসিক স্থাপত্যের প্রধান নিদর্শন হচ্ছে পার্সিপোলিসে নির্মিত সুরম্য রাজ প্রাসাদ। এ প্রাসাদ ছিল দারিয়ুস ও জারেক্সেস-এর বাসভবন ও প্রধান দফতর।
পারস্য সাম্রাজ্যের সমসাময়িক ও তার পরবর্তী সভ্যতাসমূহের ওপর পারসিক ধর্মের গভীর প্রভাব পড়েছিল। পারসিকদের এ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জরথুস্ত্র, তাই এ ধর্মের নাম দেয়া হয়েছে ‘জরথুস্ত্রবাদ’। জরথুস্ত্র খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। জরথুস্ত্রবাদ অনুসারে দু’জন শক্তিমান দেবতা বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ‘আহুর মাজদা’ হচ্ছেন মঙ্গলের দেবতা। আর আরিমান হলেন অমঙ্গলের দেবতা।
এ দু’ দেবতার মধ্যে বিরামহীন সংগ্রাম চলছে এবং শেষ পর্যন্ত আলোর দেবতা ‘আহুর মাজদা’ অন্ধকারের শক্তি আরিমানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবেন। জরথুস্ত্রবাদ অনুসারে আহুর মাজদার জয়লাভের পর সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং সৎব্যক্তিদের স্বর্গে ও দুষ্টব্যক্তিদের নরকে প্রেরণ করা হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নরকবাসীরাও উদ্ধার পাবে, কারণ পারসিক নরক চিরস্থায়ী নয়।
জরথুস্ত্রবাদ ছিল এক নৈতিক ধর্ম। এ ধর্ম অনুসারে সৎকাজে পূণ্য ছিল এবং অসৎ কাজে পাপ হত। এ ধর্মকে এক অর্থে ঐশীধর্ম বলা চলে – কারণ এ ধর্মমত অনুসারে এ ধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরের সম্পর্কে গুপ্তজ্ঞান লাভ করত এবং ঐ জ্ঞানই ছিল একমাত্র সত্য। জরথুস্ত্রবাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম ‘আবেস্তা’। জরথুস্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করত যে ঐ গ্রন্থের সমস্ত বাণী ঈশ্বরের কাছ থেকে জরথুস্ত্রের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।
জরথুস্ত্রবাদ বেশি দিন অবিকৃত থাকতে পারেনি। আদিম কুসংস্কার, যাদুবিদ্যা, পুরোহিততন্ত্র প্রভৃতির সংযোগে এ ধর্মমত অনেকাংশে রূপান্তরিত হয়। তদুপরি ভিন্ন দেশের ধর্মমত, বিশেষত ক্যালডীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবের ফলেও জরথুস্ত্রবাদের অনেক পরিবর্তন ঘটে। জরথুস্ত্রবাদের সাথে এ সকল বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মমতের উদয় ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস হল মিথ্রাসবাদ মিথ্রাইজম্)।

আহুর মাজদার প্রধান সহচর মিথ্রাস্-এর নাম অনুসারে এ মতের নামকরণ হয়েছে। কালক্রমে মিথ্রাস্ ব্যাপকসংখ্যক পারসিকদের প্রধান উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেই মিথ্রাসবাদ একটি প্রধান ধর্মমতে পরিণত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়, সে সময় মিথ্ৰাসবাদ সে সকল অঞ্চলে দ্রুত প্রসার লাভ করে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে রোমেও এর প্রসার ঘটে।
প্রধানত রোমের সাধারণ সৈন্য, দাস ও বিদেশীরাই এ ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। মিথ্রাসবাদ ক্রমশ রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মমত সমূহের একটিতে পরিণত হয় এবং রোমের পৌত্তলিক ধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্ব্বীতে পরিণত হয়। তবে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের শেষদিক থেকে মিথ্রাসবাদের প্রভাব দ্রুত কমতে থাকে। মিথ্রাসবাদের কিছু কিছু বিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্ভবত খৃস্টধর্মের মধ্যে স্থান লাভ করেছিল।
আরেকটি ধর্মমতের মাধ্যমে পারসিক সংস্কৃতির প্রভাব বিদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। এ ধর্মবিশ্বাসের নাম ছিল ‘মানিবাদ’ এর প্রবর্তক ছিলেন মানি নামক একজন অভিজাত পুরোহিত। মানি আনুমানিক ২৫০ খ্রিস্টাব্দে একবাটানায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। জরথুস্ত্রের মতো মানিও ছিলেন একজন ধর্ম সংস্কারক। ২৭৬ খ্রিস্টাব্দে মানি তাঁর পারসিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। মানির মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যগণ পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর ধর্মের প্রচার করে।
৩৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মানিবাদ ইটালিতে প্রবেশ করে। মানিবাদের অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মকে বরণ করেছিল। মিথ্রাসবাদ ও মানিবাদ ছাড়াও পারস্য থেকে উন্নত আরো কয়েকটি ধর্মমত পশ্চিম এশিয়া ও ইটালিতে বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তী সভ্যতার ওপর এ সকল ধর্মমতের মিলিত প্রভাব ছিল অপররিসীম। ৩০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের দিকে আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে প্রাচীন জগতে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।
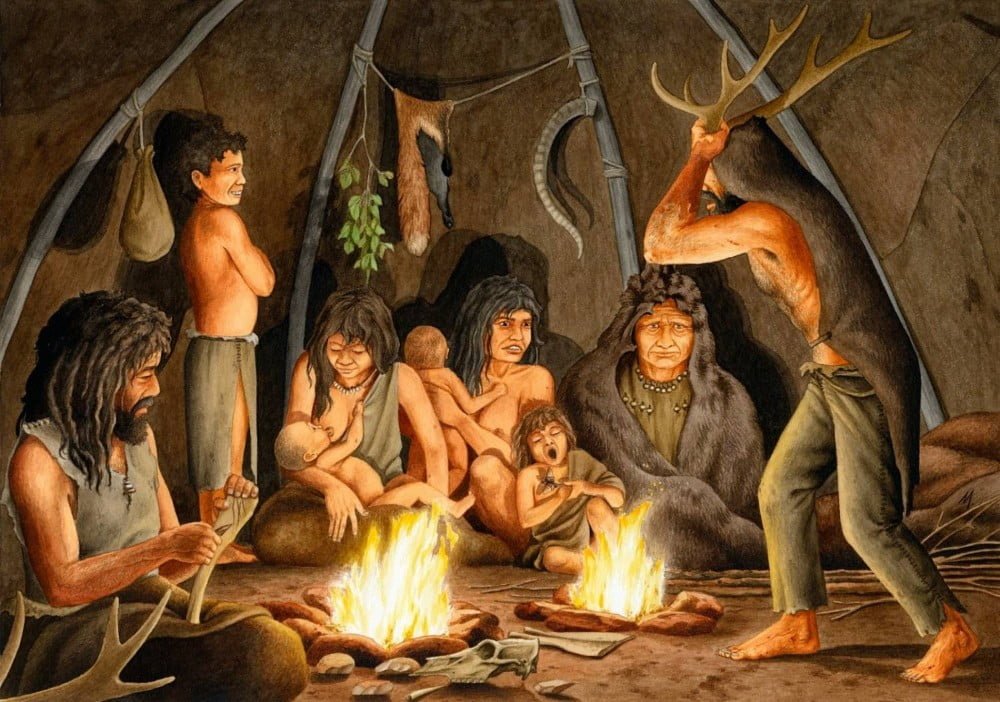
আন্তর্জাতিক সীমান্তসমূহ ভেঙে পড়েছিল, প্রাচীন ব্যবস্থাসমূহ ভেঙে পড়ছিল এবং এক অঞ্চলের মানুষ উৎখাত হয়ে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বাস স্থাপন করছিল। এর ফলে এ সময়ে মানুষের মধ্যে যে অস্থিরতা ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার সুযোগ নিয়েই পারসিক ধর্ম ও সংস্কৃতির পারলৌকিক ও মরমীবাদী প্রভাব মানুষের মনে স্থান করে নিতে পেরেছিল।
হেলেনিস্টিক যুগের অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর ঠিক পরবর্তীকালের গ্রীক দর্শন এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে পারসিক ধর্মের বিভিন্ন দিক মানুষের মনে স্থান লাভ করেছিল।
আরও দেখুন :
