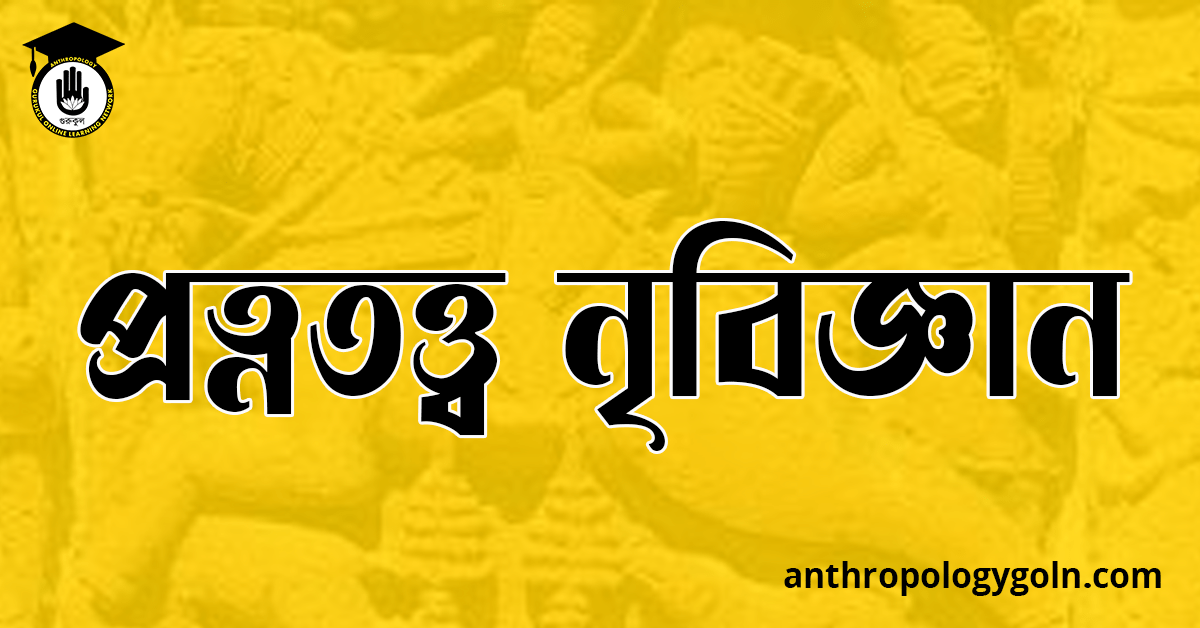প্রত্নতত্ত্ব নৃবিজ্ঞান আজকের আলোচনার বিষয়। নৃবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো অতীত ও বর্তমানের মানব সমাজ ও মানব আচরণকে অধ্যয়ণ করা। অন্যদিকে প্রত্নতত্ত্ব নির্দিষ্ট সময়ের, পরিবেশ এবং ভৌগলিক অঞ্চলগুলি থেকে খনন ও আবিষ্কার করে অতীতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মূলত প্রাচীন সভ্যতাগুলির সমাজ ও জীবন অনুসন্ধান করে।
প্রত্নতত্ত্ব নৃবিজ্ঞান

প্রত্নতত্ত্বঃ
বাংলাদেশের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আপনি হয়ত পাহাড়পুর বা ময়নামতির বৌদ্ধবিহার সম্পর্কে বলবেন। অথবা কখনো যদি ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে থাকেন, সেখানে রক্ষিত কোন নিদর্শন সম্পর্কে বলবেন। অর্থাৎ প্রতিতত্ত (archaeology) কি, এ সম্পর্কে কিছু পূর্বধারণা আপনার অবশ্যই আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে বোঝায় অতীতের মানুষদের ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও ঘরবাড়ির ধুংসাবশেষ যেগুলো কালের প্রবাহে মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে সেই বিজ্ঞান, যা অতীতকালের মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন বস্তু-সামগ্রীরধুংসাবশেষ সুনিপুণ খননকার্ষের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করে সেগুলোর ভিত্তিতে তাদের সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি প্রভৃতির রূপরেখা পুননির্মাণ করে। বিশ্বের অনেক দেশেই প্রত্নতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক জায়গায় আবার নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবেও এর চর্চা রয়েছে, (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে যখন এর চর্চা হয়, তখন তাকে প্রত্রতাত্তিক নৃবিজ্ঞান বা নৃবৈজ্ঞানিক প্রত্রতত্ত বলা হয় (অর্থের বিশেষ কোন তারতম্য ছাড়াই উভয় নামকরণই নৃবিজ্ঞানে প্রচলিত)।

প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে প্রাগৈতিহাসিক প্রততত্ও (prehistoric archaeology) বলা হয়, কারণ এর অধ্যয়নের বিষয় সচরাচর সুদূর অতীতের এমন সব মানব সমাজ যারা নিজেদের সম্পর্কে কোন লিখিত দলিল রেখে যায় নি (মানব ইতিহাসে লিপির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক; সময়ের পথে পেছনে যেতে থাকলে যেখানে ইতিহাসের কোন লিপিবদ্ধ সূত্র আর পাওয়া যায় না, সেখান থেকে শুরু প্রাক-ইতিহাস)।
প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি কথা আপনারা নিশ্চয় অনেক আগে স্কুল পাঠ্য বইয়ে পড়েছেন। এগুলি হল প্রতৃতাত্তিক নৃবিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম। আপনারা নিশ্চয় একথাও আগেই পড়েছেন যে হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর কোথাও মানুষ চাষাবাদ করত না, তারা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে পশু শিকার করত, ধরনের ছিল, কোথায় কবে মানুষ কুকুর-ঘোড়া-গরু ইত্যাদি পালতে বা চাষাবাদ করতে শুরু করে, ইত্যাদি বিষয়ে আমরা যা জানি, সবই প্রততাত্তিক নৃবিজ্ঞানীদের অবদান। এ প্রসঙ্গে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, প্রতৃতাত্তিক নৃবিজ্ঞানীরা কিসের ভিত্তিতে এতসব বিষয় জানেন?
প্রত্নতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য একজন নৃবিজ্ঞানীকে একাধারে ভূতত্ত, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সেটা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না বলে প্রততাত্বিক গবেষণা অনেকক্ষেত্রেই দলীয় গবেষণা হয়ে থাকে, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনানুসারে অংশ নেন। ভূগর্ভের বিশেষ কোন স্তর থেকে খননকার্ধের ফলে আবিষ্কৃত কোন প্রাচীন মানব বসতির ধুংসাবশেষ থেকে সযতে উদ্ধারকৃত বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক খাবার খেত, কি ধরনের হাতিয়ার ও তৈজসপত্র ব্যবহার করত, ইত্যাদি।

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা সেসব সূত্র ধরে বোঝার চেষ্টা করেন অতীতের সেই মানুষগুলো কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থার আওতায় বাস করত, তাদের উৎপাদন পদ্ধতি কেমন ছিল, তাদের মধ্যে ক্ষমতা বা মর্যাদার কোন পার্থক্য ছিল কি না, ইত্যাদি। বিশ্লেষণের এই পর্যায়ে গবেষককে অবশ্যই তার কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা তা করেন বিভিন্ন যুক্তি, প্রমাণ ও সমাজ-সংস্কৃতি সংক্রান্ত তত্তের ভিত্তিতে।
প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা প্রায় সময়ই দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের সাথেও একযোগে কাজ করেন, কারণ খননকার্ষের ফলে অতীতের মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন বস্তুসামগ্রীর ধুংসাবশেষের পাশাপাশি অনেক সময় তাদের দেহাবশেষও পাওয়া যায়, যেগুলোর সূত্র ধরে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীরা অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধার করতে পারেন।
প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আমরা একদিকে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা লাভ করি, তেমনি নির্দিষ্ট কোন দেশ বা অঞ্চলের প্রাক- ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কেও জানার সুযোগ পাই। ধরা যাক আমরা জানতে চাই আজ থেকে পাচ দশ হাজার বছর আগে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে মানব বসতি ছিল, এদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা কোথায় কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করত, তাদের প্রযুক্তি কেমন ছিল, ইত্যাদি।

এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে অবশ্যই প্রক্রতান্তিক গবেষণা চালাতে হবে। বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণা এখনো খুব একটা হয় নি। অবশ্য সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রত্তিতত্ব বিভাগ খোলা হয়েছে, তবে সেটা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এদেশের প্রথম নৃবিজ্ঞান বিভাগ হতে আলাদা।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবত যতগুলো নৃবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে, সবগুলোতেই মূলতঃ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সে হিসাবে বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের কোন স্বতন্ত্র এতিহ্য তৈরী হয় নি। তবে প্রত্রতত্ত, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষকরা একযোগে কাজ করলে বাংলাদেশের প্রাক- ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে নিশ্চয় আমরা অনেক কিছু জানতে পারব যা নিজেদের সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে।