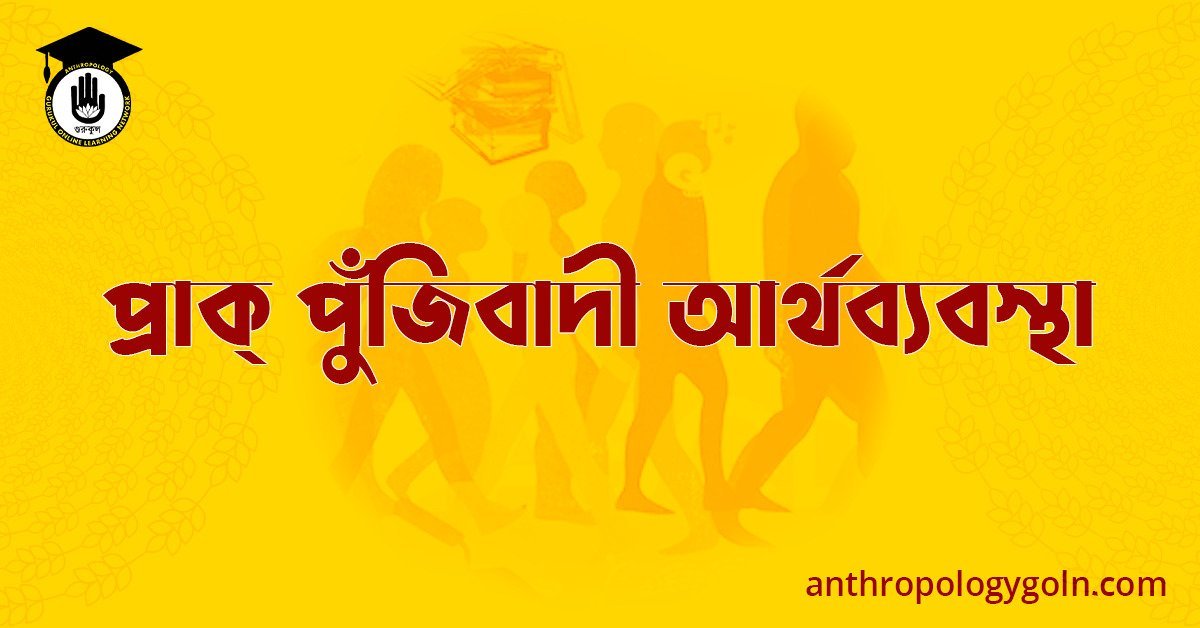আজকে আম্রাক আলোচনা করবো প্রাক্ পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা নিয়ে। আগের পাঠ থেকে আপনারা জানেন নৃবিজ্ঞানে আর্থব্যবস্থা বলতে কি বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে মুখ্য বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন সমাজের উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগের আলোচনা করা। এগুলোর ভিত্তিতে নানান সমাজের আর্থব্যবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ, নানান সমাজে উৎপাদন করবার উপায়, বণ্টনের নিয়ম এবং ভোগের ধরন এক ও অভিন্ন নয় – এই চিন্তাই নৃবিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করেছে আর্থব্যবস্থা অধ্যয়ন করতে। কিন্তু এখানে আবারও খেয়াল রাখা দরকার যে, প্রাথমিকভাবে ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীরাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা করতে গেছেন। আর তাঁদের চিন্তায় ইউরোপের ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ছিল।
যে সময়কালে এই সকল নৃবিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গেছেন সেই সময়কালে ইউরোপের আর্থব্যবস্থা গভীরভাবে পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যের ছিল। এবং নৃবিজ্ঞানীরা সেটাকেই সকল সমাজের জন্য স্বাভাবিক মনে করেছেন। ফলে অপরাপর যে সকল আর্থব্যবস্থা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল সেগুলোকে কিভাবে আলোচনা করা যাবে সেটা একটা গভীর মনোযোগের বিষয় হিসেবে দেখা দেয়।
প্রাক্ পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা
এর ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নানান আর্থব্যবস্থা নিয়ে তুলনামূলক আলাপ- আলোচনা গড়ে উঠতে। এ সকল ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীদের ভাবনা-চিন্তা নিছক একই রকম ছিল না। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে স্বাভাবিক ও ‘এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট’ ধরে নেয়া হয়েছে। এটা আমরা নামকরণ থেকেই বুঝতে পারি। লক্ষ্য করে দেখুন, প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কাম্য ও স্বাভাবিক হিসেবে দেখা হয়েছে।
নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা পাঠ করবার ক্ষেত্রে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই দুই ধারার মধ্যে অমিলের মতো মিলও প্রচুর – সে কথা আগের আলোচনাতেই পরিষ্কার। একটি ধারা অনুযায়ী প্রকৃতি, পরিবেশ এবং সেই অনুযায়ী প্রযুক্তির ভেদে আর্থব্যবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এখানে আর্থব্যবস্থার ভিন্নতার জন্য মূলত পরিবেশকে দায়ী করা হয়। কোন একটি অঞ্চলের পরিবেশের ভিন্নতায় সেখানকার মানুষজন ভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অবলম্বন করে থাকেন, ফলে সেখানে আর্থব্যবস্থা অন্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে এই হচ্ছে মূল যুক্তি।

এই ধারাকে মোটামুটি – পরিবেশকেন্দ্রিক ক্রিয়াবাদী ধারা বলা যেতে পারে। অন্য ধারাতে মূল যুক্তি হচ্ছে: মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আর্থব্যবস্থা চালু থাকলেও সেগুলো কালক্রমে বদলাতে থাকে। একটি ব্যবস্থা থেকে আর একটি ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট এবং সেই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার দিকে আর্থব্যবস্থা যেতে থাকে। এই ধারাকে বিবর্তনবাদী ধারা বলা যেতে পারে। নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই অনুসারী প্রথম ধারার। কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে, এই দুই ধারার একটা প্রধান মিল হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই আর্থব্যবস্থা বিবেচনা করার সময় সমাজে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
পরিবেশ ও প্রযুক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কয়েকটি ভাগে আর্থব্যবস্থাকে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলি বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে থাকে। অর্থাৎ, ধরে নেয়া হয় কোন একটি আর্থব্যবস্থা কালক্রমে অন্য আর্থব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। নিচে সেগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো ।
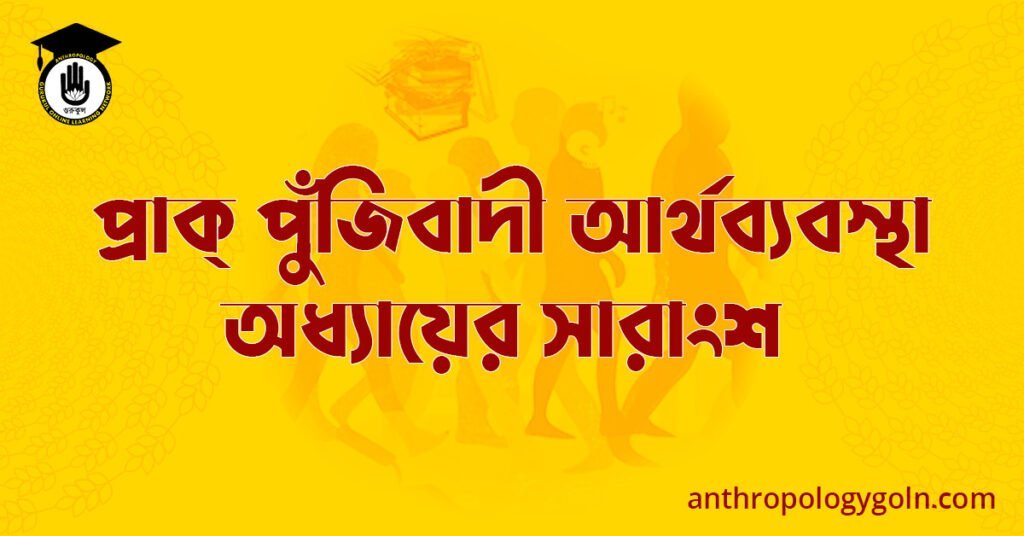
প্রাক্ পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা অধ্যায়ের সারাংশ :
আজকের আলোচনার বিষয় প্রাক্ পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা অধ্যায়ের সারাংশ – যা প্রাক্ পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা এর অর্ন্তভুক্ত, বিভিন্ন সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে গবেষণা করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। উৎপাদনের ধরন দেখতে গিয়ে সাধারণভাবে খাদ্য সংগ্রহের উপায়ের উপর জোর দিয়েছেন তাঁরা।
কিন্তু তাঁদের অনেকের চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে: পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য। এভাবেই পৃথিবীর সকল উৎপাদন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন তাঁরা: প্রাক্-পুঁজিবাদী এবং পুঁজিবাদী। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া, পরিবেশ এবং প্রযুক্তির কলা কৌশল ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনের ধরন সৃষ্টি করেছে বলে কিছু নৃবিজ্ঞানী মনে করেছেন।

সেই ভিত্তিতে ৪ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে: শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ, পশুপালক সমাজ, উদ্যান-কৃষি সমাজ এবং নিবিড় কৃষি সমাজ। তবে সেক্ষেত্রেও ‘প্রাক্-পুঁজিবাদী লেবেল দেয়া হয়েছে সেই সমাজগুলোকে। তবে অনেক নৃবিজ্ঞানীরই অভিমত হচ্ছে, বর্তমান দুনিয়ার কৃষি ব্যবস্থা পুঁজিবাদ এবং শিল্পভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ।