আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় প্রাচীন যুগের ইতিহাস
প্রাচীন যুগের ইতিহাস

প্রাচীন যুগের ইতিহাস
৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে প্রাচীন গ্রীসে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ঘটতে থাকে। ব্রোঞ্জ যুগের এবং লৌহ যুগের কারিগরি ও অন্যান্য অবদানের ভিত্তিতে গ্রীকসমাজের নতুন বিকাশ ঘটে। গ্রীসের বিভিন্ন দ্বীপ ও নগরে লোহার হাতিয়ার ঢালাই ও ঝালাই করার প্রক্রিয়ার প্রচলন হয়েছিল। মাটির পাত্র, তাঁতের কাপড়, পাথরের অট্টালিকা নির্মাণ প্রভৃতিরও প্রচলন হয়েছিল।
এ ভাবে নতুন নতুন পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদয় ঘটে। ফিনিশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক যোগযোগ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসার প্রসারের সাথে সাথে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। মুদ্রা অবশ্য প্রথম পশ্চিম এশিয়ার লিডিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল ইলেকট্রামের (অর্থাৎ সোনা ও রূপার মিশ্র ধাতুর) তৈরি উচ্চমানের মুদ্রা। লিডিয়ার অনুকরণে পারস্যে সোনার এবং গ্রীসে রূপার যে মুদ্রার প্রচলন হয় সেগুলোও ছিল উচ্চমানের মুদ্রা।
উচ্চমানের মুদ্রার সাহায্যে ধনী কৃষক মহাজনরা বড় বড় লেনদেনের কাজ চালাতে পারলেও ছোট ছোট কৃষক কারিগররা এর ফলে বিন্দুমাত্রও উপকৃত হয়নি। কিন্তু ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অল্পকাল পরে এথেন্স, করিথ্ প্রভৃতি গ্রীক নগররাষ্ট্রে তামা বা রূপার তৈরি কম মানের ছোট মুদ্রার প্রচলন হওয়ার ফলে গ্রীসের ব্যাপকসংখ্যক দরিদ্র কৃষক-কারিগরও মুদ্রা অর্থনীতির আওতায় চলে আসতে পারল।
যেমন, যে কৃষকের সামান্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত জলপাই বা আঙুর ছিল, তার পক্ষেও তা’ বিক্রি করে টাকা জমানো সম্ভব হয়েছিল অল্প মানের মুদ্রার আবিষ্কারের ফলে। এ জমানো টাকা দিয়ে পরে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা তার পক্ষে সম্ভব হত। এর ফলে একদিকে গ্রীসে জাতীয় সঞ্চয় এবং জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শিল্প ও কারিগরি উৎপাদন উৎসাহিত হয়েছিল।
অল্প মানের মুদ্রা এভাবে গ্রীসের অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে যে, গ্রীস কেবল প্রাচীন কালের আবিষ্কারসমূহকে সফলভাবে প্রয়োগই করেনি-অনেক ক্ষেত্রে তার উন্নতি এবং বিকাশসাধনও করেছিল। কারিগরি শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলেই ক্রমশ গ্রীসে হোমারীয় যুগের গ্রামসমাজ ভেঙে পড়ল। তার জায়গায় উদিত হল বড় আকারের অর্থনৈতিক কেন্দ্র অর্থাৎ নগর।
গ্রীসের এ সকল নগরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র নয়, উপরন্তু রাজনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্রেও পরিণত হয়। এ সকল নগর তার চারপাশের এক বড় অঞ্চলের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বস্তুত এ সকল গ্রীক নগর ছিল এক-একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র। তাই এদের বলা হয় নগররাষ্ট্র।
এসকল নগরে বড় বড় অট্টালিকা থাকত অভিজাত নাগরিকদের জন্যে, সার্বজনীন চত্বর (এ্যাগোরা) থাকত ব্যবসা-বাণিজ্য, সভা-সমিতি প্রভৃতির জন্যে; মন্দির ইত্যাদিও থাকত; এছাড়া থাকত প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রতি নগরে একটি করে সুরক্ষিত স্থান বা এ্যাক্রোপোলিস। বস্তুত এ্যাক্রোপোলিসকে কেন্দ্র করেই নগর রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠত। গ্রীক, জগতের সর্বত্রই এ রকম নগররাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।
যেমন, মধ্যগ্রীসের এ্যাটিকা নামক স্থানে ছিল এথেন্স নগররাষ্ট্র; দক্ষিণ পেলোপনেসাস্-এর ল্যাকোনিয়া নামক স্থানে ছিল স্পার্টা নগররাষ্ট্র; পেলোপনেসাস্-এর সাথে মধ্য গ্রীসের সংযোগকারী যোজকের ওপর অবস্থিত ছিল নগররাষ্ট্র করিন্থ; এশিয়া মাইনরের উপকূলে ছিল মাইলেটাস ইত্যাদি। এগুলো অবশ্য সুবিখ্যাত নগররাষ্ট্র। এ রকম শত শত নগররাষ্ট্র গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও উপকূলের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল।

অধিকাংশ নগররাষ্ট্রের আয়তন ছিল একশো বর্গমাইলের মধ্যে আর লোকসংখ্যা হত দশ-পনের হাজার থেকে ষাট-সত্তর হাজার। তবে বড় আকারের নগররাষ্ট্রও ছিল। যেমন, এথেন্সের আয়তন ছিল এক হাজার বর্গমাইল, স্পার্টার চার হাজার বর্গমাইল, আর এ দুই নগররাষ্ট্রেরই লোকসংখ্যা ছিল প্রায় চার লক্ষ করে। গ্রীসে নগররাষ্ট্রের উদ্ভবের কালে অর্থাৎ ৮০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীকরা ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে অজস্র উপনিবেশ স্থাপনেও উদ্যোগী হয়েছিল।
এজন্য গ্রীক ইতিহাসে এ যুগ উপনিবেশ বিস্তারের যুগ নামেও পরিচিত। উপনিবেশ বা কলোনি বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, গ্রীকরা কিন্তু সে রকম বুঝত না। আধুনিক কালে, কোনো উন্নত দেশ অপর কোনো অনুন্নত দেশকে নিজ পদানত করে রাখলে সেই পরাধীন দেশকে বলা হয় ‘উপনিবেশ’। আর প্রাচীনকালে গ্রীকরা বিদেশে গিয়ে নতুন নগর নির্মাণ করে সেখানে বাস স্থাপন করলে তাকেই বলা হত ‘উপনিবেশ’।
কোনো একটি নগররাষ্ট্র থেকে উদ্যোগ নিয়েই অবশ্য নতুন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করা হত। কিন্তু এ উপনিবেশ কোনোক্রমেই তার প্রতিষ্ঠাতা নগররাষ্ট্রের অধীন হত না। প্রত্যেকটি উপনিবেশের নিজস্ব সংবিধান, নাগরিকত্ব আইন, আদালত ও মুদ্রা ছিল। বস্তুত প্রতিটি নব-প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশই ছিল এক একটি স্বতন্ত্র নগররাষ্ট্র।
গ্রীসে এক একটি নগররাষ্ট্রের উদ্যোগেই নতুন উপনিবেশ স্থাপিত হত; এ প্রক্রিয়ায় তাই বিশিষ্ট গ্রীক সংস্কৃতি অর্থাৎ তার বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, ভাব-ভাষা ইত্যাদি সমস্ত গ্রীক নগররাষ্ট্রে বিস্তার লাভ করেছিল। গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির অভাব দেখা দেবার দরুনই প্রধানত গ্রীকরা দলে দলে নতুন জায়গায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। এ হয়েছিল।
এভাবে ঈজিয়ান সাগরের সমগ্র উপকূলে, কৃষ্ণসাগরের সমগ্র উপকূলে, ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের প্রয়োজনেও নতুন নতুন স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত আফ্রিকার উত্তর উপকূলে, ইটালিতে, সিসিলিতে, স্পেনে এবং ঈজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে অজস্র গ্রীক নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
নতুন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনের সময় গ্রীকরা দল বেঁধে নৌকায় করে কৃষক, কারিগর, বণিক, পূজারী প্রভৃতি নিয়ে যেত এবং উন্নত ধরনের লোহার অস্ত্রাদির সাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীদের পরাস্ত করে প্রয়োজনীয় ভূমি দখল করত। স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করে দাসে পরিণত করা হত।
এযুগের গ্রীকসভ্যতা তাই ক্রমশ দাসশ্রমভিত্তিক হয়ে পড়ে। এর আগের, অর্থাৎ হোমারীয় যুগেও গ্রীকসমাজে দাসের প্রচলন ছিল, কিন্তু সেসব দাস সংখ্যায়ও কম ছিল এবং তারা সাধারণত বাড়িঘরের কাজেই নিয়োজিত হত। কিন্তু নতুন যুগে দাসের সংখ্যাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের উৎপাদনের কাজেও নিয়োগ করা শুরু হয়। গ্রীসের নগররাষ্ট্রসমূহে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে কারখানায়, খামারে এবং খনিতে ব্যাপক হারে দাসনিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয়।
গ্রীকদের উপনিবেশ বিস্তারের ফলে গ্রীক ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনীতি ও সমাজ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। উপনিবেশসমূহের সাথে বাণিজ্যের ফলে গ্রীসের পণ্যের চাহিদা বাড়ে। তার ফলে গ্রীসের শিল্প উৎপাদন বিকাশ লাভ করে। ফলে গ্রীসের অর্থনীতিতে শিল্পোৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধান স্থান অধিকার করে। অনেক উপনিবেশ মাতৃভূমি থেকে পণ্য আমদানি করত এবং বিনিময়ে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কাঁচামাল রপ্তানি করত।
এর ফলে অনেক মূল গ্রীক নগররাষ্ট্র বিশেষ ধরনের শিল্পপণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পেরেছিল। এর দরুন গ্রীসের নগরের অধিবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, গ্রীসের সভ্যতা সংস্কৃতি ক্রমশ নগরকেন্দ্রিক হতে শুরু করে। উপনিবেশসমূহের মাধ্যমে দাস সংগৃহীত হওয়ার দরুন গ্রীসীয় নগরসমূহে দাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যে সকল অঞ্চলে গ্রীক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠত হয় সেখানেও ক্রমশ গ্রীসীয় শিল্প বিকাশ লাভ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।
গ্রীক সংস্পর্শের দরুন স্থানীয় পশ্চাৎপদ জনগণও দ্রুত সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়। এ যুগে গ্রীক-জগতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দু’ একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সমস্ত গ্রীক নগররাষ্ট্রে একই ধরনের রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল। গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহে প্রথমদিকে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে তার স্থলে অভিজাত পরিষদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
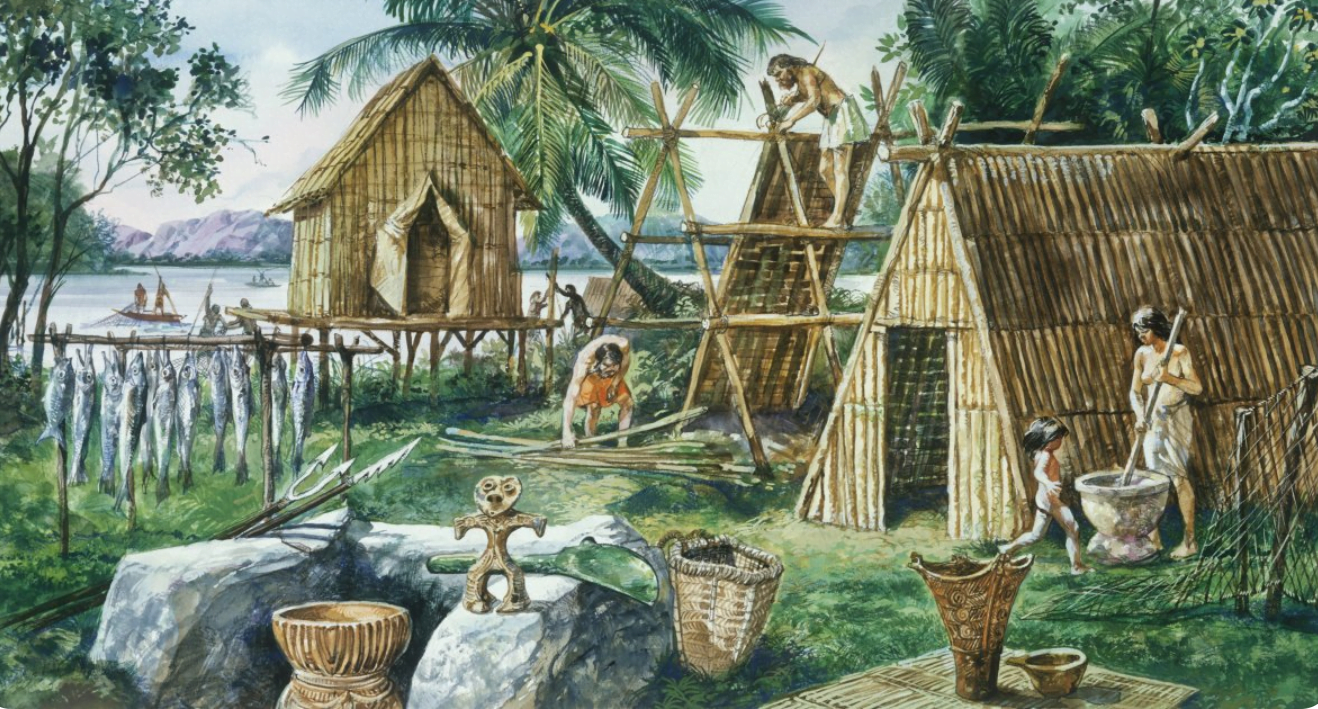
এর প্রায় একশো বছর পরে বিভিন্ন স্থানে অভিজাত পরিষদের স্থান অধিকার করে স্বৈরাচারী শাসক বা ‘টায়রান্ট।’ যে ব্যক্তি বে-আইনীভাবে ক্ষমতা অধিকার করত, গ্রীকরা তাদের নাম দিযেছিল টায়রান্ট। এ স্বৈরাচারীরা সবাই যে অত্যাচারী প্রজাপীড়ক হতেন এমন নয়, এঁদের অনেকেই ছিলেন বিবেচক ও প্রজাপালক। সবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীসের প্রায় সব নগররাষ্ট্রেই জনসাধারণের শাসন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
আরও দেখুন :
