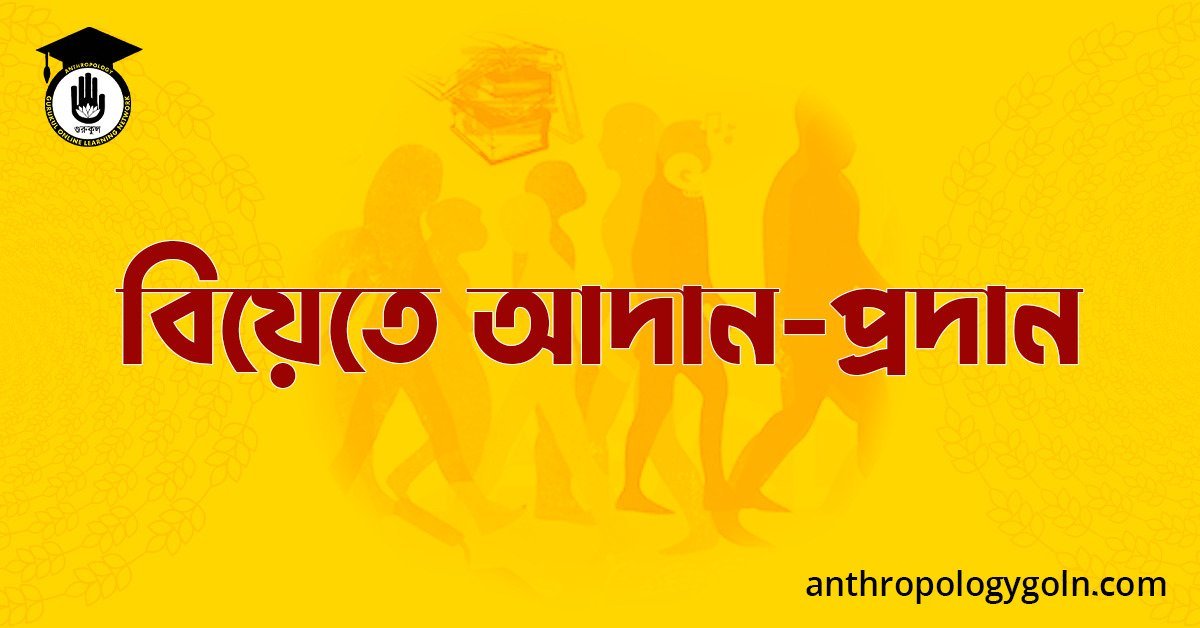আজকের আলোচনার বিষয় বিয়েতে আদান-প্রদান – যা বিয়ের ধরন এর অর্ন্তভুক্ত, বিয়ে উপলক্ষ্যে বর পক্ষ যদি কনে পক্ষকে মূল্যবান সামগ্রী দেয় সেটিকে বলা হয় কনে পণ (bridewealth, bride price)। সামগ্রীর আদান-প্রদান যদি হয় উল্টোভাবে, অর্থাৎ, বিয়ে উপলক্ষ্যে কনে পক্ষ যদি বর পক্ষ, অথবা বরকে, মূল্যবান সামগ্রী প্রদান করে, সেটিকে বলা হয় যৌতুক (dowry)। যে সমাজগুলোতে প্রথা অনুসারে কনে পণ দেয়া হয়, সেখানে দেখা গেছে যে, প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী বরের পক্ষে একা, এমনকি শুধুমাত্র তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে, যোগাড় করা সম্ভব নয়।
বিয়েতে আদান-প্রদান

গোষ্ঠীর কোন পুরুষ সদস্যের জন্য বউ আনতে বিন্ধপ্পত জ্ঞাতিকুলের কসরত করতে হয়। ঠিক একইভাবে, প্রাপ্ত সামগ্রী বউ পক্ষের বিন্ধপ্পত জ্ঞাতিকুলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যাতে যাঁরা পূর্বে সেই গোষ্ঠীতে বউ আনতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাও এই সামগ্রীর ভাগীদার হন। প্রতিটি বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনে জটিল ধরনের ঋণগ্রস্ততা ও পারস্পরিক লেনদেনের সূত্রপাত ঘটে, যা বংশ পরম্পরায় চলমান। কনে পণ সংগ্রহ এবং তার পুনর্বণ্টনে বহু মানুষজন জড়িত। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে, কিছু কিছু সমাজে দেখা যায় যে, কনে পণ ফেরৎ দেয়ার ক্ষেত্রে কার কি দায়বদ্ধতা এবং তার হিসেবনিকেশ, দুই প্রজন্মের মানুষজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।
নৃবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ বলে, কনেপণ-প্রদত্ত বিয়েতে প্রচুর পরিমানে ব্যয় করা হয়। আচার-প্রথা পালন বিয়ের অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলে। ধরে নেয়া যেতে পারে যে, লোকসম্মুখে আয়োজিত, ধূমধামের বিয়ের লক্ষ্য হচ্ছে, এই নতুন সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদটি সবার কাছে পৌঁছে দেয়া, সেটার সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন, এবং হবু সন্তানদের বৈধতা ঘোষণা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, কনে পণ প্রদান নারীর সেবার অধিকার হস্তান্তরের ইঙ্গিত করে।
অর্থাৎ, এর পর থেকে, তার শ্বশুরকুল তার গৃহীসেবা, যৌনক্ষমতা, এবং বাচ্চা জন্মদানের ক্ষমতার অধিকারী; তার পিতৃকুল নয়। নৃবিজ্ঞানী লিয়েনহার্ট-এর অভিমত হচ্ছে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, কনে পণকে দেখা হয় কন্যা সন্তানকে বড় করে তোলার কষ্ট, খাটা-খাটনির ক্ষতিপূরণ, এবং তার শ্রমশক্তি হারানোর ক্ষতিপূরণ, হিসেবে।

কিছু সমাজে প্রচলন আছে কনে সেবার (bride service)। এসকল সমাজে, স্ত্রীতে অধিকার প্রাপ্তির বিনিময়ে বর তার শ্বশুরবাড়িতে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য শ্রম ও সেবা দেন। এ ব্যবস্থার প্রচলন সে ধরনের সমাজে দেখা যায় যেখানে মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করা কঠিন। আফ্রিকার কুং!দের মাঝে, জামাই তার শ্বশুরকুলকে শ্রম ও সেবা দিতে পারেন পনের বছর পর্যন্ত, কিংবা তৃতীয় সন্তান জন্মানো পর্যন্ত।
পূর্বে, যৌতুক বিবাহ ইউরোপে প্রচলিত ছিল। ভারতের যৌতুক প্রথার ব্যাখ্যা নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মত লক্ষণীয়। এক দল মনে করেন যে, যৌতুক দেয়া হয় কন্যাকে। কন্যা যেহেতু বিয়ে সূত্রে ঘর ছেড়ে চলে যান এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নন, সেকারণে পিতা-মাতা কন্যার বিয়ে উপলক্ষ্যে তাকে মূল্যবান সামগ্রী উপহার দেয়। অন্য দল মনে করেন, যৌতুক কন্যাকে নয়, বরং বর এবং তার পরিবারকে দেয়া হয়। তাঁদের ব্যাখ্যা হল : সামাজিকভাবে নারীদের দেখা হয় অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে। বোঝা হিসেবে বিবেচিত হবার কারণ হ’ল, উঁচু জাতের নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন না।
নিচু জাতের নারীরা যদিও তা করে থাকেন, উঁচু জাতের প্রথা, রীতি-নীতি অনুসরণের প্রবনতার কারণে এ জাতেও যৌতুকের প্রচলন দেখা দেয়। বর পক্ষের জন্য বিয়ের অর্থ হচ্ছে একজন “বোঝা”-কে খাওয়া-পরার দায়ভার গ্রহণ করা। বোঝা গ্রহণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে যৌতুক প্রদান করা হয়।
চিত্র ১: যৌতুক
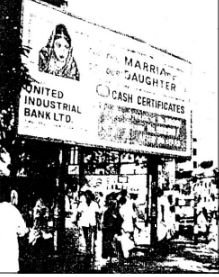
বিবাহ উপলক্ষে কেবলমাত্র সামগ্রী বা মূল্যবান জিনিসপত্রের আদান-প্রদান নয়, দুই কুলের মধ্যে নারীরও আদান-প্রদান হতে পারে। নাইজেরিয়ার টিভ সমাজে এভাবে ঘরে বউ আনার প্রচলন আছে। দুই গোষ্ঠী কন্যার বিনিময়ে কন্যা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নতুন বউ নিজ নিজ শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে, চলে যাওয়া কন্যার নাম গ্রহণ করেন।
পাশ্চাত্য সমাজসমূহে বিয়ে হচ্ছে দাম্পত্য-ভিত্তিক। এসকল সমাজে বিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং প্রেম- ভালবাসা-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিয়ের অন্য কোন ভিত্তি (“বাবা-মায়ের পছন্দ”, “দুই বংশকে আরো কাছে করতে চাই”) অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হয়। বিয়ের অর্থ হচ্ছে স্বতন্ত্র গৃহস্থালী স্থাপন এবং দাম্পত্যকেন্দ্রিক জীবন যেখানে স্বামী ও স্ত্রী, একে অপরের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ও সাথী।
বিয়েতে একান্তভাবে দম্পতিকে উপহার দেয়া হয়। বর ও কনের নিজ-নিজ পরিবার, তাঁদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা এই উপহার সামগ্রী দেন। এ হচ্ছে সাধারণ চিত্র। অতি ধনী শ্রেণীতে, এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মে সম্পত্তির হস্তান্তর বিয়েকে কেন্দ্র করে হয় না। বরং, দাদা-দাদী, নানা-নানী তাঁদের নাতি-নাতনীদের বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যেমন গ্রাজুয়েশন-এ, মূল্যবান উপহার (ডায়মন্ড, গাড়ী বা কটেজ) দেন।