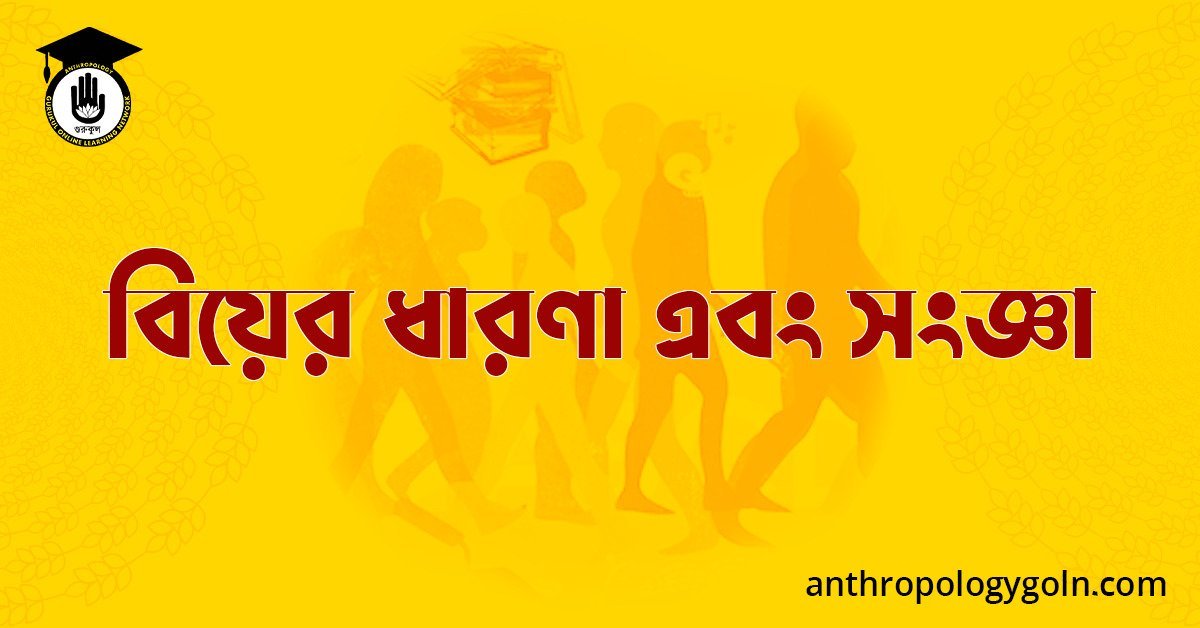আজকে আমরা আলোচনা করবো বিয়ের ধারণা এবং সংজ্ঞা নিয়ে । বিয়ের এমন কোন সংজ্ঞা দাঁড় করানো সম্ভব নয় যা কিনা সকল স্থান এবং সকল সময়কালের জন্য প্রযোজ্য। বিগত প্রায় একশ’ বছর ধরে সমাজ বিজ্ঞানীরা বিয়ের একটি সর্বকালব্যাপী, এবং সর্বস্থানের জন্য প্রযোজ্য – এক কথায় বললে, “বিশ্বজনীন” (universal ) – সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের এই | প্রচেষ্টার অগ্রভাগে ছিলেন নৃবিজ্ঞানীরা। কিন্তু হাল আমলের ভাবনা হচ্ছে, এ ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ ধরনের প্রচেষ্টায় প্রাধান্য পায়, হয় “নিজ” সমাজের অথবা নৃবিজ্ঞানীর কাছে বহুল পরিচিত কিছু সমাজের, বিয়ে ব্যবস্থা।
এসব সমাজ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিয়ে সংক্রান্ত তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়। এতে সমস্যা তৈরী হয়। এভাবে ভাবনা চিন্তা করলে কোনমতেই এ বিষয়ে বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা (cultural differences) বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অন্য কথায়, বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা । ক্ষেত্র বিশেষে পৃথিবীর মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এ ধরনের প্রচেষ্টায় ধরে নেয়া হয় যে, বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই আমরা যা কিছু জানি, তা পর্যাপ্ত।
বিয়ের ধারণা এবং সংজ্ঞা
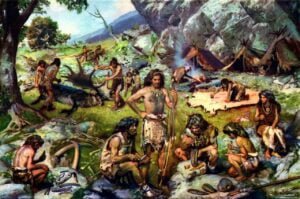
অন্য কোন কিংবা ভিন্ন কোন সমাজ সম্বন্ধে পাওয়া তথ্য “সংযোজন” মাত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কোন কোন সমাজের বিয়ের প্রথাকে দেখা হয় “ব্যতিক্রম” অর্থে, এবং মূলধারার আলোচনায় এই ভিন্নতাগুলোকে সমান গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করা হয় না। কিন্তু, নৃবিজ্ঞানের ঘোষিত লক্ষ্য যেহেতু মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে জানা, সেকারনে জরুরী হয়ে পড়ে সমাজে সমাজে ভিন্নতা, এক কাল হতে আরেক কালের পার্থক্য এই – বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রে রাখা।
এই লক্ষ্য সামনে রেখেই সাম্প্রতিককালের নৃবিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী সংজ্ঞা দাঁড় করানোর উপর আর জোর দিচ্ছেন না। বরং গুরুত্ব দিচ্ছেন নির্দিষ্টতার (specificity) উপর: তারা জানতে চাচ্ছেন, বুঝতে চাচ্ছেন নির্দিষ্ট কোন সমাজে, নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর মাঝে, নির্দিষ্ট সময়কালে কি ধরনের বিয়ে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বা আছে।
বিগতকালে, কিছু নৃবিজ্ঞানী বিয়ের একটি বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, সকল সমাজে বিয়ে, আকর (core) কিছু কার্য (function) সম্পাদন করে। তাদের মতে (ক) যৌনতা নিয়ন্ত্রণ এবং (খ) সন্তানের বৈধতা প্রদান – এদুটো কাৰ্য সম্পাদন বিয়েকে দান করে এক বিশ্বজনীন রূপ। উইলিয়াম গুডএনাফ-এর মতে (১৯৭০), বিয়ে হচ্ছে একটি চুক্তি যার মাধ্যমে একজন নারীর যৌনতার উপর অধিকার সৃষ্টি করা হয়। নৃবিজ্ঞানী ক্যাথলিন গফ-এর মতে (১৯৫৯), সন্তানের বৈধতা নির্ধারণ বিয়ে নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সর্বজনীনতা প্রদান করে থাকে।
তার মানে, গফ বলতে চাচ্ছেন, বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী এবং একজন পুরুষের যৌন মিলন সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই যৌন মিলনের ফলে ভূমিষ্ট সন্তান বৈধ সন্তান হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু, গফ বিয়ের অর্থ যেভাবে দাঁড় করাচ্ছেন – বৈধ সন্তান নিশ্চিত করা হচ্ছে বিয়ে নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্য, এবং এ কার্য সম্পাদন বিয়েকে করে তোলে বিশ্বজনীন – সেটা সকল সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। –
সুদানের নুয়ের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে ‘ভূত বিবাহ’ (ghost-marriage) এবং নারী-নারী (woman-woman marriage) বিবাহ প্রচলিত। ভূত বিবাহ বলা হচ্ছে সে ধরনের বিয়েকে যেখানে একজন বিধবা হয় পুনরায় বিয়ের মাধ্যমে, অথবা প্রেমিক গ্রহণের সাহায্যে, মা হন।
নবজাতক সন্তানটি স্বীকৃতি পায় মৃত স্বামীর বৈধ সন্তান হিসেবে – তার নতুন স্বামী অথবা প্রেমিকের বংশধর হিসেবে না। নুয়েরদের মাঝে আরেক ধরনের বিয়ের প্রচলন আছে, যা কিনা ‘নারী-নারী বিবাহ’ হিসেবে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত: এ বিয়ের মাধ্যমে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। বয়োকনিষ্ঠ নারী বিয়ের পর স্বাধীনভাবে প্রেমিক গ্রহণ করতে পারেন। প্রেমিকের সাথে শারীরিক মিলন সূত্রে যে সন্তানেরা জন্মায় তাদের ধরা হয় “স্বামী”র (বয়োজ্যেষ্ঠ নারী) পিতৃকূলের সদস্য হিসেবে।

খুব স্পষ্টতই, নুয়ের সমাজের বিয়ের এ দুই ধরন, বিয়ের সর্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর বহু প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তোলে। আবার বাঙ্গালী হিসেবে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণাকেও ধাক্কা দেয়। একমাত্র বিয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেবে সমাজের চোখে সন্তান বৈধ হিসেবে স্বীকৃত হবে কিনা – এই ধারণা নুয়ের সমাজের ভূত বিবাহের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই খাটে না।
বিয়ের মানে বৈধ সন্তান – বিষয়টাকে নুয়ের জনগোষ্ঠী এভাবে দেখেন – না। কারণ, সে সমাজে, একজন বিধবা নারীর পুনরায় বিয়ে করার পরও তার পরবর্তী স্বামীর ঔরসজাত সন্তান তার পূর্বতন/মৃত স্বামীর বংশধর। আরও উল্লেখ্যযোগ্য, মৃত স্বামীর বৈধ বংশধর হিসেবে স্বীকৃতি পাবার জন্য সন্তানের মার বিয়ে করা বাঞ্ছনীয় নয়। বিয়ে না করে তিনি যদি প্রেমিকের সাহায্যে সন্তান লাভ করেন, সেই সন্তানও মৃত স্বামীর বৈধ সন্তান হিসেবে স্বীকৃত।
নুয়ের সমাজের নারী-নারী বিবাহের যে প্রচলন রয়েছে সেখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: প্রথমত, একজন – নারী এবং একজন পুরুষ নয়, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন দুইজন নারী। এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, বর্তমানে পত্র-পত্রিকায় “সমকামী” সম্পর্ক বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে, এটা কিন্তু তা নয়। একই লিঙ্গের মাঝে কামনার সম্পর্ককে সমকামিতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। সমকামিতার দরুন কিন্তু দুই নুয়ের নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিতে ধরে নেয়া হয় পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় শুধুমাত্র পুরুষের মাধ্যমেই বংশ বৃদ্ধি হয়। নারীর ভূমিকা এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় কিংবা গৌণ।
কিন্তু নুয়েরদের বিয়ের এই প্রথা এ ধরনের পুরুষালী ধারণাকে ধাক্কা দেয়। নুয়েরদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, নারী-নারী বিবাহ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে পিতৃকূলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয়ত, নুয়েরদের বিবাহ প্রথার সাথে গুডএনাফের সংজ্ঞা খাপ খায় না। ভূত বিবাহ প্রথা অথবা নারী-নারী বিবাহ প্রথা, কোনটার ক্ষেত্রেই বলা সম্ভব নয় যে বিয়ের অর্থ হচ্ছে নারীর যৌন ক্ষমতার উপর কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা। একজন বিধবা নুয়ের নারী বিয়ে না করেও প্রেমিক গ্রহণ করতে পারেন।
সেটা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। নুয়েরদের নারী-নারী বিবাহের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, নারীর যৌনতায় অধিকার প্রতিষ্ঠা এ ধরনের বিবাহ প্রথার প্রধান কার্য বা function না ঠিক একইভাবে, ভারতের মাতৃতান্ত্রিক নায়ার সমাজের বিবাহ প্রথা বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাকে সংকটাপন্ন করে তোলে । একজন নায়ার মেয়েকে একজন পুরুষের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে দেয়া হয় কিন্তু বিয়ের পর মেয়েটি তার স্বামীর সাথে বসবাস করে না, সে তার মাতৃকূলেই থেকে যায়। মেয়েটি চাইলে প্রেমিক গ্রহণ করতে পারেন। সন্তান জন্মালে, সেই সন্তান মায়ের আনুষ্ঠানিক স্বামীর বংশের নয়, অথবা মায়ের প্রেমিকের বংশেরও নয় কিংবা নিজের প্রেমিকের বংশেরও নয়।
সন্তানটি হয় নিজ মায়ের বংশের সদস্য। এ সকল কারণে নৃবিজ্ঞানী এডমান্ড লীচ্ বিয়ের বিশ্বজনীন সংজ্ঞার সমালোচনা করছেন। যেমন ধরুন, এ ধরনের সংজ্ঞা: “Marriage is a union between a man and a woman such that children born to the woman are the recognized legitimate offspring of both partners.” (বিয়ে হচ্ছে একজন নারী এবং একজন পুরুষের মিলন। এই মিলনের ফলে যে সকল সন্তান জন্ম লাভ করে, তারা দুইজনেরই [স্বামী এবং স্ত্রী] বৈধ সন্তান হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে)।
লীচ প্রশ্ন তুলেছেন: শুধু মাত্র একটি গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কি পৃথিবীর সকল বিয়ের অর্থ, কিংবা কার্য, আদৌ বোঝা সম্ভব? উদ্ধৃত সংজ্ঞায় স্পষ্টতই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (আবারও) সন্তানের বৈধতা – এই একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের উপর। পক্ষান্তরে লীচ প্রস্তাব করছেন যে, বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনকে আমরা দেখতে পারি দুই পক্ষের মাঝে নির্দিষ্ট কিছু “অধিকার গুচ্ছ” (classes of right) তৈরি হওয়া হিসেবে। এই অধিকার গুচ্ছের মধ্যে রয়েছে একজন পুরুষ (পিতা) অথবা নারীর (মাতা) সন্তানের বৈধতা প্রতিষ্ঠা, রয়েছে বিবাহ সঙ্গীর (স্বামী কিংবা স্ত্রী) যৌন ক্ষমতার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা।
রয়েছে গৃহী (domestic) কিংবা শ্রম সেবার ( labour services) উপর অধিকার সৃষ্টি। এই অধিকার গুচ্ছ হতে পারে যৌথ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত, অথবা বিবাহ সঙ্গীর – তার মানে স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর — সম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। আবার এমনও হতে পারে যে বিয়ের – সম্পর্কের অর্থ হচ্ছে শুধু স্বামী নয়, স্বামীর ভাইদের সাথেও বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া। লীচ আরও বলছেন, এই তালিকা কোন ভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয়। হয়তো বা গবেষণা চলাকালীন অবস্থায় নৃবিজ্ঞানী বুঝবেন যে, নির্দিষ্ট কোন সমাজে বিয়ের অর্থ হচ্ছে অন্য কোন কার্য সম্পাদন।
লীচ আরও বলেন, কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজে সকল বৈশিষ্ট্য যে একই সাথে বিদ্যমান থাকবে, তাও নয়। নির্দিষ্ট কোন সমাজে নৃবিজ্ঞানী একটি কিংবা একাধিক অধিকার গুচ্ছ পাবেন। পরিশেষে তিনি বলছেন,”বিয়ে বলতে যে প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়ে থাকে, সকল সমাজে এর একই ধরনের সামাজিক কিংবা আইনী আনুষঙ্গিক ব্যাপার-স্যাপার থাকবে, তা কিন্তু নয়”। লীচের পরামর্শ হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট সমাজে বিয়ের সম্পর্ক সমাজের অপরাপর সম্পর্কের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা উদ্ঘাটন করা।

এ অব্দি আলোচনা হয়েছে বিয়ের সর্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর সমস্যা নিয়ে। মূল বক্তব্য হচ্ছে এ পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানীদের যাবতীয় চেষ্টা কম বেশি ব্যর্থ হয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে। বিয়ের অর্থবহ এবং সকল স্থান-কালের জন্য প্রযোজ্য সংজ্ঞা দাঁড় করাতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন, এমন কোন “কার্য” নেই যা জোর দিয়ে বলা যাবে সকল সমাজের, সকল সময়ের বিয়ের ক্ষেত্রেই সত্য। এ কারণেই সাম্প্রতিককালের নৃবিজ্ঞানীরা সর্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজে, বিশেষ কোন সময়কালে বিয়ের কি ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেটা বোঝার উপরই গুরুত্ব দিচ্ছেন।
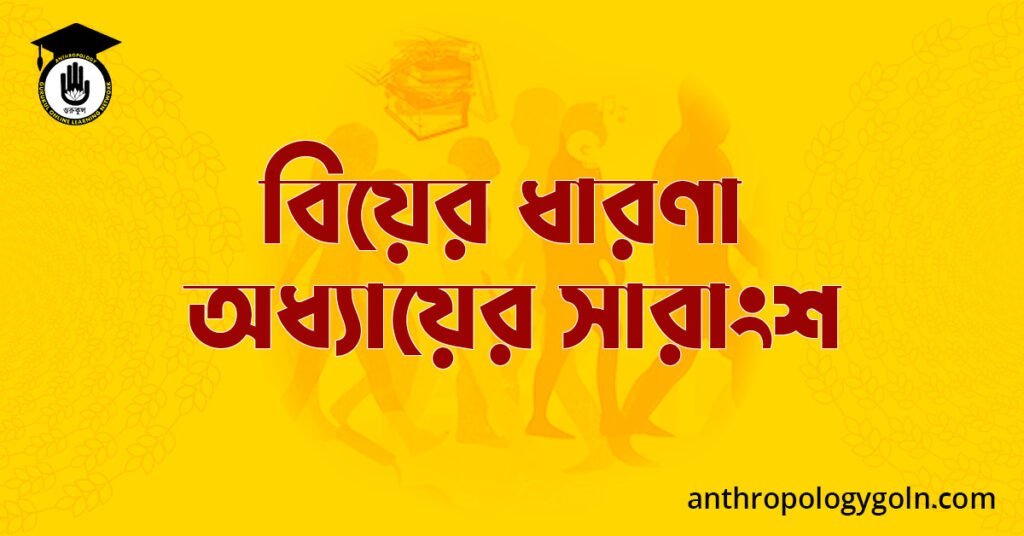
বিয়ের ধারণা অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয় বিয়ের ধারণা অধ্যায়ের সারাংশ – যা বিয়ের ধারণা এবং সংজ্ঞা এর অর্ন্তভুক্ত, প্রায় একশ বছর ধরে নৃবিজ্ঞানীরা বিয়ের একটি বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টায় রত ছিলেন। এই কাজে সমাজ বিজ্ঞানীরাও সহায়তা করেন। তাঁদের এই যৌথ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।
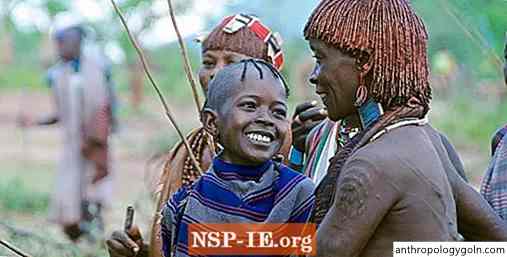
বিয়ের নির্যাস হিসেবে তাঁরা যা কিছু চিহ্নিত করেছেন – যেমন ধরুন, নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ, সন্তানদের বৈধতা প্রদান – তা পৃথিবীর কোন না কোন সমাজের ধ্যানধারণা এবং অনুশীলন দ্বারা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়। ১৯৬০-এর দশক হতে নৃবিজ্ঞানে ‘নির্দিষ্টতার’ উপর গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে অনুভূত হয়। বৈশ্বিক ইতিহাস রচনা করার চাইতে, নির্দিষ্ট কোন সমাজের নির্দিষ্ট ইতিহাস রচনা করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপলব্ধ হয়।

সমাজতান্ত্রিক/মার্ক্সবাদীরা ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতার সাথে সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ, কিভাবে পুঁজিবাদ ‘আকর’ পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে বিবেচিত দেশগুলোতে আমূল সামাজিক বদল ঘটিয়েছে, কিভাবে পুঁজিবাদ অপাশ্চাত্যের সমাজকে রূপান্তরিত করেছে এসব প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করেন।

এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা বিয়ের – প্রসঙ্গে লিঙ্গীয় এবং শ্রেণী সত্তা, এদের অন্তপ্রবিষ্টতা, পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর অধস্তনতা, এবং সামগ্রিক ব্যবস্থার বদল (যেমন ধরুন, পুঁজিবাদের আবির্ভাব ) এসব প্রসঙ্গকে কেন্দ্রে নিয়ে আসা – জরুরী মনে করেছেন ।
আরও দেখুনঃ