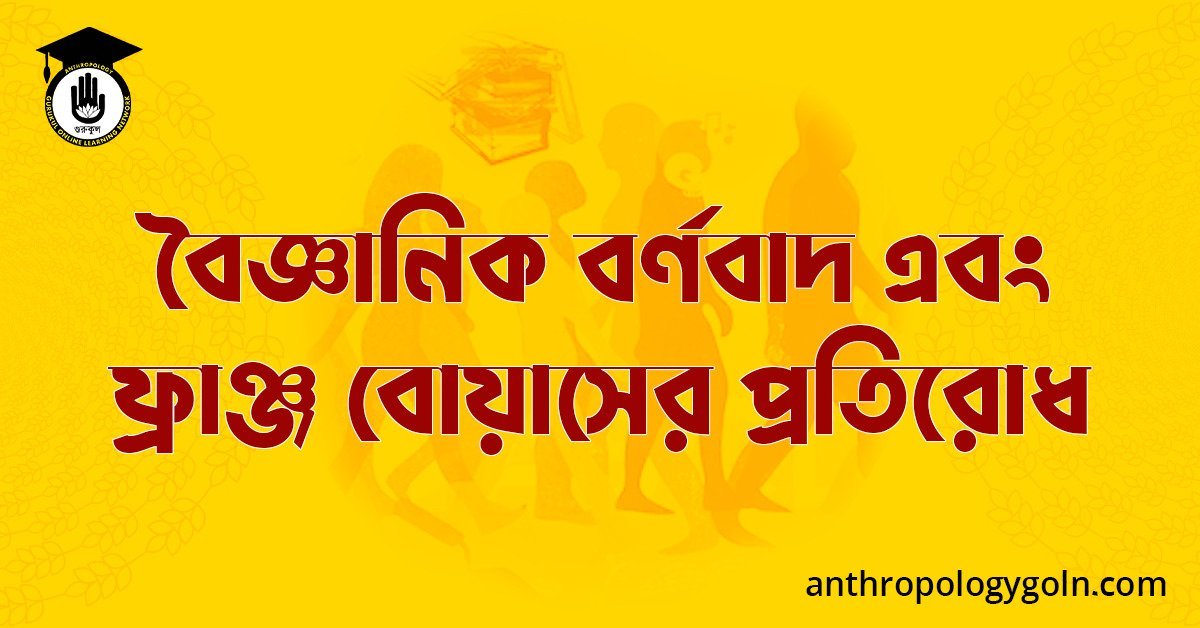আজকের আলোচনার বিষয় বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ এবং ফ্রাঞ্জ বোয়াসের প্রতিরোধ – যা বর্ণবাদের সম্পর্ক এর অর্ন্তভুক্ত, কিছু তত্ত্ব দাবি করে যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে নরবর্ণের উৎকৃষ্টতা এবং নিকৃষ্টতা প্রমাণ করা সম্ভব। এই তত্ত্ব সমষ্টিকে বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ বলা হয়। এ ধরনের তত্ত্বের বক্তব্য হ’ল: নরবর্ণ অনুসারে মানুষের যোগ্যতা ভিন্ন । নিচু নরবর্ণের, জাতিত্বের, শ্রেণীর মানুষজনের বুদ্ধি কম। এই তত্ত্ব অনুসারে, বুদ্ধির তারতম্য সামাজিক অসমতার কারণ। বুদ্ধির এই তারতম্য প্রকৃতি-প্রদত্ত এবং সেই কারণে সামাজিক অসমতা অনিবার্য। বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ বিরোধীরা বলেন, এই তত্ত্বসমূহের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক নয়, মতাদর্শিক। সামাজিক অসমতাকে বৈধতা দানের লক্ষ্যে এই তত্ত্বগুলো তৈরি করা হয়েছে।
অসমতা প্রকৃতি-প্রদত্ত নয়, বরং সামাজিক। বর্ণবাদী মতাদর্শ হচ্ছে ক্ষমতা এবং টাকাপয়সার বৈষম্যকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার প্রচেষ্টা। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক তৈরি হয়। এই বিতর্কে বিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা অংশ নেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, হাল আমলের নয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, পুনরুৎপাদনমূলক প্রযুক্তি) কখনও কখনও, অতি সূক্ষ্মভাবে, পূর্বতন বর্ণবাদী এবং শ্রেণীবাদী চিন্তাভাবনাকে শক্তি-সমর্থন যোগায়।
বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ এবং ফ্রাঞ্জ বোয়াসের প্রতিরোধ

বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদের উৎপত্তি ঘটে ১৮ এবং ১৯ শতকে যখন জীববিজ্ঞান একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকান্ড হিসেবে গড়ে উঠে। বিবর্তনবাদী তত্ত্বের গঠন ও প্রসার অসমতার ধর্মীয় (খ্রিস্টীয়) ব্যাখ্যাকে কোণঠাসা করে। এই প্রেক্ষিতে অসমতার প্রবক্তারা জীববিজ্ঞানের মতন নতুন বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হন। তাঁরা প্রথমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ এবং অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষজনের মগজ (brain) শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির। বিংশ শতকের প্রথম দিকে এই তত্ত্বের অসারতা যখন প্রমাণিত হয় তখন তারা “বুদ্ধি পরীক্ষা” প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।
ইংরেজিতে একে বলা হয় Intelligence Quotient Test অথবা সংক্ষেপে, আই কিউ পরীক্ষা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে, আই কিউ পরীক্ষা পদ্ধতি সমালোচনার সম্মুখীন হয় । সমালোচনা ছিল এরূপ: আই কিউ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে শ্বেতাঙ্গ শিশুদের জানাশোনা বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা বেড়ে ওঠার সময় যা যা শেখে, সেসব বিষয় প্রশ্নপত্রে উপেক্ষিত হয়। এ কারণে তারা আই কিউ পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় না। প্রশ্নপত্রের পক্ষপাতিত্বকে আড়াল করে, আই কিউ পরীক্ষার প্রবক্তারা কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকে দোষারোপ করেন। আই কিউ পরীক্ষা পদ্ধতি দাঁড় করিয়েছিলেন প্রধানত মনোবিজ্ঞানীরা।
ক্ষেত্রবিশেষে, বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জেনেটিসিস্ট দৃষ্টিও বলা হয়ে থাকে কারণ বক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে জিন্স । বর্ণবাদী জেনেটিসিস্টদের বক্তব্য হ’ল, জেনেটিক কারণেই এই বুদ্ধিবৃত্তিক তারতম্য। জেনেটিসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি বাদে আরেকটি বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যার নাম প্রতিবেশবাদী (environmentalist)। প্রতিবেশবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে: জেনেটিক কারণে নয়, প্রতিবেশের কারণে – এট্টটিপূর্ণ সাংস্কৃতিক এবং পারিবারিক জীবনের কারণে – কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের বুদ্ধি কম। তাঁদের মতে, – কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ নজর রাখলে, বিশেষ ধরনের বাস্তবতা গ্রহণ করলে, এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদী এই পরিসরে নৃবিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ বোয়াস (১৮৫৮-১৯৪২) বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁর বক্তব্য ছিল: অসমতা জৈবিক নয়, এটা বরং সামাজিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী সামাজিক কারণে অধস্তন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আফ্রিকানরা স্বতন্ত্রভাবে লৌহ-যুগ পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েছিলেন। ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় পৌঁছে তাদের অধিক উন্নতির সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দেয়। পরবর্তীতে, তিনি খুলির মাপ নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, নিচু বর্ণের মানুষজনের খুলির মাপ সর্বকালের জন্য অপরিবর্তিত থাকেনা।
নতুন প্রতিবেশে নিচু হিসেবে বিবেচিত নরবর্ণের মানুষের খুলির মাপ বদলাতে পারে। নাৎসীবাদ যেভাবে বিজ্ঞানের সহায়তায় আর্য-বর্ণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশরত ছিল, বোয়াস তারও সমালোচনা করেন। নরবর্ণ প্রসঙ্গে বোয়াসের বক্তব্য মার্কিনী নৃবিজ্ঞানে তাত্ত্বিক মাত্রা যোগ করে। বোয়াসের উত্তরসূরীরা পরবর্তী কালে এই ধারায় কাজ করতে থাকেন এবং বর্ণবাদবিরোধী তাত্ত্বিক ধারা তৈরীতে অবদান রাখেন।
১৯৬০ হতে ধীরে ধীরে নরবর্ণ প্রসঙ্গের উত্থাপনের ঢঙ পাল্টে যেতে থাকে। বোয়াস এবং তার উত্তরসূরীরা সমালোচনা দাঁড় করিয়েছিলেন বর্ণবাদী স্তরায়নের বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল সামাজিক পঞ্চরায়নের কারণ জৈবিক নয়, সামাজিক। সে অর্থে, তাঁরা যুক্তি দেখান, নরবর্ণকে জৈবিক বলার কোন অর্থ নেই, যেহেতু নরবর্ণের কোন জৈবিক ভিত্তি নেই। পরবর্তী সময়ে, নৃবিজ্ঞানীদের মনোযোগ “নরবর্ণ” হতে “বর্ণবাদ” এ সরে যায়। এই মনোযোগ এখনও অব্যাহত। এই ধারার নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে, নরবর্ণের কোন জৈবিক ভিত্তি নেই, তা স্পষ্ট। কিন্তু বর্ণবাদ একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো যা পৃথিবীর মানুষজনকে বিভিন্ন স্তরে (উঁচু, নিচু) বিভক্ত করে।
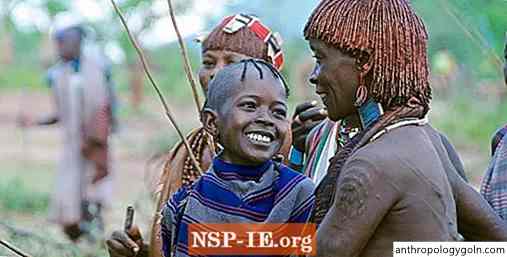
এ স্তরায়ন ও বিভাজন বিশ্বব্যাপী। এবং সেই কারণে “নরবর্ণ নেই”, এই বলে প্রসঙ্গটিকে উড়িয়ে দেয়ার চাইতে, আরো বেশি জরুরী হচ্ছে এর শক্তিমত্তা অনুসন্ধানের কাজে মনোনিবেশ করা। এই উপলব্ধি বিভিন্ন কাজের জন্ম দিয়েছে। কিছু কাজ মার্কিনী সমাজের স্ববিরোধিতা উদ্ঘাটনের উপর জোর দিচ্ছে: মার্কিনী সমাজের একটি মূলনীতি হচ্ছে “সকল মানুষ সমান”, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বর্ণবাদী বৈষম্য। এবং সেটি সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত – শিক্ষা, চাকুরি, বসবাসের এলাকা ইত্যাদি।
কিছু কাজ গুরুত্ব আরোপ করছে বর্ণবাদী বিভাজন বর্তমানে যে নতুন নতুন রূপ লাভ করেছে (“আরব” বনাম “সভ্য”) তার উপর। আবার কিছু নৃবিজ্ঞানী এই নতুন বর্গীকরণের সাথে পূর্বতন বর্গীকরণের ধারাবাহিকতা এবং বিভিন্নতা বিষয়ে গবেষণা করছেন।