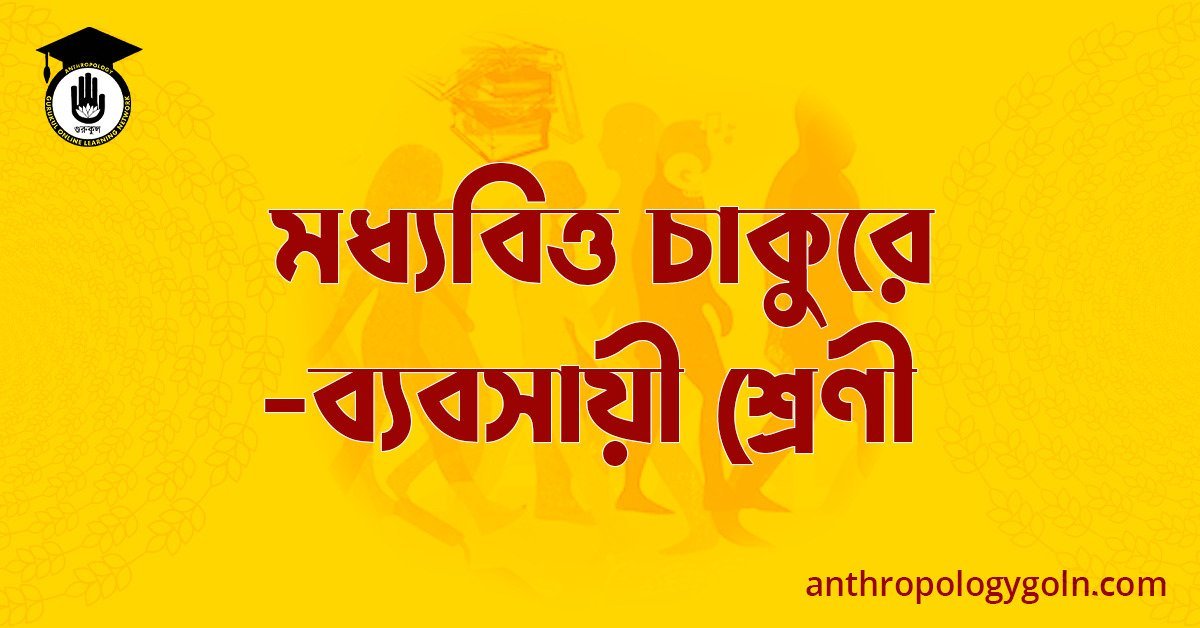আজকের আলোচনার বিষয় মধ্যবিত্ত চাকুরে-ব্যবসায়ী শ্রেণী – যা শ্রেণী ও জাতিবর্ণ স্তরবিভাজ এর অর্ন্তভুক্ত, পুঁজিবাদী সমাজে একটা শ্রেণী আছে যার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে মালিক নয়, আবার শ্রমিকও নয়। এখানে কাজ না পাওয়া শ্রমিকদের কথা হচ্ছে না। একটা স্বচ্ছল শ্রেণীর কথা হচ্ছে। সাধারণভাবে এঁরাই হচ্ছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীর সদস্যরা রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করে থাকেন, কিংবা পণ্যের বাণিজ্য করে থাকেন। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নানাবিধ দপ্তর এবং বিভাগ করা হয়েছে। এই সকল দপ্তর ও বিভাগে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের কিছু কর্মচারী প্রয়োজন পড়ে।
সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে শিক্ষক অব্দি। সেই সকল কর্মচারীরা রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে বেতন পেয়ে থাকেন। এছাড়া সরকারী দপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী দপ্তরে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। চাকুরির আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে শিল্প, কল-কারখানার ব্যবস্থাপনা। যে সব কর্মস্থলে শ্রমিকরা শ্রম দিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করে থাকেন, সেখানে ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজিং-এ অনেক কর্মী চাকুরি করেন যাঁরা শারীরিক শ্রম দিয়ে কিছু উৎপাদন করেন না। তবে তদারকি করেন।
মধ্যবিত্ত চাকুরে-ব্যবসায়ী শ্রেণী

ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে কোন শিল্প-কারখানার মালিক নাও হতে পারেন। তাঁরা এক স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য অন্য স্থানে বেচাকেনার কাজ করে থাকেন। তবে ব্যবসায়ী শব্দটি দিয়ে সাধারণভাবে এত কিছু বোঝায় যে এটি নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটবার সুযোগ আছে। আগের আলোচনায় যাঁদের মালিক বলা হয়েছে তাঁদের অনেকেই নিজেকে পরিচয় দেবেন ব্যবসায়ী বলে। তবে বৃহৎ শিল্প-মালিকদের বেলায় শিল্পোদ্যোক্তা বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পরিচয়টা চলে।
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যদের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য খেয়াল করার মত। প্রথমেই বলা যায় শিক্ষার কথা। | প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন এই শ্রেণীর একটা বৈশিষ্ট্য। আর চাকুরির ক্ষেত্রেও এটা প্রয়োজনীয় বটে। উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেবার পর যে ধরনের চাকুরি করা হয় তাকে বলা হয় হোয়াইট কলার জব।
বাংলায় আমরা সম্মানজনক চাকুরি বলতে পারি। এই শ্রেণীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক উচ্চবিত্তের মতই কঠোর। এঁদের পরস্পরের প্রতি তেমন কোন সংহতি লক্ষ্য করা যায় না। দরিদ্রদের দিক থেকে সেটা সঙ্গত। কারণ প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারের দেখভালের শ্রম তাঁদেরই দিতে হয়। আর সেখানেও তাঁর শোষণের অভিজ্ঞতাই হয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বরং উচ্চবিত্তের দিকেই বেশি টান দেখায়।

এই শ্রেণী আশা-আকাঙ্ক্ষার ধরনও উচ্চবিত্তের সঙ্গে মেলে বেশি। এই শ্রেণীর তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এঁরাও কোন উৎপাদন কাজে অংশ নেন না। সে কারণে কোন কোন বিশে- ষক সমাজের মানুষজনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন উৎপাদক শ্রেণী এবং অনুৎপাদক শ্ৰেণী । প্রথম শ্রেণী হচ্ছে দরিদ্র মানুষজনের, আর অন্য সকলে (মালিক সমেত) অনুৎপাদক শ্রেণী। আবার উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভোগ্যপণ্যের প্রায় সবটারই খদ্দের বলে এঁদের ভোক্তা শ্রেণীও বলা হয়ে থাকে।
সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজ-কর্মকে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সমস্যা হ’ল: গরিব শ্রেণীর পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের আবার তেমন দরকার পড়ে না। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে ধরনের কাজ করে কিংবা পেশায় নিয়োজিত হয় তার ফলাফল কেবল নিজেদের ভোগে ও মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। তা সে গান, নাটক, উপন্যাস হোক আর অফিসের ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করা হোক। কিন্তু গরিব শ্রেণীর গান কিংবা সাহিত্য বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ বলে গণ্য হয় না। অবশ্যই মালিক শ্রেণীর কারখানা বা উৎপাদন ক্ষেত্র চালু রাখার জন্য এই শ্রেণীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীর সকল মহানগর এই শ্রেণীর মানুষজনের আবাসস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এর মানে এই নয় যে অন্যত্র মধ্যবিত্ত নেই কিংবা মহানগরে উচ্চবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষজন থাকেন না। বরং মহানগরের যাবতীয় শারীরিক কাজ-কর্ম দরিদ্র মানুষজনই করছেন – ইমারত বানানো থেকে শুরু করে আবর্জনা পরিষ্কার করা অব্দি। কিন্তু মহানগরের মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। যেহেতু চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী মানুষজন ও তাঁদের পরিবারকে মধ্যবিত্ত ধরে নেয়া হয়েছে তাই মধ্যবিত্ত বলতে মোটেই এক ধরনের স্বচ্ছলতা বোঝায় না। ঢাকা শহরের এ্যাপার্টমেন্টে বসবাসকারী পরিবার যেমন মধ্যবিত্ত, তেমনি গাইবান্ধার একজন মনোহারী দোকানদার মধ্যবিত্ত।

মহানগরের মধ্যবিত্তদের গুরুত্ব হচ্ছে তাঁরাই সমাজের ধ্যান ধারণা নিয়ন্ত্রণ করেন। শিল্প-সাহিত্য, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত চিন্তা ভাবনাকেই প্রতিফলিত করে, দরিদ্রদের নয়। এ কারণেই কারো কারো মতে শ্রমিক শ্রেণী বা দরিদ্র মানুষদের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বড় বাধা।