আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় মাইনোসীয় – মাইসিনীয় সভ্যতা। মাইসিনীয় গ্রিস (বা মাইসিনীয় সভ্যতা) প্রাচীন গ্রিসের ব্রোঞ্জ যুগের সর্বশেষ পর্যায়। ১৬০০-১১০০ খ্রিস্টপূর্ব জুড়ে এর স্থায়িত্ব। গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে এটিই প্রথম উন্নত এবং স্বতন্ত্র গ্রিক সভ্যতা। প্রাসাদ-প্রকরভিত্তিক রাজ্য, নগরভিত্তিক কাঠামো, শিল্পকর্ম এবং লিখনপদ্ধতির দ্বারা তা প্রতীয়মান হয়।
মাইনোসীয় – মাইসিনীয় সভ্যতা

মাইনোসীয় – মাইসিনীয় সভ্যতা
ঘটনাক্রমে হিট্টাইট সভ্যতা এবং মাইনোসীয়-মাইসিনীয় সভ্যতা৷ উভয়ের অস্তিত্বের আবিষ্কার প্রায় একই সময়ে ঘটে। ১৮৭০ সালের আগে কেউ ধারণাও করেনি যে, ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপমালায় এবং এশিয়া মাইনরের উপকূলে গ্রীসীয় সভ্যতার উদয়ের আগে এক অত্যুচ্চ সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল।
১৮৭০ সালে হাইনরিখ শ্লিমান নামক একজন জার্মান ব্যবসায়ী ও সৌখিন পুরাতাত্ত্বিক ‘ইলিয়াড’ মহাকাব্যে বর্ণিত ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করার মানসে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু করেন এবং এ কাজে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। তিনি এশিয়া মাইনরে ট্রয় এবং মূল গ্রীক ভূখণ্ডে মাইসিনী ছাড়াও আরো একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ঘাটন করেন।
অতঃপর ইংরেজ পুরাতাত্ত্বিক স্যার আর্থার ইভান্স প্রাচীন ক্রীটের রাজধানী নোসস্ আবিষ্কার করে প্রাচীন ক্রীটীয় সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। প্রাচীন ক্রীটের রাজাদের ‘মাইনোস’ নাম অনুসারে ক্রীটীয় সভ্যতাকে মাইনোসীয় সভ্যতা নামেও অভিহিত করা হয়। ক্রীটীয় সভ্যতা ও মাইসিনীয় সভ্যতাকে একত্রে ‘মাইনোসীয়-মাইসিনীয়’ সভ্যতারূপে অভিহিত করা হয়। এ উভয় সভ্যতাকে ঈজিয়ান সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে।
ইতিপূর্বে আমরা যে নগর-বিপ্লবের বিবরণ দিয়েছি তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, যে পলিভূমির উদ্বৃত্ত ফলনের ওপর নির্ভর করে ধাতুশিল্পভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠত, সে সকল পলিভূমিতে স্বভাবতই খনিজ সম্পদের স্বল্পতা ছিল। এ সকল অঞ্চলে তাই ধাতু আমদানি করতে হতঃ তামা আসত ইরান, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, সিনাই থেকে; সোনা আর্মেনিয়া ও নুবিয়া থেকে; রূপা ও সীসা কাপাডোসিয়া থেকে।
বাণিজ্য ছিল তাই এ সব ব্রোঞ্জযুগীয় অর্থনীতির জীবনস্বরূপ এবং যতই এর প্রসার ঘটে ততই তা নতুন পাথর যুগে গ্রাম ও পার্বত্য গোষ্ঠীসমূহকে সভ্যতার আওতায় টেনে আনে । ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই তামার ব্যবহার সারা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু তা সার্বজনীন ছিল না। এ ধাতু যেসব জায়গায় প্রচুর উৎপন্ন হত সেখানেও লোকেরা তার সাহায্যে স্থানীয় শিল্প গড়ে না তুলে তা রপ্তানি করত।
তাই মেসোপটেমিয়া ও মিশরের বাইরের যেসব নগরের উদয় হয়েছিল তা ছিল মূলত বাণিজ্যকেন্দ্র। যেমন, সিরিয়াতে যেখানে তামা, টিন ও কাঠের প্রাচুর্য ছিল— সেখানে বিলস্, উগারিট প্রভৃতি একগুচ্ছ নগর গড়ে ওঠে, যাদের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তিই ছিল মিশর, মেসোপটেমিয়া ও আনাতোলিয়ার সাথে বাণিজ্য। সভ্যতা এ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর নগর-বিপ্লব ভূমধ্যসাগরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছিল সস্তায় জলপথে চলাচলের সুবিধা।

কিন্তু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাইপ্রাসের সভ্যতার বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, সিরীয় উপকূলের উন্নত সভ্যতার কাছাকাছি থাকার ফলে সাইপ্রাসবাসীরা তামাশিল্পভিত্তিক সভ্যতা না গড়ে তামা রপ্তানি করত। তা ছাড়া আনাতোলিয়ার দক্ষিণ উপকূলের নিকটবর্তী অবস্থান বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূলও ছিল না। কিন্তু ক্রীটের অবস্থা ছিল অন্যরকম। সিরিয়া ও মিশর থেকে সমদূরস্থিত এ দ্বীপটি ঈজিয়ান সাগরের প্রায় প্রবেশমুখে অবস্থিত ছিল।
ক্রীটের কৃষিসম্পদ মিশর ইত্যাদির তুলনায় কম হলেও তা ছিল সীমিত আয়তনের। সেখানে ছিল চারণভূমি, আর ছিল শস্য, জলপাই, আঙ্গুর ইত্যাদির উপযুক্ত উর্বর ভূমি, কিন্তু দ্বীপের বৃহৎ অংশই ছিল পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ। অপরপক্ষে, জলযান নির্মাণের উপযুক্ত কাঠের প্রাচুর্য ও ভাল বন্দরের সুযোগ থাকায় দ্বীপবাসীরা অনেক আগে থেকেই জলপথে চলাচলের সুবিধা গ্রহণ করে। ফলে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকেই ক্রীটের অধিবাসীরা বাণিজ্যভিত্তিক নগরসভ্যতা গড়ে তোলে।
এরা রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করত প্রধানত মদ্য ও জলপাইয়ের তেল, মৃৎপাত্র, রত্ন ও আঙ্গুরীয়, ছুরি ও কৃপাণ এবং কারিগর-নির্মিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি, আর আমদানি করত খাদ্যদ্রব্য ও ধাতু। এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশটি সমৃদ্ধ নগরমালা সমন্বিত এক শিল্প-সমৃদ্ধ সভ্যতায় পরিণত হয় এবং নিকটস্থ সভ্যজগতের সাথে তার ব্যাপক সংযোগ স্থাপিত হয়।
ক্রীটীয় সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে (২৯০০-২২০০ খ্রিঃ পূঃ), তখন ধাতুর প্রচলন হয়েছে, বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল মিশর ও সাইক্লেস্ দ্বীপপুঞ্জের সাথে এবং নগর বিকাশ তখন দ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে সীমিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২২০০-১৬০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) আমরা লক্ষ্য করি জনসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি, ব্রোঞ্জের প্রচলন, মিশরের সাথে ব্যাপক বাণিজ্য ও সিরিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।
১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অনতিকাল পরে কাসাইটরা ব্যবিলন আক্রমণ করলে প্রাচ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সিরিয়ার সাথে সংযোগ ছিন্ন হয়; ক্রীটীয়রা তখন ঈজিয়ানের দিকে মুখ ফেরায়। তারা সাইক্লেস্-এর সাথে সম্পর্ক জোরদার করে এবং মধ্যগ্রীস পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নোসস্ ও ফিস্টস্ নগরদ্বয়ের নেতৃত্বে ক্রীটীয় সভ্যতা উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করে। সম্প্রতি ক্রীটের পূর্ব উপকূলে কাটো জাক্রোস্ নামে আরেকটি সমৃদ্ধ নগরীর সন্ধান পাওয়া গেছে।
এখানে ২৫০টি কক্ষবিশিষ্ট এক বিরাট প্রাসাদ ও সাঁতারের পুকুর এবং হাজার হাজার অলঙ্করণযুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। ক্রীটীয় সভ্যতার শেষ পর্যায়ে (১৬০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নোসস্-এর রাজা বহুসংখ্যক রাস্তা তৈরি করেন ও তার পাশে পাশে সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপন করে সমস্ত দ্বীপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং সাগরপারে সাইক্লেস্, আগোলিস, এ্যাটিকা ও সম্ভবত সিসিলি পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু এ সমৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে পরবর্তীকালে একিয়ান নামে পরিচিত একদল গ্রীক বর্বর গোষ্ঠীর মানুষ উত্তর পেলোপনেসাস্ থেকে অগ্রসর হয়ে ক্রমে মাইসিনি অধিকার করে। ক্রমশ পরাজিত জাতির বৈষয়িক সংস্কৃতি আয়ত্ত করে তারা সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে তারা নোসস্ জয় করে নেয় এবং তার অনতিকাল পরেই সমগ্র ক্রীটে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

এরপর সাবেক ক্রীটীয় সাম্রাজ্য মাইসিনিকে কেন্দ্র করে কয়েক শতাব্দী টিকে ছিল। মাইসিনীয় আধিপত্যের যুগে ক্রীটীয় সংস্কৃতির অবনতি ঘটেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাইসিনীয়রা ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়, কিন্তু তার দু’শো বছরের মধ্যে নিজেরাই বর্বর আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে। এ নবাগত দলও ছিল গ্রীসীয়, তবে তারা ছিল ডোরিয়ান দলের এবং সম্ভবত বলকান উপদ্বীপ থেকে এরা এসেছিল।
এদের সংস্কৃতি ছিল আদিম ধরনের, তবে এরা লোহার ব্যবহার শিখেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে এরা গ্রীসীয় ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল; তারপর তারা ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হয়। ১২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এরা মাইসিনীয় নগরসমূহ জয় করে নেয়। এর দু’শো বছর পরে ক্রীটীয়-মাইসিনীয় সভ্যতার চিহ্ন ইতিহাসের অঙ্গন থেকে মুছে যায়। মাইসিনীয় সভ্যতার দ্রুত অবসানের বিশেষ কারণ ছিল।
তারা মাইনোসীয় সংস্কৃতির কারিগরি অবদানসমূহকে যুদ্ধে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল। বিশেষত তারা ঘোড়া ও যুদ্ধরথ, নতুন ধরনের তলোয়ার, শিরস্ত্রাণ, দেহবর্ম ইত্যাদির প্রচলন করেছিল। কিন্তু উৎপাদনযন্ত্রের বিকাশের তারা কোনো চেষ্টাই করেনি। ফলে নতুন আক্রমণকারীদের সামনে তারা টিকতে পারেনি। কারণ, নবাগতরা লোহার অস্ত্রের ব্যবহার জানত।
তদুপরি, ডোরিয়ানরা আদিম গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল বলে সভ্য জাতিসমূহের মতো তাদের অস্ত্র কোনো বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষিগত ছিল না, তাদের লোহার অস্ত্র দলের সকল মানুষের আয়ত্তে ছিল। তাই এ বিষয়টা লক্ষণীয় যে, ঈজিয়ান বক্ষে ব্রোঞ্জযুগের অবসান গ্রীসীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাথে যুক্ত ছিল। মাইনোসীয় সভ্যতা সম্ভবত ছিল নিকট-প্রাচ্যের সভ্যতাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মুক্ত, স্বাধীন ও প্রগতিশীল।
ক্রীটীয় শাসকরা ফারাও-এর অনুকরণে মাইনোস উপাধি ধারণ করলেও এঁরা কোনো যুদ্ধবাজ শাসক ছিলেন না। তাঁদের স্থায়ী সেনাবাহিনীর আকার ছিল ছোট, তাঁদের কোনো সুরক্ষিত নগরী ছিল না এবং বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যসংগ্রহের কোনো নজিরও পাওয়া যায় না। তাদের অবশ্য বৃহৎ নৌবাহিনী ছিল, কিন্তু তা’ ছিল বাইরের আক্রমণ রোধ ও বাণিজ্য-বহরের সংরক্ষণের জন্যে, প্রজার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে নয়।
ক্রীটের নগর পরিকল্পনার মধ্যেও সহজ ও স্বাধীন সামাজিক সম্পর্কের লক্ষণ অনুভব করা যায়। মাইনোসীয় নগর গড়ে উঠত রাজপ্রাসাদ ও তার সংলগ্ন চত্বরকে কেন্দ্র করে। এ রাজা আবার প্রধান পুরোহিতও ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত বণিকরাজা।
রাজপ্রাসাদের চারপাশে থাকত অন্যান্য বণিকদের প্রাসাদ, তার চারপাশে কারিগর ও সাধারণ মানুষের বাড়ি। কিন্তু রাজা, অভিজাত ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের বাসগৃহের মধ্যে কোনো রকম প্রাচীরের ব্যবধান ছিল না। বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে ভূস্বামীদের হাতে সম্পদ তথা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে পারেনি; সে কারণেই মিশর-ব্যবিলন থেকে ভিন্নতর ধারায় সামাজিক বিকাশ এখানে সম্ভব হয়েছিল।
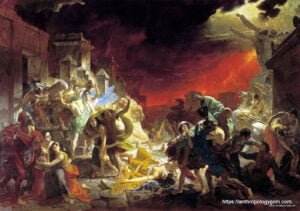
এ বিষয়ে মাইনোসীয় সভ্যতা থেকে মাইসিনীয় সভ্যতার পার্থক্য ছিল। মাইসিনীয় নগর গড়ে উঠত সুরক্ষিত দুর্গকে কেন্দ্র করে। দুর্গ-প্রাকারের অভ্যন্তরে থাকত রাজপ্রাসাদ, রাজভাণ্ডার, তার চারপাশে থাকত অভিজাতদের প্রাসাদ। দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে থাকত কারিগর ও ব্যবসায়ীদের বাসগৃহ। এরা রাজবাড়ির প্রয়োজন মেটাত। মাইসিনীয় সভ্যতায় শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল ব্রোঞ্জের একচেটিয়া আধিপত্যের ভিত্তিতে।
আরও দেখুন :
