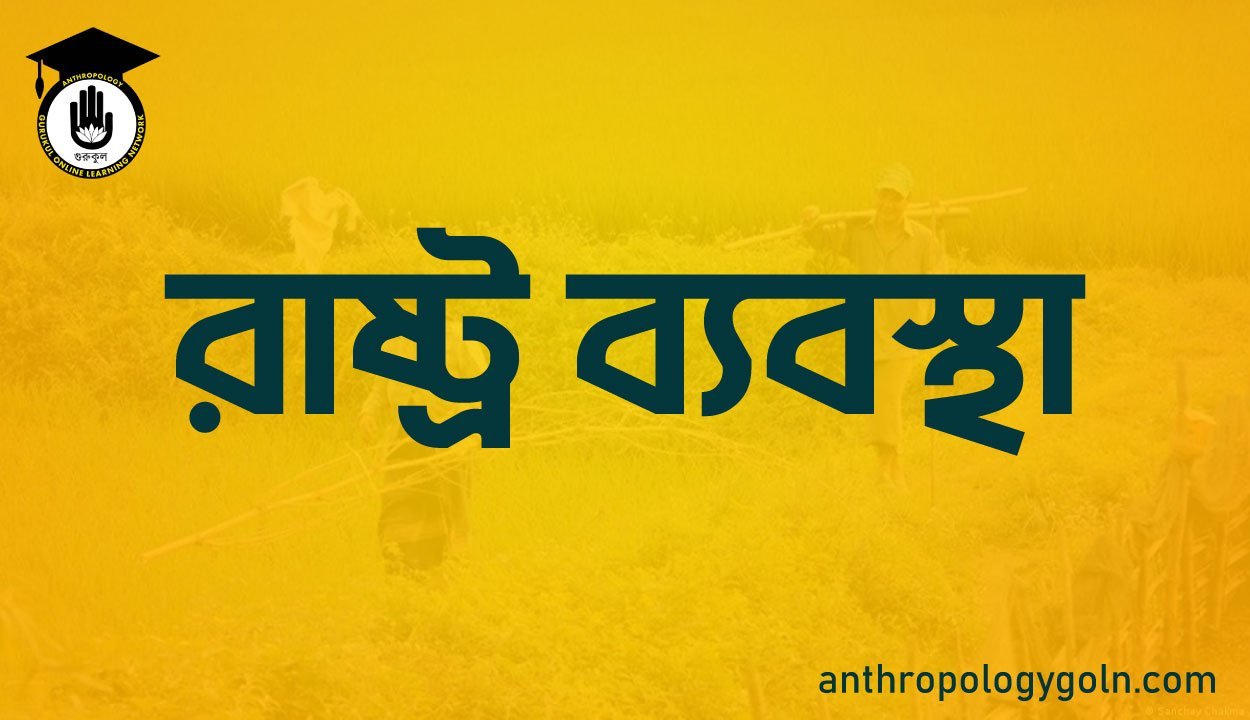আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও নৃবিজ্ঞান | যেখানে রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ,গৃহ যুদ্ধ ,সহিংসতা এবং সন্ত্রাস ছিল খুব সাধারন একটা বিষয় সেখানে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে মাঠ গবেষনা করা অনেক বেশি কঠিন অথবা অপ্রিয় ছিল তাই রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান বিগত ঔপনিবেশিকতাবাদ এর অধ্যয়নের দিকে অধিকতর ঝুকে পড়েছিল । রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং অপব্যবহারের সমালোচনামুলক নিবন্ধনের অধ্যায়নের মাধ্যমে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট এলাকা সীমাবদ্ধ করেছিল এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার স্বাতন্ত্র গল্প এবং অস্থায়ী বাসস্থান, প্রতিদন্দ্বিতা ,তলোয়ার যুদ্ধে ক্ষিপ্র প্রত্যাঘাতে সাধারনত অনেক অবদান রেখেছিল । রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা আধিপত্য শ্রেণির বিপরীতে মৌখিক ইতিহাস , লোক গল্প , ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা , ঢোল উৎসব এবং নারীদের অসুস্থতা শুধুমাত্র কিছু এথনোগ্রাফিক কেস স্ট্যাডি হিসেবে উপলব্ধি করতে পেরেছে ।
রাষ্ট্র ব্যবস্থা

আমরা যে সময়কালে জন্মেছি সেই সময়কালে রাষ্ট্রের অর্থ দুনিয়া ব্যাপী বিস্তার হয়েছে। রাষ্ট্র ছাড়া কোন সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করাই অসম্ভব এখন। কেবল তাই নয়, সকল সমাজে রাষ্ট্রের চেহারা একই রকম দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো যখন দুনিয়া জুড়ে বাণিজ্য করতে বের হয়েছে। এর মানে এই নয় যে বাইরের শক্তি আসবার আগে পৃথিবীর সকল স্থানে একই রকম অবস্থা ছিল। বরং, তখন এক এক অঞ্চলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেহারা ভিন্ন ভিন্ন ছিল।
সেটা ভাল না মন্দ তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। বোঝার বিষয় হ’ল: আধুনিক কালে সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা কাঠামোর দিক থেকেও, আবার সাধারণ মানুষের চিন্তা- ভাবনার দিক থেকেও। আর এটা ঘটেছে ইউরোপীয় শক্তির বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থেকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের চারটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:
ক) রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষমতার একটা কেন্দ্রীভূত এবং ক্রমোচ্চ ব্যবস্থা। অর্থাৎ পূর্বতন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে নানা প্রকার শিথিলতা ছিল, এবং ক্ষমতা কোন নির্দিষ্ট একটা জায়গায় জড়ো ছিল না, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা জড়ো হয়েছে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানে। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চীফডমও বটে। তবে রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে একেবারে চূড়ান্ত উদাহরণ।
আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানাবিধভাবে ক্ষমতার নানা স্তর থাকে। কখনো সেটা সরাসরি নানান দপ্তরের মাধ্যমে, কখনো অনানুষ্ঠানিকভাবে। আর সম্পদের ভিত্তিতে ক্ষমতা এখানে নিশ্চিত হয়েছে। যাবতীয় সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম। কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র – যেমন: সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান কিউবা ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। কিংবা সম্পদ বলতে খুব সামান্য জিনিসই আবিষ্কার হয়েছিল।
খ) রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পদশালীর অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। ক্ষমতা এবং মর্যাদা উভয়েই সম্পদের পাশাপাশি বেড়ে যায় এখানে। এর মানে এই নয় যে অন্য কোন উপায়ে এখানে মর্যাদাবান হবার পথ নেই। কিন্তু সম্পদ যেহেতু ব্যক্তির হাতেই থাকতে পারে – তাই সম্পদের বাড়তি সুবিধা ব্যক্তির পক্ষে – নেয়া সম্ভব হয় এই ব্যবস্থায়। ফলে ব্যক্তিগত মনোভাব বেড়ে যায়। আগের ব্যবস্থায় যেখানে সামাজিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব ছিল অধিক, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।
গ) রাষ্ট্রে শক্তি বা বল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং অনেক শক্তিশালীভাবে কাজ করে। সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের হাতে নানান শক্তি সঞ্চিত থাকে। রাষ্ট্র সেটা প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করতে পারে। সাধারণভাবে ভাবা হয় কোন অশুভ শক্তির বিপক্ষে এই সব বাহিনী কাজ করে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাস বলে যে এই সব শক্তি মূলত ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ মানুষের বিপক্ষে। উপরন্তু, নানাবিধ আধুনিক অস্ত্রের আবিষ্কার রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে পোক্ত করেছে।
ঘ) রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় লিখিত আইনের শক্তি বিশাল। আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে যাবতীয় কথ্য ঐতিহ্য বিলীন এবং গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। আগেকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক নিয়ম-কানুনের উৎস ছিল মানুষের বিচার বুদ্ধি এবং কথ্য অভিজ্ঞতা। আধুনিক রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম লিখিত আইন দ্বারা পোক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর পক্ষে হত্যাযজ্ঞ করাও সম্ভব হয়। আর তা আইনের দ্বারা অনুমোদন পায়। লেখ্য ব্যবস্থার শক্তি বুঝতে চাইলে আর একটি বিষয় উলে- খ করা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রের সীমারেখা খুবই গুরুত্ব বহন করে।
বহু দেশের মধ্যে এই সীমারেখার সঠিক মাপ নিয়েই যুদ্ধ হবার নজির আছে। আর এই সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় ভূগোলবিদের অঙ্কনের মাধ্যমে। কখনো কখনো রাষ্ট্র বলতে আমরা ঐ আকা ছবিটাই মনে করতে পারি কেবল।
রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং বিস্তার
রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে লেখাপড়ার জগতে বিতর্ক আছে। বিতর্কটা বহুদিন ধরেই চলছে। বিতর্কটার প্রেক্ষাপট হচ্ছে রাষ্ট্রের ভূমিকা। এর মানে হ’ল রাষ্ট্র মানুষের জন্য কল্যাণকর কিনা সেই তর্কের উপরেই ব্যাখ্যাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। অনেকেই মনে করেন রাষ্ট্র মানুষের উপকার করে থাকে, তাদের সেবা দিয়ে থাকে। অন্যদের যুক্তি হচ্ছে: রাষ্ট্র প্রধানত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করে এবং ধন-সম্পদশালীদের সম্পত্তি পাহারা দিয়ে থাকে।
এই দুই অবস্থান থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে বড় সড় দুইটা ঘাঁটি লেখাপড়ার জগতে আছে। একদিকে, কোন কোন পন্ডিত ব্যাখ্যা দেন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, চুক্তির মাধ্যমে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রকে যাঁরা দমনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে থাকেন তাঁদের ব্যাখ্যা হচ্ছে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে সমাজের শক্তিশালীদের সংঘ হিসেবে।
নৃবিজ্ঞান এবং প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে বেশ কিছু তাত্ত্বিক এর থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। তাঁরা প্রযুক্তি এবং পরিবেশকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সেটা শুরুতে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় হলেও পরবর্তীতে নানারকম সমালোচনার মধ্যে পড়ে। সমালোচকগণ এই ব্যাখ্যার অসারতাগুলো চিহ্নিত করেন। এই মুহূর্তে নৃবিজ্ঞানে চলমান বিতর্কগুলোকে বিবেচনা করলে মোটামুটি তিন ধরনের চিন্তাধারা পাওয়া যায় ।
প্রথমটি প্রযুক্তি ও পরিবেশ ধারা। এই ধারার চিন্তাবিদদের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে মূলত পরিবেশ এবং প্রযুক্তির বদলের কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। পরিবেশের দিক থেকে চিন্তা করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জনসংখ্যা বাড়বার কারণে মানুষের পক্ষে ছোট দলের সমাজ ব্যবস্থাতে থাকা সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে, কারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেড়ে উঠেছে কৃষিভিত্তিক সমাজের সাথে সাথে। তাই কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা হ’ল কৃষির উন্নতির সাথে সাথে উৎপাদন বেড়ে গেল। একই সঙ্গে তা জটিল ব্যবস্থারও হয়ে গেছে।

ফলে সমাজের ব্যবস্থাপনা করা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেচ বা এই ধরনের সুযোগ কৃষি কাজে সরবরাহ করবার জন্যও সাংগঠনিক কাঠামোর দরকার পড়েছিল। রাষ্ট্রের মত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এইসব তাগিদ থেকেই।
তাঁদের ব্যাখ্যার পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো হয়ে থাকে। তা হচ্ছে: পৃথিবীর আদি সভ্যতার সবগুলিই কোন না কোন নদীর পাশে। যেমন: সিন্ধু সভ্যতা সিন্ধু নদের পাড়ে। মিশর সভ্যতা নীল নদের পাড়ে, আর চীনের সভ্যতা হোয়াং হো’র পাড়ে অবস্থিত। এর মাধ্যমে বোঝা যায় সেচ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে। এই ধারার চিন্তা-ভাবনা থেকে আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না।
দ্বিতীয় ধারার নাম দেয়া যেতে পারে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র (political economy) ধারা। এই ধারাতে ভাবা হয়ে থাকে সমাজে সম্পদের ধরন বদলাবার সাথে সাথে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবার একটা দল তৈরি হয়েছে। সমাজে এভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানা তৈরি হয়েছে। সম্পদ জড়ো করা এই দলকে ধনী শ্ৰেণী বা মালিক শ্ৰেণী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য শ্রেণী শ্রম দেয় এবং সেই সম্পদ তৈরি করে থাকে। আপনারা অর্থনৈতিক সংগঠন অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা দেখেছেন।
সম্পদ যখন কোন শ্রেণীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে তখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করবার। এ ছাড়াও বঞ্চিত শ্রেণী যেহেতু পরিশ্রম করে সেগুলো উৎপাদন করে, তারাও মালিকদের সম্পত্তিকে দখল করতে চাইতে পারে। ফলে উঁচু শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিল। আর তারা নিজেদের এই আয়েশী উৎপাদন না করা জীবন রক্ষা করতেও চাইল। এভাবে সমাজে প্রহরী রাখার ব্যবস্থা চালু হ’ল। এই প্রহরী দলই সামরিক বাহিনীর সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণীকে চাপে রাখা এবং দমন করে রেখে নিজেদের সুবিধা বজায় রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।
দমন করবার সেই প্রাথমিক ব্যবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে বহু দপ্তর তৈরি হয়েছে। এই চিন্তাধারা থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে অন্য রাষ্ট্রকে কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করে। ইউরোপে শিল্পের বিকাশের পর মালিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর সম্পদ জড়ো হয়েছে। কৃষির পর শিল্প আসার পর মুনাফা বা লাভের নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। মুনাফার লোভে নতুন দেশ থেকে কাঁচামাল পাবার জন্য আক্রমণ করার নজির আছে। তাছাড়া আছে কোন উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিয়ে লড়াই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এর ভাল উদাহরণ।
তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেছনে উগ্র জাতীয়তাবাদ কাজ করেছে, সেই সাথে আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারও আছে। এই ধারার চিন্তুকগণ জাতীয়তাবাদকেও উচ্চ শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত করে দেখেছেন। তৃতীয় ধারাকে আমরা ঐতিহাসিক ধারা বলতে পারি। এই ধারার প্রধান আগ্রহ ঔপনিবেশিক ইতিহাস নিয়ে। উপনিবেশ গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। এর মাধ্যমে পৃথিবী ব্যাপী, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন।
ঔপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে জড়ো করতে চেয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি তারা অর্জন করেছিল। উপনিবেশ স্থাপন করবার আগের সময়কালে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছে। বাস্তবে এই পার্থক্যটাই অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বড় পার্থক্য ছিল। উপনিবেশ স্থাপনার মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ জড়ো হয়েছে ইউরোপে। শিল্প উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল পেয়েছে তারা উপনিবেশ থেকে।
আর এভাবে উপনিবেশের সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই দুর্বল কাঠামোর উপরেই ইউরোপের দর্শন এবং চিন্তা-ভাবনা সমেত আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সকল এলাকা থেকে উপনিবেশ সরে গেছে তখন এই রাষ্ট্র কাঠামো থেকে গেছে। তখন অন্য দেশগুলো হতে বাণিজ্যের মাধ্যমে সুবিধা বজায় রেখেছে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যেহেতু শিল্পভিত্তিক উৎপাদনের চাহিদা তখন এইসব রাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে। ফলে একটা দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পাঠ করা দরকার বলে এই ধারা যুক্তি দেখায় ।
শ্রেণী ভেদাভেদ
রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে সম্পদশালীর বাড়তি ক্ষমতা এবং সুযোগ থাকে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিশেষভাবে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে শিল্পভিত্তিক সমাজে। শিল্পভিত্তিক সমাজে পূর্বতন সমাজ অপেক্ষা সম্পদের ধরন এবং পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পাশাপাশি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যাপক চল বাড়ে। ফলে সেই ভোগ করবার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য হবার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী ভোগ করবার সেই সুযোগ পেয়ে থাকে। রাষ্ট্রের আইন কানুন ও তৈরি হয়ে থাকে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য।
এমন কোন নজির পাওয়া যাবে না যেখানে কোন রাষ্ট্রের আইনে ব্যক্তির হাতে অধিক সম্পদ থাকাকে অপরাধ বলে দেখা হয়। কিছু সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু সেখানেও সম্পদশালী শ্রেণী অল্প বেশি ছিল। পক্ষান্তরে, শ্রমিকদের আয় হবে কতটা তাও রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন বা দপ্তর দেখভাল করে থাকে।
কখনোই শ্রমিকদের এরকম আয়ের পথ থাকে না যে তাঁরা অনেক ভোগ্যপণ্য খরিদ করবেন কিংবা অবকাশ কাটাবেন। ভোগ্যপণ্য, আরাম-আয়েশ এবং অবকাশ একেবারেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষজনের জন্য বরাদ্দ। এ কথা ঠিক যে শিল্পোন্নত কিছু দেশে শ্রমিকদের আয় তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিকদের থেকে বহুগুণ বেশি এবং বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধাও তাঁরা পেয়ে থাকেন। কিন্তু সেই অবস্থা তাঁদের নিজ দেশের ধনীদের তুলনায় নগণ্য ।
রাষ্ট্র ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেকার এই পার্থক্য নানাভাবে টিকিয়ে রাখা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে সংসদ থাকে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কার্যসূচি জনগণকে জানিয়ে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে সেই সংসদে বসে আলাপ-বিতর্ক করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এছাড়া আছে শক্তিশালী বিচারালয়। এত কিছুর মধ্য দিয়ে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর জন্য বড় ধরনের কোন পরিবর্তনের নজির নেই। বরং কোন কোন বিশ্লেষকের মতে এই বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এই বিভাগগুলো কাজ করে থাকে।

বলপ্রয়োগ ব্যবস্থা
রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবচেয়ে ভয়ানক দিক হচ্ছে এখানে নিয়ম মাফিক বল প্রয়োগ করবার যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই শক্তিশালী সামরিক বাহিনী আছে, পুলিশ বাহিনী আছে, সীমানা রক্ষী বাহিনী আছে। এই সব বাহিনীকে যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা সম্ভব। সাধারণভাবে সীমানা প্রহরীদের কাজ দেশের সীমারেখাতে বাইরের কাউকে বা অবৈধ দ্রব্যাদি ঢুকতে না দেয়া। সামরিক বাহিনীর কাজ হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের সীমারেখা থেকে বহিঃশত্রুকে হঠিয়ে দেয়া। প্রয়োজনে সেই শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা। তবে ইদানিংকার দুনিয়ায় কোন দুইটা রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে নিজেরা কোন ফল আনতে পারে না।
শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করে। সাম্প্রতিক কালে উপসাগরীয় যুদ্ধ তার বড় প্রমাণ। পুলিশ বাহিনীর কাজ হচ্ছে দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সেটা করবার জন্য নিয়ম মাফিক প্রচুর ক্ষমতা তাদের হাতে দেয়া আছে। বাস্তবিক পক্ষে সমাজের প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের আছে, যা কিনা অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোতে ছিল না। সেটাই অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।
আরও দেখুনঃ