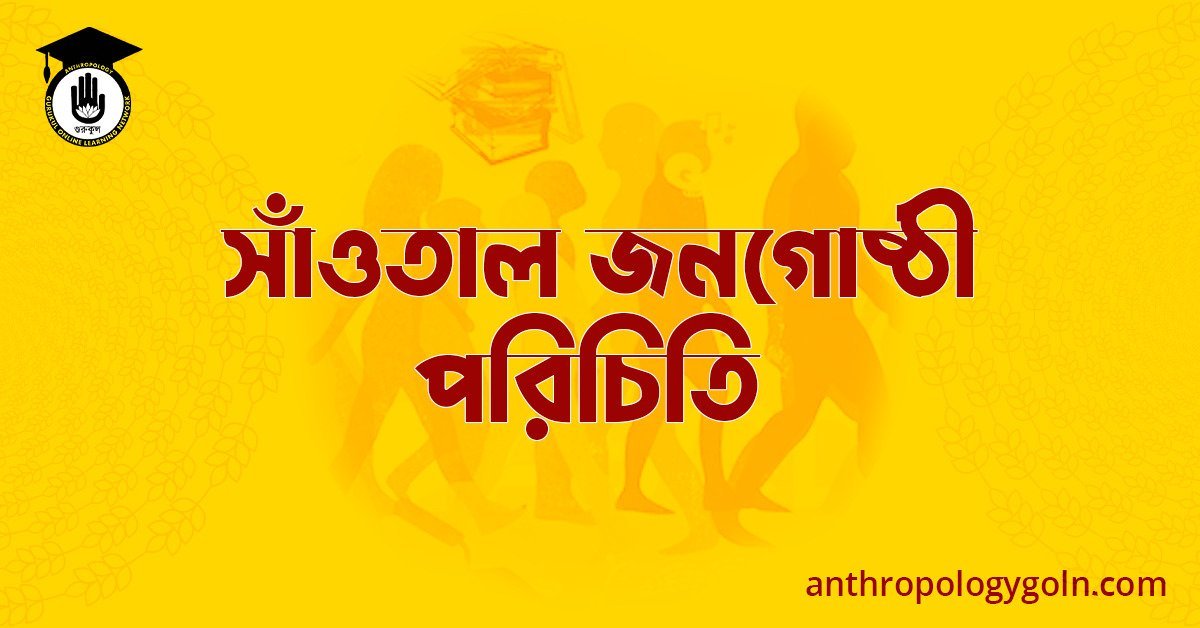আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সাঁওতাল জনগোষ্ঠী পরিচিতি নিয়ে। সাঁওতালদের সম্পর্কে আপনি কতটা জানেন, কিভাবে জানেন, একটু ভেবে দেখবেন কি? মাদলের তাল, বাঁশীর সুর ও হাড়িয়ার মাদকতা সহযোগে নৃত্যগীত-উৎসবে মেতে আছে নারী পুরুষ সকলে – সাঁওতাল জীবনের এরূপ চিত্রায়নের সাথে শিল্প, সাহিত্য, ছায়াছবি প্রভৃতির মাধ্যমে আপনি হয়তবা পরিচিত হয়ে থাকবেন।
সাঁওতাল জনগোষ্ঠী পরিচিতি
সাঁওতালরা দেখতে কেমন, এ সম্পর্কেও হয়ত বিভিন্ন সূত্রে আপনার একটা পূর্ব-ধারণা থাকতে পারে। সব মিলিয়ে বাংলা অঞ্চলের প্রধান একটি আদিম জনগোষ্ঠী হিসাবে সাঁওতালদের সম্পর্কে বাঙালী জনমানসে বেশ কিছু বদ্ধমূল ধারণা রয়ে গেছে, যেগুলোর প্রধান দুটি দিক রয়েছে।
একদিকে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে সাঁওতালদের একটা রোমান্টিক প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে, যেখানে তারা হয়ে দাঁড়ায় আদিম সারল্যের প্রতিমূর্তি, এবং কখনোবা সুদূর অতীতে ফেলে আসা বাঙালীদের কোন পূর্বতন সত্তা বা ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছায়া; অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনে সাঁওতালদের অনেকে বাঙালীদের কাছে অচ্ছুৎ হিসাবেও গণ্য হয়ে এসেছে, যেমন উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে সাঁওতালদেরকে দোকানে চা খেতে দেওয়া হত না, এমন ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, যে প্রবণতা এখনো পুরোপুরি ঘুচে যায়নি।

সাধারণভাবে বলা চলে, সাঁওতালদের সম্পর্কে সংখ্যাগুরু বাঙালীদের অধিকাংশের ধারণা অস্পষ্ট, অনেকক্ষেত্রে কল্পনাশ্রয়ী, এবং সচরাচর অবজ্ঞাসূচক। একথা শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই সত্য তা নয়, বরং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বেলায়ও প্রযোজ্য, যেখানে অনেক বেশী সংখ্যায় সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে। (ভারতে সাঁওতালদের মোট সংখ্যা অর্ধকোটির মত হতে পারে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক সাঁওতালদের বসবাস। ছোট নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি হচ্ছে মূল সাঁওতাল-অধ্যুষিত এলাকা।
এছাড়া উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি ভারতীয় অঙ্গরাজ্যে, এবং নেপালেও সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে।) ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক সাঁওতাল রয়েছে, যাদের অধিকাংশ বাস করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় – যেমন, রাজশাহী, দিনাজপুর, নওগাঁ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি।
অবশ্য উত্তরবঙ্গে দৈহিক বৈশিষ্ট্যে সাঁওতালদের সাথে মিল রয়েছে, এমন অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরও (সংখ্যায় যারা ক্ষুদ্রতর) সাধারণভাবে সাঁওতাল বলেই মনে করা হয়। উত্তরবঙ্গের বাইরে সিলেটের চা বাগান এলাকায়ও সাঁওতালদের দেখা মেলে শ্রমিক হিসাবে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার মত দূরবর্তী স্থানেও সাঁওতাল পল্লীর অস্তিত্ব রয়েছে।
সরল ও আমোদপ্রিয় জনগোষ্ঠী হিসাবে সাঁওতালদের যে সাধারণ পরিচিতি রয়েছে, তার বাইরে এই উপমহাদেশের ইতিহাসে তাদের রয়েছে সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। অধিকন্তু বাংলা ভাষা তথা বাঙালী জনসমষ্টির আবির্ভাবের ইতিহাস তলিয়ে দেখলেও সাঁওতাল ও সম্পর্কিত অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে সুদূর অতীতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়। কাজেই নীচে আমরা সেসব ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব।
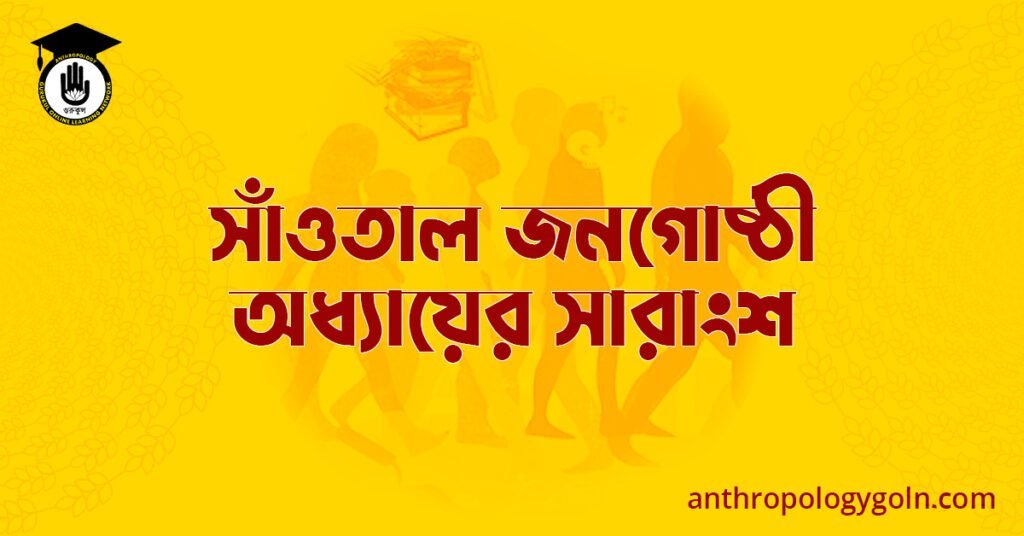
সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয় সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অধ্যায়ের সারাংশ – যা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এর অর্ন্তভুক্ত, সাঁওতালরা এ উপমহাদেশের অন্যতম একটি সংখ্যাবহুল আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশে যাদের একট ক্ষুদ্রাংশ মাত্র – সংখ্যায় দুই লক্ষাধিক – বসবাস করছে। বহু শতাব্দী ধরে জাতিগত বৈষম্য ও সামন্ত-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই সাঁওতালরা তাদের আত্মপরিচয় সমুন্নত রেখেছে।
অনেক গবেষকের মতে বাংলা ভাষা তথা বাঙালী জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতির উৎপত্তির ইতিহাসের সাথে সাঁওতালদের মত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পূর্বসূরীদের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষার ‘দেশী’ শব্দ ভান্ডার সেই সাক্ষ্যই দেয়। তবে সাধরাণভাবে বাঙালী ভদ্রলোকেরা তাদের জাত্যাভিমানের কারণে সাঁওতালদের সাথে তাদের এই ‘আত্মীয়তা’কে রোমান্টিকতা বা অবজ্ঞা-উপেক্ষার আড়ালেই লুকিয়ে রেখেছে।
অধিকন্তু ঐতিহাসিকভাবে তাদের অনেকে ‘ডিকু’র ভূমিকায় সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার আগ্রাসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে সাঁওতালরা নিজেরা এই আগ্রাসন বিনা বাধায় মেনে নেয় নি, বরং বিভিন্ন সময়ে তারা বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করেছে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের সাঁওতালরা অধিকাংশই দরিদ্র ও শিক্ষাবঞ্চিত হলেও বিভিন্নভাবে তারাও প্রতিকূল পরিবেশের খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করছে।
ভাষা ও সংস্কৃতি: সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বাঙালীদের সাথে যোগসূত্র
ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের শ্রেণীকরণ অনুসারে সাঁওতালদের ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের অন্তর্গত (Austro-Asiatic)। এই উপমহাদেশে এই ভাষা-পরিবারের দুটি শাখার প্রতিনিধি রয়েছে, একটি হল ‘মুন্ডা’ এবং অন্যটি হল ‘মন-খমের’ (Mon – Khmer)। মুন্ডা নামে একটি জনগোষ্ঠীও আছে, যাদের নামানুসারে প্রথমোক্ত শাখার নামকরণ করা হয়েছে, যদিও সংখ্যায় মুন্ডাদের চাইতে সাঁওতালরাই বেশী।
‘মুন্ডা’ ভাষাগোষ্ঠীর আওতায় সাঁওতাল ও মুন্ডা ছাড়াও কোল, হো, খেরওয়ারি, খারিয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষা পড়ে। (অন্যদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাইরে এই উপমহাদেশে মন-খমের শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি মাত্র ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে–খাসিয়াদের ভাষা)। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, বাংলা ভাষার বিকাশ ও প্রসারের আগে এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে মুন্ডা গোষ্ঠীর ভাষাসমূহই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল।
বাঙালী জনগোষ্ঠীর একটা প্রধান অংশই জাতিগতভাবেও সেই উৎস থেকেই এসেছে বলেও ধারণা করা হয়। কালক্রমে সেই মুন্ডা- ভাষীদের অনেকে ‘বাংলা’ ভাষী তথা বাঙালী হয়ে উঠলেও বাংলা ভাষা বা বাঙালী সংস্কৃতিতে অস্ট্রো- এশিয়াটিক বহু ছাপ এখনো রয়ে গেছে। যেমন, বাংলা ব্যাকরণের বইয়ে ‘দেশী’ হিসাবে যেসব শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশ মুন্ডা-গোষ্ঠীর শব্দ।
একইভাবে গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীদের পালিত জন্ম-বিবাহ প্রভৃতি সংক্রান্ত অনেক লোকজ আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসও একই উৎসজাত বলে নৃবিজ্ঞানীরা রায় দিয়েছেন। তবে বাঙালী ভদ্রলোকেরা বেশীরভাগই নিজেদেরকে আর্য (হিন্দুদের বেলায়) বা শেখ-সৈয়দ-মুগল-পাঠানদের (মুসলমানের ক্ষেত্রে) বংশধর হিসাবেই কল্পনা করে আসছেন। কাজেই সাঁওতালদের মত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সাথে ঘনিষ্ঠ উৎপত্তিগত বা সাংস্কৃতিক যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও সামষ্টিকভাবে সমকালীন বাঙালীরা সেই যোগসূত্রকে বিস্মৃতির গহ্বরেই ফেলে রেখেছে।
সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ ও সংগ্রামের ইতিহাস
নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও আপেক্ষিক স্বাধীনতা বজায় রেখে সাঁওতালদের মত আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা | অপেক্ষাকৃত দুর্গম এলাকাসমূহে বসতি স্থাপন করে আসলেও বিভিন্ন সময়ে অধিকতর শক্তিশালী | জনগোষ্ঠীদের আগ্রাসনের মোকাবেলা তাদের করতে হয়েছে।
এই আগ্রাসন নূতন মাত্রা ও তীব্রতা লাভ করে উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার | আওতায় যখন সাঁওতাল তথা অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা ব্যাপক হারে শোষণ-নিপীড়নের মুখে | পতিত হয়, তাদের অনেকে চেষ্টা করেছিল রুখে দাঁড়াতে।
এভাবে সংঘটিত হয়েছিল ১৮৫৫-৫৬ সালের ইতিহাস-খ্যাত ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’, যেখানে সিদু ও কানু, নামের দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতাল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েছিল। বিহারের ভাগলপুর থেকে বীরভূম পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ও তাদের সহায়ক দেশীয় জমিদার-মহাজনদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে।
শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, কিন্তু সাঁওতালদের প্রতিরোধকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় নি। বাঙালী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর যেসব সদস্যরা জমিদার-মহাজন বেশে সাঁওতাল-ভূমিতে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে সাঁওতালরা অভিহিত করত ‘ডিকু’ হিসাবে। এই ‘ডিকু’দের প্রতি সাঁওতালরা যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস ঐতিহাসিকভাবে লালন করেছে, সেটাকে দেখা যেতে পারে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের প্রতি তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসাবে।
বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ তথা অন্যান্য অঞ্চলে যেসব সাঁওতালরা এখন রয়েছে, তারা মূলতঃ এসব এলাকায় অভিবাসিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে। ঐতিহ্যগতভাবে শিকার ও কৃষি-নির্ভর সাঁওতালরা এদেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রথম জনবসতি গড়ে তুলেছিল। তবে এসব জায়গায়ও তারা সংখ্যাগুরুদের আগ্রাসন ও ক্ষমতাসীনদের শোষণ-নিপীড়ন থেকে রেহাই পায়নি।
১৯৪০-এর দশকে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে রাজশাহীর নাচোলে সংঘটিত ‘তেভাগা আন্দোলনে’ সাঁওতাল বর্গাচাষীরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই আন্দোলন ‘নাচোল বিপ্লব’ বা ‘রাজশাহীর / নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ’ নামেও পরিচিত। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জমির ফসলের ভাগাভাগিতে বর্গা-চাষীদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা। তবে রাষ্ট্রব্যবস্থা এগিয়ে এসেছিল জোতদারদের পক্ষে।
ফলে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা ব্যাপক নিপীড়নের শিকার হয়। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরাও এই আন্দোলনে সমর্থন-সহায়তা জোগালেও দমনমূলক ব্যবস্থা মূলতঃ সাঁওতালদের বিরুদ্ধেই গৃহীত হয়েছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ধরনের বৈষম্য, অন্যায় ও নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে এদেশের সাঁওতালরা এখনো মুক্ত হয় নি।
বাংলাদেশের সাঁওতালদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা
বাংলাদেশের সাঁওতালরা অধিকাংশই দরিদ্র এবং শিক্ষাবঞ্চিত। তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার সম্ভবতঃ ১০%-এর বেশী হবে না। তবে বিদ্যমান আর্থসামাজিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সাঁওতাল ও তাদের প্রতিবেশী অন্যান্য আদিবাসীরা তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত হচ্ছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।
যেমন, বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে ‘সাঁওতাল স্কুল’ পরিচালিত হচ্ছে, যে উদ্যোগের সাথে সাঁওতালরা নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অবশ্য মিশনারীদের থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের একাধিক রাজনৈতিক দল ও বেশ কিছু বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেও ‘ডিকু’দের প্রতি সাঁওতালদের ঐতিহ্যগত অবিশ্বাস কতটা ঘুচে গেছে, তা ততটা স্পষ্ট নয়।
নিজেদের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও এদেশের সাঁওতালরা যেসব বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা সম্ভবতঃ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে একাধিক দেশে ছড়িয়ে থাকা সমগ্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বেলায় কমবেশী প্রযোজ্য। যেমন, অর্থনৈতিকভাবে সাঁওতালরা এখন শিকারের উপর আদৌ বা তেমন নির্ভরশীল নয়, যদিও তীর-ধনুকের সাথে তাদের প্রতীকী সংশ্লিষ্টতা এখনো লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে গোত্র-সংগঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগা স্বাভাবিক, যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দুর্লভ।
প্রথাগতভাবে সাঁওতাল সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল, যে ব্যবস্থায় ‘মাঝি হাড়াম’ (গ্রাম-প্রধান) থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদ রয়েছে। এই ব্যবস্থা বর্তমানে কতটা কার্যকর রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠনের অন্য একটি দিক হচ্ছে গোত্র-সংগঠন। এদেশে সাঁওতালদের বারটি গোত্র রয়েছে বলে জানা যায়, যেগুলির মধ্যে রয়েছে কিন্তু, হাসদা, মুর্মু, হেমব্রম, মারান্ডি, টুডু, সরেন, বাস্কি প্রভৃতি। উল্লেখ্য, এই গোত্র-উপাধিগুলোকে সাঁওতালদের নামের অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অবশ্য অবস্থাপন্ন সাঁওতালদের অনেকে বাঙালী হিন্দুদের পদবী তথা আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছে, এমন তথ্য পাওয়া যায়।
অন্যদিকে সাঁওতালদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খ্রিস্টান ধৰ্মও গ্রহণ করেছে, যদিও এক্ষেত্রে সাঁওতাল পদবী ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। বলা বাহুল্য, নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কতটা কিভাবে তারা ধরে রাখবে, বাইরের কতটুকু কি তারা গ্রহণ বা বর্জন করবে, এসব বিষয়ে ভেবে চিন্তে সাঁওতালরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে।
তারা সরল বা অজ্ঞ, এ ধরনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বাইরের কেউ যদি অভিভাবকসুলভ ভঙ্গীতে তাদের উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায়, তবে এমন ব্যক্তি হয়ত ‘ডিকু’র মতই আচরণ করবে। এ প্রসঙ্গে একটা কথাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, অন্যান্য সকল জনগোষ্ঠীর মতই বাংলাদেশের সাঁওতালরাও পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বের সাথে খাপ খাইয়েই চলার চেষ্টা করবে। কাজেই “সাঁওতাল’ জনগোষ্ঠীর কথা শুনলেই স্থির-অনড় কিছু গতানুগতিক চিত্র যদি কারো মানসপটে ভেসে ওঠে, সেগুলো অবশ্যই ঝেড়ে ফেলা দরকার।