আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সফিস্টবিদ্যার সাথে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শনের সম্পর্ক
সফিস্টবিদ্যার সাথে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শনের সম্পর্ক

সফিস্টবিদ্যার সাথে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শনের সম্পর্ক
প্রোটাগোরাস থেকে আইসোক্রেটিস পর্যন্ত সকল সফিস্টকে যদি তাদের অন্য সব পরিচয় বাদ দিয়ে মূলত শিক্ষকরূপে গণ্য করা হয়, তাহলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, সফিস্টদের ক্রিয়াকলাপ ও কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষাদানের তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে উন্নত করার ক্ষেত্রে কোনো অবদান রেখেছে কি না। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচের শতকের শুরুতে প্রতিটি অবস্থাপন্ন ও বুদ্ধিমান গ্রীক তরুণ পড়ালেখা, সঙ্গীত এবং শরীরচর্চার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত।
তদুপরি গ্রীক উপনিবেশসমূহে, বিশেষত ইটালি প্রভৃতি পশ্চিম অঞ্চলের উপনিবেশগুলোতে, দর্শন এবং শিল্পচর্চা উচ্চশিক্ষার অভাব পূরণ করত। যেমন, ইটালিতে পিথাগোরাসের সম্প্রদায়ের শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রকৃত পক্ষে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল। আর সিসিলিতে কোরাক্স এবং টিসিয়াসের যে বক্তৃতাদানবিদ্যা শিক্ষা দিতেন সেটাও শিক্ষামূলকই ছিল। কিন্তু মধ্যগ্রীসে (এবং এথেন্সে) গ্রীক-পারসিক যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় এবং বৈদেশিক রাজনীতি নিয়েই নাগরিকরা সর্বদা ব্যস্ত থাকত।
আত্মশিক্ষার কোনো সময়ও তাদের হাতে থাকত না, আর উচ্চশিক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করত না। কিন্তু গ্রীক-পারসিক যুদ্ধে গ্রীকরা পারসিকদের পরাজিত করার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। এরপর থেকে গ্রীসের সেরা শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের আগমন ঘটল এথেন্সে এবং এ সকল বিদ্যার একত্রীকরণ ও বিকাশ ঘটার সাথে সাথে এথেন্সে এ বিষয়ে শিক্ষালাভের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।
আমরা আগেই দেখেছি, ঠিক এ সময়েই আবার গ্রীসে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে দর্শন ও শিল্পচর্চার বিলোপ ঘটেছিল। ফলে সাহিত্যবিষয়ক সফিস্টরা এ সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কারণ, তাঁরা এমন ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রদান করতেন, যা দর্শন বা শিল্পবিষয়ক ছিলনা। সফিস্টরা যে ঐ মুহূর্তে গ্রীসের জনগণের শিক্ষার ঐ চাহিদা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এবং তা পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এটা তাঁদের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।
প্রোটাগোরাসের আবির্ভাবের আগে গ্রীসের উপনিবেশসমূহে বা মধ্যগ্রীসে উচ্চশিক্ষা বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু প্রোটাগোরাসের পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবেই সফিস্টদের বক্তৃতাকক্ষে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। এ থেকে বোঝা যাবে যে সফিস্টদের আন্দোলন সফল হয়েছিল। এ ছাড়াও সফিস্টদের পক্ষে আরো কিছু বলার আছে। সংস্কৃতিবিষয়ক সফিস্টরা যে, শিক্ষা প্রদান করতেন তার অনেক ইতিবাচক গুণ ছিল।
প্রোটাগোরাস তাঁর পাঠক্রমের মধ্যে ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, কবিতার ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতাদানবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং বিরামহীনভাবে ব্যাখ্যা এবং আলোচনা দ্বারা এবং ছাত্রদের সাথে তর্কবিতর্কের মাধ্যমে ঐ পাঠক্রমকে প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর ঐ ব্যাপক পাঠক্রমকে প্রোডিকাস এবং অন্যান্যরা আরো সম্প্রসারিত করেছিলেন।
অনুমান করা যেতে পারে যে, এঁদের প্রবর্তিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর গুণেই এথেনীয় নাগরিকরা ক্রমে বহুমুখী গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, যে বহুমুখী কর্মক্ষমতাকে এথেনীয়দের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য বক্তৃতাদানবিদ্যা, রাজনীতি এবং বিতর্কবিষয়ক সফিস্টদের সম্পর্কে এত উচ্চ প্রশংসামূলক কথা বলা চলে না। এঁরা এক একজন এক একটি সীমিত শাখায় নিবদ্ধ হবার ফলে শিক্ষক না হয়ে প্রশিক্ষকে পরিণত হন।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে বক্তৃতাদানবিদ্যা এবং বিতর্কবিদ্যা শিক্ষাদানের একটা প্রধান হাতিয়ার। অবশ্য, এ ধরনের সফিস্টরা সীমিত শাখায় নিবদ্ধ হয়ে পড়লেও, ছাত্ররা এক শাখার সফিস্টের নিকট শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর অন্য শাখার সফিস্টের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এতে মনে হয়, সফিস্টবিদ্যার পতনের যুগেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ছিল। তবে এ কথা সম্ভবত মেনে নেয়া যায় যে, এক শতাব্দীকালের মধ্যে সফিস্টরা সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষাদানের সবগুলো পদ্ধতি আবিষ্কার ও ব্যবহার করেছিলেন।
এ সকল গুণ সত্ত্বেও সাধারণ সফিস্টবিদ্যার একটা প্রধান ত্রুটি ছিল সত্যের প্রতি উদাসীনতা। আয়োনীয় যুগের দর্শন তথা প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে সফিস্টরা সন্দেহবাদীতে পরিণত হন। ফলে সব ধরনের সফিস্টরাই বিষয়বস্তুর পরিবর্তে রচনাশৈলী, সঠিক বস্তুর পরিবর্তে বাস্তব ফললাভ, প্রমাণ দানের বদলে বিশ্বাস উৎপাদন ইত্যাদি পদ্ধতির প্রতি মনোনিবেশ করেন।
সংক্ষেপে বললে, বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতে গিয়ে সফিস্টরা সাহিত্যক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের বিরোধিতা করেন। সফিস্ট বিদ্যার এ ত্রুটি যে একটি গুরুতর ত্রুটি, তা যে-সকল নাগরিকরা সফিস্টদের সম্মান করতেন তাঁরাও অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সফিস্টদের এ ত্রুটি যে মারাত্মক রকম ক্ষতিকর, তা সক্রেটিস বুঝতে পেরেছিলেন।
সফিস্টবিদ্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পর্যায়ে সত্যকে এবং সত্যানুসন্ধানকে অবজ্ঞা করা হত— এবং এটাই ছিল সক্রেটিসের আপত্তির মূল কারণ। সফিস্টদের সম্পর্কে এ সমালোচনাকে বর্তমানকালের পণ্ডিতরা সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। সাহিত্য এবং বাগ্মিতার (বক্তৃতাদান বিদ্যা) ক্ষেত্রে সফিস্টদের অবদান নিতান্ত অল্প নয়। পেশাগত সাফল্য অর্জনের জন্যে তাদেরকে বাধ্য হয়েই উচ্চমানের রচনাশৈলী আয়ত্ত করতে হত।
এ যুগের প্রধান সফিস্টরা তাঁদের কালের উপযোগী রচনাশৈলীর প্রবর্তনও করেন। সফিস্টবিদ্যার সূত্রপাত ঘটার আগে মধ্যগ্রীসে বা এথেন্সে গদ্যরচনার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। সাহিত্যবিষয়ক সফিস্টরাই উত্তম গদ্যরচনা এবং উত্তম বক্তৃতাদানের গুরুত্ব শিক্ষা দেন।
পণ্ডিতদের মতে, সফিস্টরা উচ্চমানের রচনাশৈলীসম্পন্ন গদ্যরচনা এবং উৎকৃষ্ট মানের বক্তৃতাদানের কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন বলেই প্লেটোর পক্ষে ‘রিপাবলিক’ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থরচনা সম্ভব হয়েছিল এবং ডেমোস্থেনিস-এর মতো বাগ্মীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। সফিস্ট তত্ত্বের সাথে দর্শনের সম্পর্ক বরাবরই ছির সুস্পষ্ট বিরোধিতার সম্পর্ক। প্রোটাগোরাস থেকে আইসোক্রেটিস পর্যন্ত সব সফিস্টই ছিলেন সন্দেহবাদী।
প্রোটাগোরাস, গর্গিয়াস প্রভৃতি প্রথম যুগের সফিস্টরা তাঁদের পূর্ববর্তী দার্শনিকদের রচনা পাঠ করেছিলেন ঐ দর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। দর্শনশাস্ত্রকে উ খাত করে সফিস্টরা যখন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সর্বশক্তির অধিকারী হলেন, ‘জ্ঞান কি?” এ প্রশ্নটি তখন অনেক দিনের জন্যে সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। আসলে ‘সফিস্ট জ্ঞানতত্ত্ব’ বলে কিছু নেই কারণ সফিস্টরা জ্ঞানতত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।
অনুরূপভাবে, ‘সফিস্ট নীতিশাস্ত্র’ বলেও কিছু নেই। বস্তুত, সফিস্টরা নীতিশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতেন না বা এ বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন না। এমন ঘটে থাকতে পারে যে বাস্তবতার চেয়ে কৃত্রিমতা এবং সত্যের চেয়ে সাফল্যের প্রতি সফিস্টদের পক্ষপাতিত্ব থাকার ফলে ঐ যুগের নৈতিকতার ওপর সফিস্টরা একটা কুপ্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন।
কিন্তু একথা ঠিক যে সফিস্টদের কোনো সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতিশাস্ত্র ছিল না এবং কোনো সফিস্ট নীতিশাস্ত্র বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেন এমন ধারণা করার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। সফিস্টদের সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে, সফিস্টদের সাথে সক্রেটিসের মিল এবং পার্থক্যের বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। সফিস্টদের মতো সক্রেটিসও ছিলেন দর্শনশাস্ত্র এবং শিল্পকলার বিরোধী এবং এ বিষয়ে প্রোটাগোরাসের সাথে তাঁর মিল ছিল।
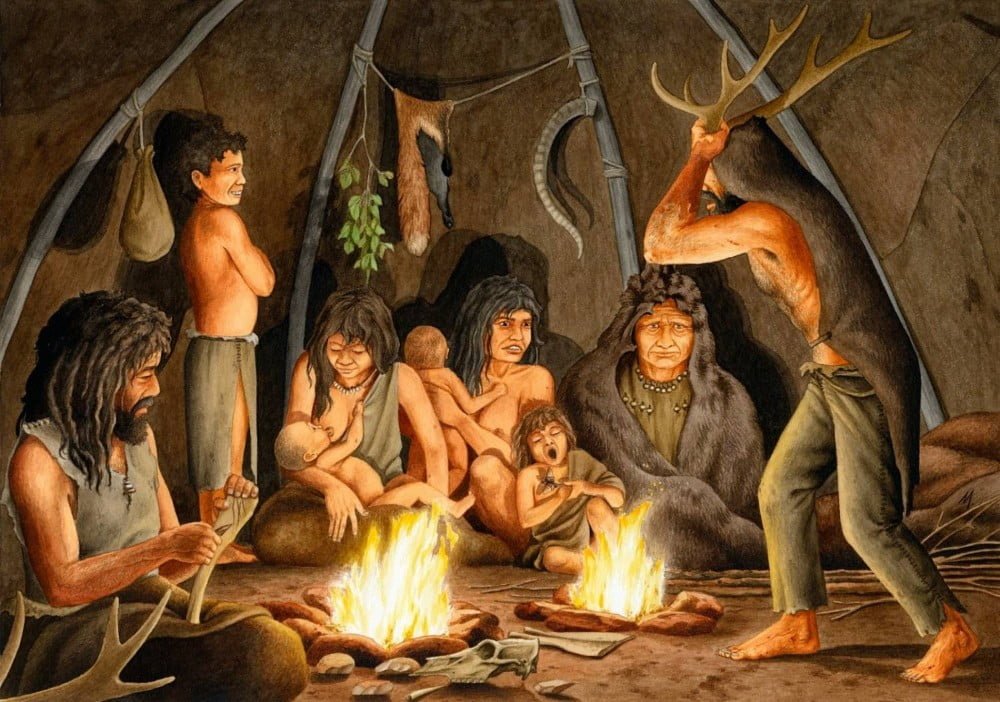
সক্রেটিস সৎগুণ ও উৎকর্ষ অর্জনকে বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধানের বিকল্পরূপে গণ্য করেছিলেন এবং বিতর্কের মাধ্যমে সৎগুণ ও উৎকর্ষ লাভ করা যায়, একথা বিশ্বাস করতেন। এ হিসেবে সংস্কৃতিবিষয়ক ও বিতর্কবিষয়ক সফিস্টদের সাথে তাঁর মিল ছিল। সক্রেটিসের সমকালীন লোকেরা তাঁকে সফিস্ট বলে মনেও করত। কিন্তু, সফিস্টরা যেক্ষেত্রে বিতর্কে জয়লাভের উদ্দেশ্যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতো, সক্রেটিস সেক্ষেত্রে সত্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেন।
তাই যখন গ্রীসে দর্শনচর্চার হ্রাস ঘটেছিল, তখন সক্রেটিসকে অদ্ভুত ধরনের সফিস্ট হিসাবেই গণ্য করা হত। কালক্রমে যখন আবার দর্শনচর্চার পুনরুথান ঘটল, তখন সক্রেটিস দার্শনিকরূপেই গণ্য হতে শুরু করলেন।
আরও দেখুন :
