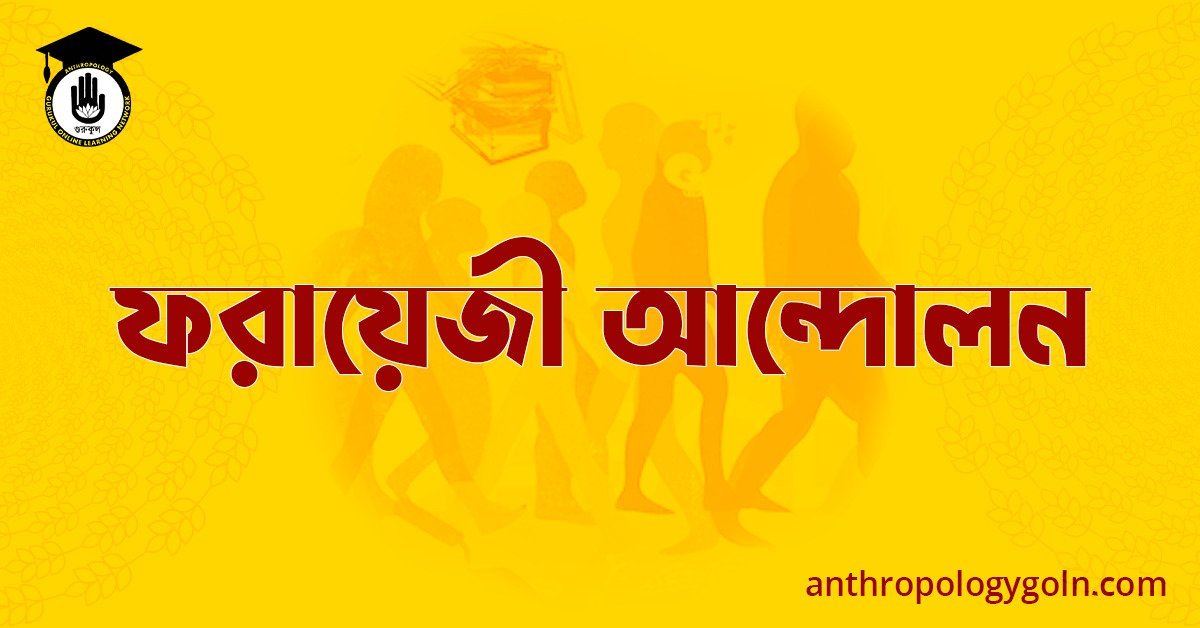বাংলার উনিশ শতকের ইতিহাসে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের উত্থান ঘটে। এর মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, যা কেবল ধর্মীয় সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এর সাথে যুক্ত হয়েছিল কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষোভ, জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী চেতনা। ফলে ফরায়েজী আন্দোলন কেবল ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনই নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার কৃষকসমাজের আত্মপ্রকাশেরও একটি দৃষ্টান্ত।
ফরায়েজী আন্দোলন
আন্দোলনের সূচনা ও প্রভাব
হাজী শরিয়তউল্লাহ (১৭৮১–১৮৪০) ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হজ্জ পালনকালে আরব দেশে গিয়ে সমসাময়িক ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। ফিরে এসে তিনি বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নানা অনৈসলামিক আচার, লোকাচার, সুফি দরগাহকেন্দ্রিক অতিরঞ্জিত ভক্তি ও হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবে আসা বিভিন্ন প্রথা বর্জনের আহ্বান জানান।
“ফরায়েজী” নামকরণের কারণও এখানেই নিহিত—ইসলামে যে ফরজ বা মৌলিক কর্তব্যসমূহ (যেমন নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ) পালন করা বাধ্যতামূলক, সেগুলোই কেবল অনুসরণের জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন।
হাজী শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুদু মিঞা আন্দোলনের নেতৃত্ব নেন। দুদু মিঞার সময়ে আন্দোলন ফরিদপুর থেকে ছড়িয়ে পড়ে বাখেরখঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, নোয়াখালী, এমনকি ত্রিপুরার মতো অঞ্চলেও।
ধর্মীয় লক্ষ্য ও সংস্কার
ফরায়েজী আন্দোলনের মূল ধর্মীয় লক্ষ্য ছিল:
কোরআন ও হাদিস-ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার,
অনৈসলামিক ও হিন্দু প্রভাবিত আচার-অনুষ্ঠানের বর্জন,
দরগা ও পীরপন্থার অতিরঞ্জন প্রতিরোধ,
মসজিদকেন্দ্রিক ধর্মচর্চার পুনর্জাগরণ।
এভাবে ফরায়েজীরা মুসলমান সমাজকে একধরনের ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন।
সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য
যদিও আন্দোলনের শুরুটা ধর্মীয় সংস্কার হিসেবে, তবে দ্রুতই এর সাথে মিশে যায় তৎকালীন কৃষকসমাজের দুঃখ-দুর্দশার প্রশ্ন।
বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু, যারা মুসলমান কৃষকদের উপর শোষণ চালাত।
ইউরোপীয় নীলকররাও কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করত।
ভূমি রাজস্ব ও কর আদায়ের চাপ কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল।
এই প্রেক্ষাপটে দুদু মিঞা কৃষকদের সংগঠিত করে ঘোষণা করেন যে “সকল মানুষ সমান”। ফরায়েজীরা অন্যায় খাজনা দিতে অস্বীকার করে, জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ফলে আন্দোলনটি শ্রেণীসংগ্রামের চরিত্র অর্জন করে।
রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ঔপনিবেশিক বিরোধিতা
ফরায়েজী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এর রাজনৈতিক প্রতিধ্বনি।
জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থকেও চ্যালেঞ্জ করেছিল।
অনেক ক্ষেত্রে ফরায়েজীরা স্থানীয় প্রশাসনের সাথেও সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল।
ফরায়েজী আন্দোলনের কারণে বাংলার কৃষকসমাজ প্রথমবারের মতো একটি সমবেত রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর পায়।
ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে বিদ্রোহ হিসেবে দেখত, ফলে ফরায়েজীদের উপর বহুবার দমন-পীড়ন চালানো হয়। তবুও আন্দোলন চলতে থাকে এবং বাংলার মুসলিম কৃষকদের মধ্যে আত্মপরিচয় ও প্রতিবাদী চেতনা গড়ে তোলে।
আন্দোলনের উত্তরাধিকার
ফরায়েজী আন্দোলন উনিশ শতকের বাংলায় শুধু ধর্মীয় শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা ছিল না, বরং এটি সামাজিক সমতা, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের ভিত্তিও স্থাপন করেছিল।
এটি বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও পরবর্তী সময়ের জমিদারবিরোধী আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক পূর্বসূরি।
মুসলিম কৃষক সমাজের আত্মপরিচয় গঠনে এবং তাদের মধ্যে সংগ্রামী মানসিকতা সৃষ্টিতে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি গঠনে ফরায়েজী আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।
ফরায়েজী আন্দোলন ছিল এক বহুমাত্রিক আন্দোলন—যা ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধকে একত্র করেছিল। হাজী শরিয়তউল্লাহ ও দুদু মিঞার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এ আন্দোলন বাংলার মুসলিম কৃষক সমাজকে নতুন চেতনা ও আত্মপরিচয় দিয়েছিল। তাই ইতিহাসে ফরায়েজী আন্দোলন শুধু ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ঘটনা নয়, বরং এটি ছিল বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণের এক অনন্য অধ্যায়।