ব্রোঞ্জযুগের নগর সভ্যতার একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হল লেখন পদ্ধতি ও লিপির আবিষ্কার। নগর সভ্যতার উদয়ের পর মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মন্দির ও রাজবাড়িতে এত প্রভূত সম্পদ জড়ো হয়েছিল যে, তার হিসাব রাখার একটা ব্যবস্থা না করলেই চলছিল না। শুধু তো সম্পদের হিসাব রাখা নয়, ব্যবসায়ী বা অন্যান্য মানুষকে যেসব জিনিস ঋণ, সাহায্য বা অগ্রিম হিসাবে দেয়া হত, তা ফিরে পাবার জন্যে শুধু স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে থাকা নগর সভ্যতায় সম্ভব ছিল না।
নগর সভ্যতার লেখন ও লিপি
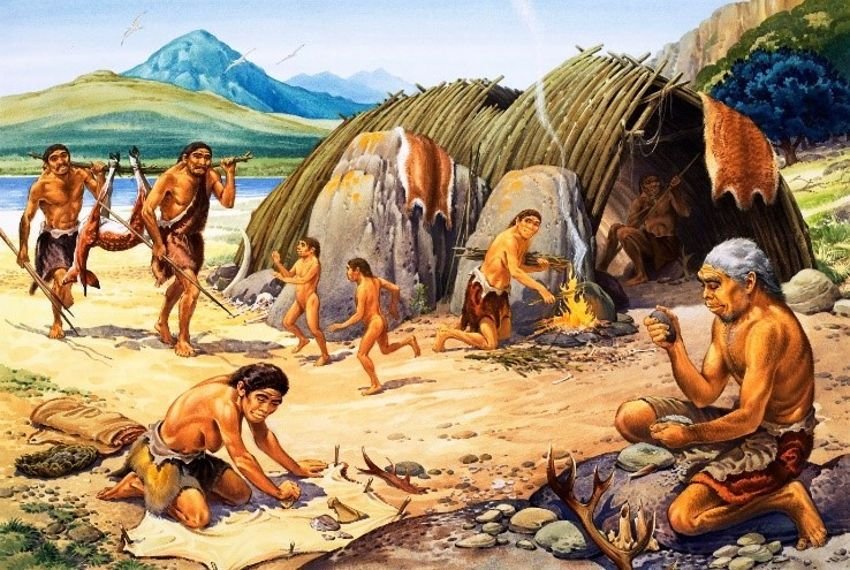
প্রথম প্রথম ছবির সাহায্যে এ সব হিসাব রাখা হত। যেমন পাঁচটা ভেড়ার ছবি বা ভেড়ার মাথা আঁকলে বোঝানো যেত যে পাঁচটা ভেড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এটাকে ঠিক লিপি বলা চলে না। এটা হল আসলে স্মৃতি-সহায়ক লিপি। ছবির সাহায্যে শুধুমাত্র কোনো কোনো ভাব প্রকাশ করে চলে, তাই এটাকে বলা হয় ভাবব্যঞ্জক লিপি বা চিত্রলিপি।
আমরা যে পদ্ধতিতে লিখি তাকে বলা হয় ‘ধ্বনিলিপি’। ধ্বনিলিপিতে এক এক রকম চিহ্ন দিয়ে এক এক রকম ধ্বনি বোঝান হয়। ফলে, কথা বলার সময় আমরা যে রকম শব্দ উচ্চারণ করি, ধ্বনিলিপিগুলো পড়ে গেলেও সে রকম শব্দ উৎপন্ন হয়। কারণ তাতে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণমালা আছে। ইংরেজি ফরাসি জার্মান প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ লিখিত ভাষাই বর্ণমালাভিত্তিক। কিন্তু এটা ধ্বনিলিপির সবচেয়ে উন্নত পর্যায়। বর্ণমালা ছাড়াও ধ্বনিলিপি সম্ভব।
তাদের বলা হয় ‘শব্দাংশ’ (ওহফফটঠফণ) বা অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপি। যেমন, দাঁড়কাক লিখতে আমরা যদি একটা দাঁড় এবং একটা কাকের ছবি বসিয়ে দিই এবং পরপর পড়ে যাই দাঁড়কাক তাহলে এটা হবে অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির একটা দৃষ্টান্ত। বাস্তবেও এভাবেই চিত্রলিপি থেকে প্রথমে অক্ষরলিপি এবং তারপরে ক্রমশ বর্ণমালার আবিষ্কার হয়েছিল।
ব্রোঞ্জযুগে মেসোপটেমিয়ার সুমের অঞ্চলে এবং মিশরে প্রায় একই সময়ে (আজ থেকে পাঁচ ছ’হাজার বছর আগে) অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির প্রচলন হয়েছিল। মিশরের লিপিকে বলা হয় ‘হায়ারোগ্লিফ’ (Hieroglyph); এর অর্থ ‘পবিত্র লিপি’। সুমের ও পরবর্তিকালে ব্যবিলনিয়ার লিপিকে বলা হয় ‘কিউনিফর্ম’। ব্যবিলনিয়ার নরম মাটির চাকতির উপর সরু কাঠি দিয়ে লিখে চাকতিগুলোকে পুড়িয়ে শক্ত করা হত। লেখাগুলো তাই দেখতে হত কীলকের মতো।
তাই এ লেখাগুলোর নাম দেয়া হয়েছে ‘কীলকলিপি’ বা কিউনিফর্ম(Cuneiform)। এ দু’ ধরনের লিপিরই যে চিত্রলিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে। তা লিপিগুলোর ক্রমবিবর্তন দেখলেই বোঝা যায়। মিশরের হায়ারোগ্লিফ লিপিতে পাখি, মানুষ, চাবুক, আঙুল ইত্যাদির ছবি অপরিবর্তিত আকারেই রয়ে গেছে। কিন্তু দেখতে ছবি হলেও এগুলো আসলে ধ্বনির প্রতীক, পাখি বা মানুষ ইত্যাদির প্রতীক নয়। যেমন ইংরেজি ‘বী’ (ঈণণ) শব্দের অর্থ মৌমাছি।
এ শব্দটি যদি প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় হত তবে তারা হায়ারোগ্লিফ লিপিতে মৌমাছির ছবি দিয়ে ‘বী’ ধ্বনিটিকে বোঝাত, মৌমাছিকে নয়। সুমেরীয় ভাষা থেকে দৃষ্টান্ত নিলে আমরা দেখব, এ ভাষায় ‘টি’ শব্দটির অর্থ ছিল দুটো তীর এবং জীবন। এখন, তীরের চিহ্ন আঁকা যত সহজ, জীবনের প্রতীক আঁকা তত সহজ নয়। কিউনিফর্ম লিপি যখন চিত্রিলিপি থেকে অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপিতে রূপান্তরিত হয় তখন তীরের ছবি এঁকে জীবনকে বোঝান চলত।
কারণ, তীরের ছবি এখন আর তীরের প্রতীক নয়, ‘টি’ ধ্বনিটির প্রতীক এবং ‘টি’ শব্দের অর্থ জীবনও হতে পারে। ব্রোঞ্জযুগের নগর সভ্যতা লেখন পদ্ধতি ও লিপি ছাড়া অচল হত। ব্রোঞ্জ যুগের বিভিন্ন নগর সভ্যতায় অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির প্রচলন দেখা যায়। আবার, ব্রোঞ্জযুগের সামাজিক অবস্থাও লেখন পদ্ধতির আবিষ্কারের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি থাকলেই যে একটা জটিল আবিষ্কার সহজ হতে পারে এমন নয়।
অর্থাৎ এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, প্রাচীন কালে যত জায়গায় ব্রোঞ্জযুগের নগর সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সব জায়গাতেই লেখন পদ্ধতি ও লিপির আবিষ্কার নতুন করে পৃথক পৃথক ভাবে ঘটতে পারত। কারণ, লেখন পদ্ধতির মতো জটিল একটা বিষয় আবিষ্কৃত হবার জন্যে অনুকূল পরিবেশ ছাড়াও আরো অনেক জটিল শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক। যেমন, লেখন পদ্ধতির আবিষ্কারের জন্যে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও কতগুলো শর্ত পূরণ হওয়ার দরকার ছিল।

প্রাচীনকালে প্রচলিত সব ভাষাই লেখন পদ্ধতির জন্ম দেবার অনুকূল ছিল না। পুরাতত্ত্ববিদ স্যার লেনার্ড উলি ‘হিস্ট্রি অব ম্যানকাইণ্ড’ গ্রন্থে পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে সুন্দর ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সুমের অঞ্চলেই প্রথম লেখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিল। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, সুমেরীয় ভাষা লেখন ও লিপির উদ্ভবের অনুকূল ছিল। সুমেরীয় ভাষার মূল শব্দ অধিকাংশই ছিল এক বা দুই সিলেবিশিষ্ট।
ফলে ঐ সব শব্দের চিত্ররূপসমূহকে পাশাপাশি স্থাপন করলে এবং পর পর পড়ে গেলে নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে, ঠিক যেভাবে পর পর ধ্বনি উচ্চারণ করলে শব্দ উচ্চারিত হয়। এ সকল বিবেচনা থেকে লেনার্ড উলি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতেই প্রথম লেখন পদ্ধতি ও ধ্বনি লিপির উদ্ভব হয়েছিল। আমরা মনে করি, পরে সেখান থেকে তা’ মিশরে, চীনে, মহেঞ্জদাড়োতে বিস্তার লাভ করেছে।
এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, মিশর, চীন, বা মহেঞ্জদাড়ো ঐ লেখন পদ্ধতি গ্রহণ করার সময় নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষা ও চিত্রলিপির সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন ধ্বনিলিপির সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই মেসোপটেমিয়ার লিপির সাথে মিশর, মহেঞ্জদাড়ো বা চীনের প্রাচীন লিপির যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এখানে বলা দরকার, কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে লেখন পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে আবিষ্কৃত হয়ে থাকতে পারে।
আবার, অন্যান্য অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, শুধু লেখন পদ্ধতিই নয়, ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা ও সমাজ কাঠামো প্রথম সুমেরে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সেখান থেকে মিশরে তার বিস্তার ঘটেছে। মিশর ও মেসোপটেমিয়া থেকে আবার তার বিস্তার ঘটেছে মহেঞ্জদড়ো, চীন প্রভৃতি স্থানে। এ অভিমতকে অবহেলা করা চলে না।
ব্রোঞ্জযুগের বিভিন্ন জটিল যন্ত্রপাতি ও কারিগরি আবিষ্কার এবং সমাজ সংগঠন মিশর, ব্যবিলনিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন প্রভৃতি স্থানে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে বারবার আবিষ্কৃত হয়েছিল এ কথা মেনে নেয়া সত্যিই কঠিন। তার চেয়ে সহজ হল এ কথা মেনে নেয়া যে, একস্থানে এ সভ্যতা । সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হবার পর তার অনুকরণে অন্যান্য স্থানে ব্রোঞ্জযুগের এ সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল।
অবশ্য, মনে রাখা দরকার যে, প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার অনুকরণে মিশবে, বা মিশর-মেসোপটেমিয়ার অনুকরণে ভারতীয় উপমহাদেশ ও চীনে এ সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটলেও তারপর থেকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে এসব অঞ্চলে সভ্যতা স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ লাভ করেছিল। এ কারণে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে সূক্ষ্ম বিষয়ে কিছু কিছু অমিলও দেখা যায়।
মেসোপটেমিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন প্রভৃতির প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা কালে আমরা এ সকল প্রাচীন সভ্যতার পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাব সম্পর্কে আরো আলোচনা করব। চিত্রলিপি থেকে প্রথম যে ধ্বনিলিপির উদ্ভব হয়েছিল, তা ছিল শব্দাংশ বা অক্ষরভিত্তিক (Syllable) । লেখন পদ্ধতির বিকাশে পরবর্তী ধাপ হল বর্ণমালাভিত্তিক ধ্বনিলিপি। অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপিতে এক একটা লেখনচিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে এক একটা শব্দাংশ বোঝান হয়।
আর বর্ণমালা ভিত্তিক লেখন পদ্ধতিতে এক একটা বর্ণ দিয়ে এক একটা বিশুদ্ধ ধ্বনি বোঝান হয়। যেমন, বাংলাভাষা হল বর্ণমালাভিত্তিক, তাই ক, খ, চ প্রভৃতি দিয়ে মুখে উচ্চারিত এক একটা বিশেষ ধ্বনিকে মাত্র বোঝানো হয়। বর্ণমালাভিত্তিক লিপি অবশ্যই আগেকার অক্ষরভিত্তিক লেখন পদ্ধতি থেকে উন্নত।

প্রাচীন মিশরীয়দের, হায়ারোগ্লিফিক লিপির নমুনা। ছবিতে বিভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রতীক দেখা যাচ্ছে।
কারণ পঁচিশ তিরিশটা বর্ণ শিখে নিলেই সহজে ছোট ছেলেমেয়েরাও যে কোনো বই পড়তে পারে। অপর পক্ষে, অক্ষরলিপিতে একটা চিহ্ন দিয়ে একটা শব্দাংশ বোঝানো হয় বলে এতে অনেক বেশি চিহ্ন লিখতে হয়। অক্ষরভিত্তিক লিপিতে অনেক ক্ষেত্রেই শত শত বা হাজার হাজার চিহ্ন শিখতে হয় লেখাপড়া জানার জন্যে; কারণ, এক একটা চিহ্ন সেখানে এক একটা পৃথক শব্দ বা শব্দাংশের জন্যে ব্যবহার করা হয়।
প্রাচীন মিশরের ছাত্রদের তাই পড়তে শিখতেই দশ পনেরো বছর সময় লাগত। মিশর ব্যবিলনে তাই লেখাপড়া শেখানোর কাজটা পুরোহিততন্ত্রের কুক্ষিগত থাকতে পেরেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে তা খুব বেশি প্রসার লাভ করতে পারেনি। বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতি শেখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ হলেও খুব সহজে এর আবিষ্কার ঘটেনি।
আমরা পরে দেখব যে বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতি আবিষ্কারের অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতির উদয় ঘটেছিল অনেক পরে— লৌহযুগে। ব্রোঞ্জযুগের সমাজ কাঠামোর পরিসরে বর্ণমালার আবিষ্কারের সুযোগ ছিল না। ব্রোঞ্জ যুগে সর্বত্র কেবল অক্ষরলিপিরই প্রসার ঘটেছে। অবশ্য সে যুগে এ লিপিই যথেষ্ট যুগান্তকারী ও বিপ্লবাত্মক ছিল।
