আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় দর্শন ও ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প
দর্শন ও ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প
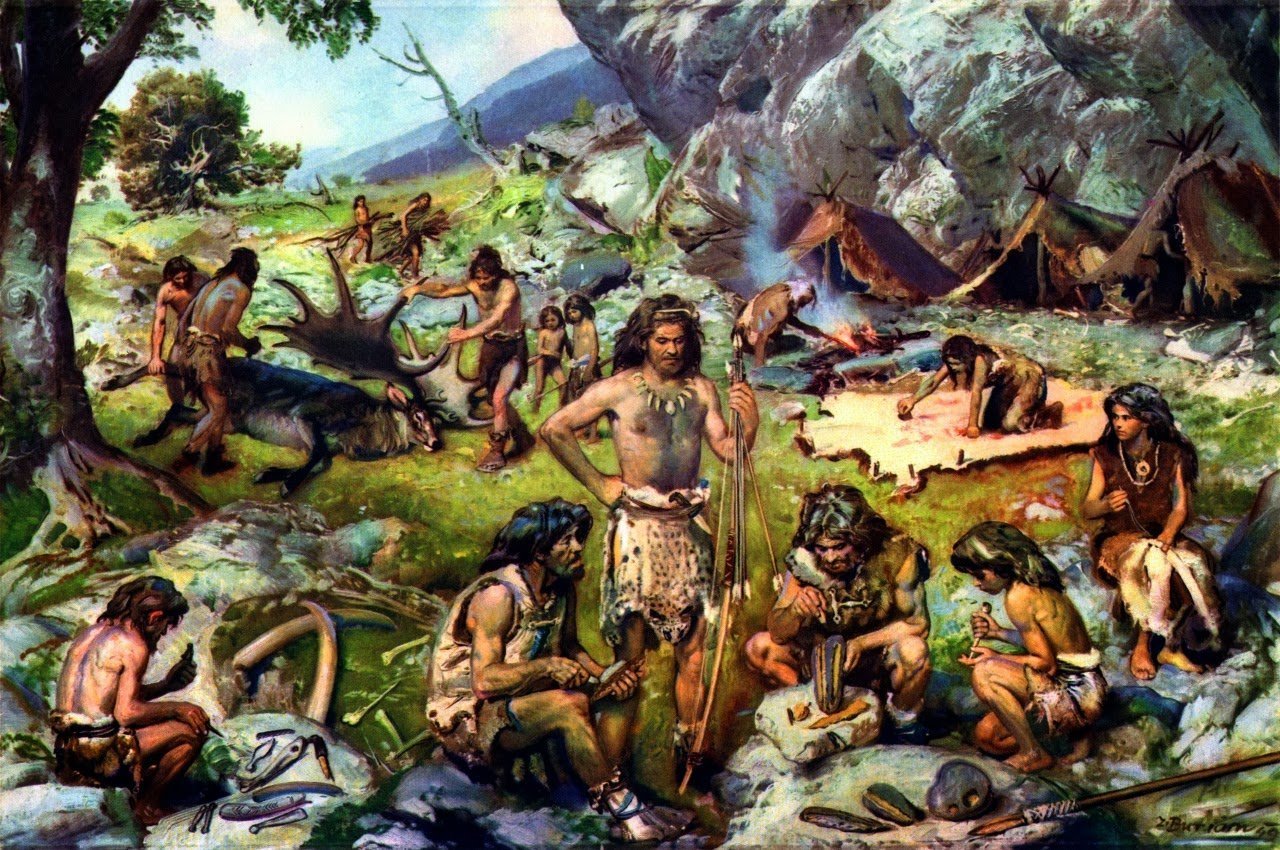
দর্শন ও ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প
হেলেনিস্টিক যুগে দর্শনের দুটো সুস্পষ্ট ধারার প্রকাশ ঘটেছিল। মূল ধারায় ছিল স্টোয়িকবাদ ও এপিকিউরাসবাদ। এ দুটোই ছিল গ্রীক দর্শন। আর অপ্রধান ধারায় সমাবেশ ঘটেছিল বিভিন্ন প্রাচ্য ধর্মবিশ্বাসের। এপিকিউরাসবাদের প্রবর্তক ছিরেন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩২৪-২৭০ খৃঃ পূঃ) আর স্টোয়িকবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গ্রীক দার্শনিক জেনো (আনুমানিক ৩০০ খ্রিঃ পুঃ)। উভয় দর্শনেরই উদ্ভব ঘটেছিল ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকেঃ এ দুই দর্শনের মধ্যে কিছু কিছু মিল ছিল।
উভয় দর্শনেরই লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির কল্যাণসাধন। উভয় দর্শনই ছিল বস্তুবাদী এবং আত্মিক পদার্থে অবিশ্বাসী। দুই দর্শনেই কিছু কিছু বিশ্বজনীনতার উপাদান ছিল। যেমন উভয় দর্শনই জগতের সব মানুষকে অভিন্ন বলে মনে করত এবং বলত যে গ্রীক ও বর্বর মানুষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ দুই দর্শনের মধ্যে অনেক বিষয়ে অমিলও আছে।
জেনোর মত ছিল এই যে, এ বিশ্বজগৎ মূলত সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে এতে মাঝে মাঝে যে অসঙ্গতি দেখা দেয় তার সমাধানের মধ্য দিয়েই পরম মঙ্গল লাভ করা যায়। স্টোয়িকবাদ অনুসারে, শান্ত মনের মধ্যেই পরম মঙ্গল নিহিত আছে। তাই তারা আত্মশাসন ও কর্তব্যপালনকে পরম সদগুণ বলে বিবেচনা করত। এপিকিউরাসবাদীরা মনে করত যে, আনন্দলাভের মধ্যেই পরম মঙ্গল নিহিত আছে। তবে লাম্পট্য বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে তারা আনন্দ বলে মনে করত না।
ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিকে তারা প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলজনক মনে করত বটে; তবে মানসিক আনন্দ ও সদ্বিবেচনার আনন্দকেই তারা প্রকৃত আনন্দ বলে মনে করত। এপিকিউরাস ডেমোক্রিটাস-এর পরমাণু তত্ত্ব অংশত গ্রহণ করেছিলেন। হেলেনিস্টিক দর্শনের অপর ধারা তথা যুক্তিবিরোধী ধারাটি চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে— ফিলো জুডিয়াস এবং নব পিথাগোরীয়দের দর্শনে। এ দুই দর্শনের মধ্যে মূল বিষয়ে যথেষ্ট মিল ছিল।
উভয় দর্শনই এক অজ্ঞেয় ও অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। উভয় মতের অনুসারীরাই মনে করত যে, এ জগৎ আত্মা এবং বস্তু এ দুই সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত। তারা মনে করত যে, বস্তু দ্বারা গঠিত সবকিছুই অমঙ্গলজনক এবং মানুষের আত্মা তার দেহে বন্দী হয়ে আছে।
এদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিবাদবিরোধী। তারা মনে করত বিজ্ঞান বা যুক্তি থেকে সত্যকে জানা যায় না, ঈশ্বরের কাছ থেকে অতিপ্রাকৃত উপায়ে সত্যকে লাভ করা যায়। ফিলো মনে করতেন যে, পুরাতন টেস্টামেন্টকে ঐশ্বরিকসূত্রে পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যে সমস্ত সত্য নিহিত রয়েছে। ফিলো এবং নব পিথাগোরীয়গণ উভয় সম্প্রদায়ই খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের বিকাশে অবদান রেখেছিল ।
বিশুদ্ধ গ্রীক সংস্কৃতি এবং হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির পার্থক্য বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে ধর্মের ক্ষেত্রে। হেলেনিস্টিক যুগে বুদ্ধিজীবীরা গ্রীক নাগরিকদের সাধারণ ধর্মের পরিবর্তে স্টয়িকবাদ, এপিকিউরাসবাদ প্রভৃতিকে গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মকে গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে প্রাচীন মিশরীয় দেবী আইসিসের পূজা প্রসার লাভ করে। তারপর আবার ক্যালডীয়দের জ্যোতিষীয় ধর্মও প্রসার লাভ করে।

এর ফলে স্বভাবতই জ্যোতিষচর্চা অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায়। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব পড়েছিল জরথুস্ত্রবাদের বিভিন্ন শাখার, বিশেষত মিথ্রাবাদের। এ যুগের মানুষ ইহজীবনের অসারতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে পরকালে সুখ-সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। এ যুগে মানুষ হতাশাবাদী, অতীন্দ্রিয়বাদী এবং অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছিল। হেলেনিস্টিক যুগের ধর্মবিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইহুদীদেরও কিছু অবদান ছিল।
প্রথমে আলেকজান্ডার ও পরে রোমকরা প্যালেস্টাইন জয় করে নেয়ায় ইহুদীরা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরা অবশ্য স্বভাবতই গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এ ইহুদীদের মাধ্যমেই আবার প্রাচ্য ধর্মবিশ্বাস গ্রীক জগতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। আলেকজান্দ্রীয় বা হেলেনিস্টিক সাহিত্যের গুরুত্ব শুধু এ কারণে যে, তার মাধ্যমে ঐ সভ্যতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ রচনাতেই কোনো মৌলিকতা বা চিন্তার গভীরতার ছাপ ছিল না।
কিন্তু নকলনবিসদের হাত থেকে এত ব্যাপক সংখ্যায় এ সব বই বের হত যে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। এগার শতাধিক লেখকের নাম এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিবছর আরও হচ্ছে। এ সব পুস্তকের অধিকাংশই ছিল নিকৃষ্ট রচনা, তবে কয়েকটি রচনা সত্যই উৎকৃষ্ট ছিল।
হেলেনিস্টিক কাব্যের প্রধান রূপ ছিল নাটক ও দৃশ্যকাব্য। আর হেলেনিস্টিক নাটক ছিল প্রধানত মিলনান্তক। এ যুগের প্রধান নাট্যকার ছিলেন মিনাণ্ডার।
গদ্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক, জীবনীকার এবং কল্প-কাহিনীকারদেরই প্রাধান্য ছিল। এ যুগে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন পলিবিয়াস। তিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও সত্যানুসন্ধানের দিক থেকে বিচার করলে প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে একমাত্র পলিবিয়াসকেই থকিডাইডিসের সাথে তুলনা করা চলে। হেলেনিস্টিক শিল্প আগের যুগের গ্রীক শিল্পের সব মহৎ গুণকে বজায় রাখতে পারেনি।
গ্রীক স্বর্ণযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে যে মানবতাবাদ, সামঞ্জস্য ও সংযমের প্রকাশ ঘটেছিল, হেলেনিস্টিক যুগে তার স্থলে মাত্রাতিরিক্ত বাস্তবতা, রোমাঞ্চ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রকাশ ঘটে। হেলেনিক যুগের সরল গাম্ভীর্যপূর্ণ মন্দিরের পরিবর্তে হেলেনিস্টিক যুগে উদিত হয়েছিল বিলাসময় প্রাসাদ, ব্যয়বহুল অট্টালিকা, সুবিশাল সার্বজনীন ভবন এবং শক্তি ও বৈভবের প্রতীকস্বরূপ বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ।
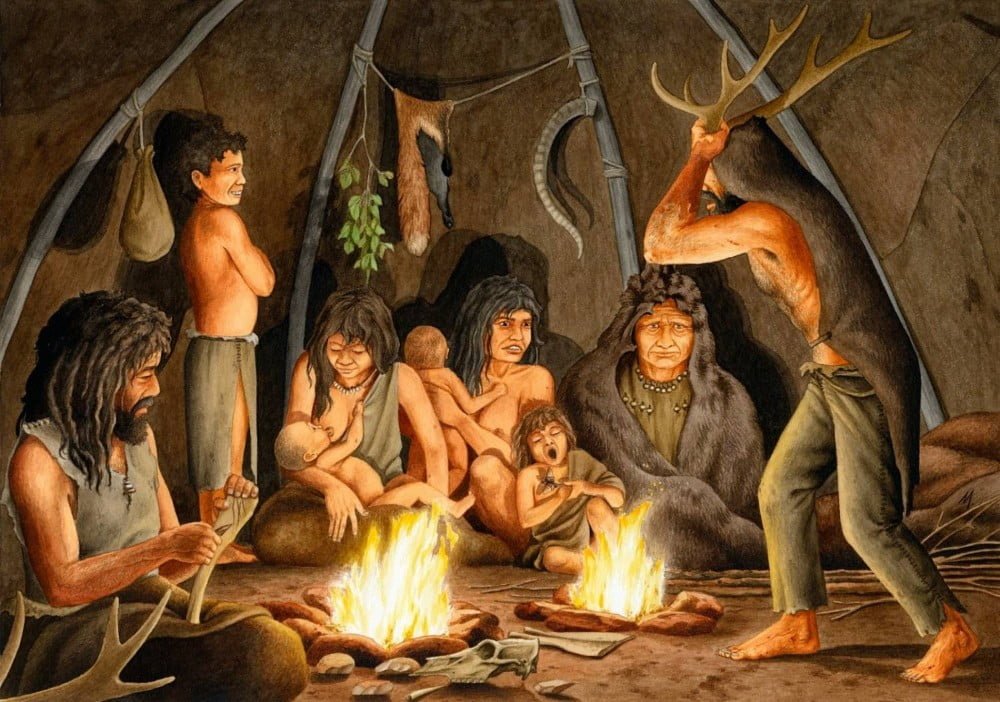
হেলেনিস্টিক যুগের স্থাপত্যকর্মের একটা সুন্দর নিদর্শন হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ। সমুদ্র দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজসমূহের পথনির্দেশের জন্য এ আলোকস্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল। ত্রিতলবিশিষ্ট এ বিশাল ভবনটির উচ্চতা ছিল ৪০০ ফুট। হেলেনিস্টিক যুগের ভাস্কর্যে যদিও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও রোমাঞ্চের প্রকাশ ঘটেছিল, তার ব্যতিক্রমও আছে। ভেনাস ডি মিলো নামে পরিচিত আফ্রোডিটির মূর্তিটি এ যুগের একটি সার্থক সৃষ্টি।
আরও দেখুন :
