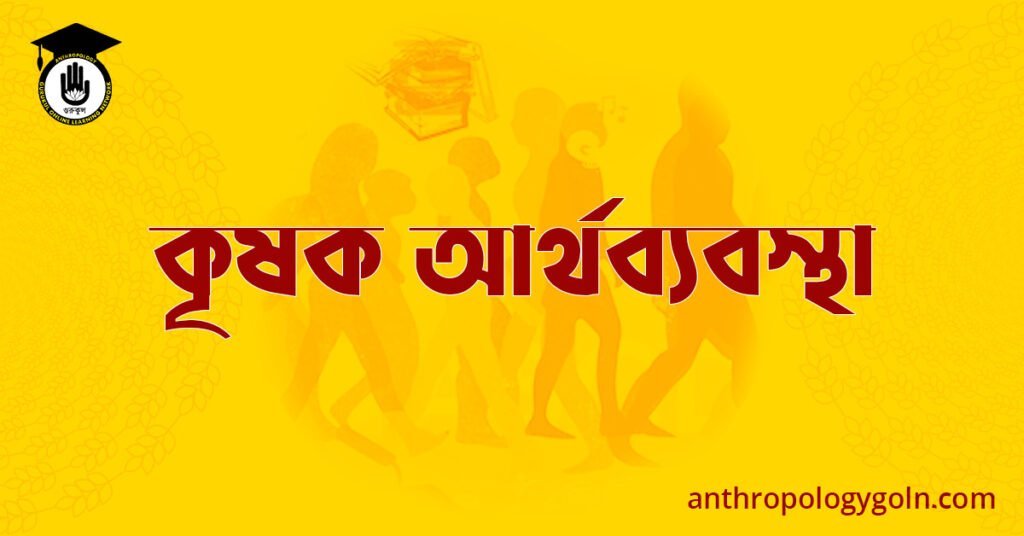আজকে আমরা আলোচনা করবো কৃষক আর্থব্যবস্থা নিয়ে। নৃবিজ্ঞানে দীর্ঘকাল ধরে কৃষক আর্থব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা চলেছে। আসলে বলা উচিৎ বিতর্ক চলেছে। বিতর্কটার প্রধান জায়গা হচ্ছে কৃষক আর্থব্যবস্থা আসলেই স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থা কিনা। অনেকেই মনে করেছেন কৃষকদের মধ্যে একেবারেই বিশিষ্ট ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং চর্চা অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে একেবারেই আলাদা। ফলে তাঁদের আর্থনীতিক কর্মকান্ডকে একটা স্বতন্ত্র আর্থব্যবস্থা বলা প্রয়োজন। আবার অন্য দল শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়েছেন কৃষক আর্থব্যবস্থাকে একটা স্বতন্ত্র আর্থব্যবস্থা বলা যায় না।
বিশেষভাবে বর্তমান কালে সারা পৃথিবীর কৃষক বর্গএকটা সাধারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এমন নয় যে তাঁদের মধ্যে অবস্থার কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু একটা অভিন্ন বাস্তবতা হচ্ছে পুঁজিবাদ। বর্তমান পৃথিবীর সকল অঞ্চলের কৃষকরাই কোন না কোন ভাবে এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। ফলে আর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী বা বাজার আর্থব্যবস্থা বলা প্রয়োজন।
কৃষক আর্থব্যবস্থা
এই বিতর্কটির একটি প্রেক্ষাপট আছে। আপনারা আগেই দেখেছেন: নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই প্রযুক্তি এবং পরিবেশের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কখনো কখনো এর নাম খাদ্য সংগ্রহ কৌশল । এখানে নৃবিজ্ঞানীদের একটা ধারণা কাজ করেছে, তা হচ্ছে কোন একটা ব্যবস্থা অন্য ব্যবস্থার চেয়ে প্রাচীন এবং প্রযুক্তির দিক থেকে নিকৃষ্ট। মোটামুটি ব্যাপারটা এরকম:
শিকারী-সংগ্রহকারী —> পশুপালন –> উদ্যানকৃষি – –> নিবিড় কৃষি –> শিল্প
দেখা গেছে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা পৃথিবীতে একটা লম্বা সময় ধরে প্রচলিত আছে। বর্তমান শিল্প ভিত্তিক উৎপাদনের যুগেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ প্রথমত, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একটা অন্যতম উৎস কৃষি। দ্বিতীয়ত, মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস এখনও কৃষি। ফলে তৃতীয় গুরুত্ব নতুন করে নৃবিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে।
আরেকটি প্রেক্ষাপট রয়েছে এই বিতর্কের। এই শতকে, বিশেষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে কৃষক বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই সময়কালে তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলোতে কৃষিক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য প্রাথমিকভাবে নৃবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদদের বিস্মিত করেছে। এই বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।
একদিকে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে এবং বাজারের মুনাফার আশায় শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কৃষির বিশাল বিশাল খামার গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই প্রবণতাটি আরও আগে থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিল্পভিত্তিক সমাজে। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের বহু সমাজে কৃষিক্ষেত্র তখনও ক্ষুদ্রাকার আছে। অনেক চাষীই কোন রকমে নিজেদের জমিতে বছরের খোরাকী উৎপাদনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্যকে বুঝবার জন্য অনেক নৃবিজ্ঞানী একে বিশেষ সমাজের প্রথা কিংবা রীতি-নীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে বিষয়টা এত সহজ-সরল নয়। যাই হোক, তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলোতে চলমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কৃষকদের এই বৈশিষ্ট্যকে অনেকেরই বেমানান মনে হয়েছে।
ফলে কৃষকদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে একটা স্বতন্ত্র আর্থব্যবস্থা ভাববার এটাও একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে । যাঁরা মনে করেন কৃষক আর্থব্যবস্থা স্বতন্ত্র তাঁরা অনেকেই আর্থব্যবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন। সেগুলি হচ্ছে: আদিম বা “উপজাতীয়” আর্থব্যবস্থা (primitive/tribal economy), কৃষক আর্থব্যবস্থা (peasant economy) এবং আধুনিক বা শিল্প আর্থব্যবস্থা (modern/industrial economy)। কৃষক আর্থব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়নের সুস্পষ্ট নজির থাকলেও নৃবিজ্ঞানের শুরুর দিকে কৃষকদের একটা মধ্যকালীন দশা হিসেবে দেখা হ’ত।
পরবর্তী কালে এই চিন্তা আর সমর্থন লাভ করেনি। অনেক তাত্ত্বিক কৃষক বলতে কেবলই ভূমি নির্ভর কৃষিকাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যেরা আবার মনে করেছেন মৎস্যজীবী কিংবা গ্রামীণ কারিগরদেরও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা প্রয়োজন। একটা ব্যাপারে অনেকেই একমত যে, কৃষক সমাজ আর শহুরে সমাজের মধ্যে একটা ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। কৃষক সমাজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এই ধারণাকে কেন্দ্র করে অনেকেই এগিয়েছেন |
কৃষক আর্থব্যবস্থা অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয় কৃষক আর্থব্যবস্থা অধ্যায়ের সারাংশ – যা কৃষক আর্থব্যবস্থা এর অর্ন্তভুক্ত, নৃবিজ্ঞানে এবং অন্যান্য সামাজিক- বিজ্ঞানে কৃষক -আর্থব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের চর্চাকারীদের অনেকেই মনে করেন কৃষকদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্বতন্ত্র।
কিন্তু অন্যান্য নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, অপরাপর প্রক্রিয়া থেকে কেবলমাত্র কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করে পাঠ করা সম্ভব নয়। বিশেষভাবে, বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে কৃষকদের অস্তিত্ব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত – যেমন, রাষ্ট্র। সামাজিক ইতিহাসে যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্প শক্তিশালী হবার পেছনে গরিব বিশ্বের কৃষির বিরাট ভূমিকা।
সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে কৃষি বিষয়ক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বোঝা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষজন মূলত ভুমিহীন এবং মজুর শ্রেণীর। নিঃস্ব হবার কারণে এর বড় অংশই খুচরা শ্রমিকের কাজ পাবার আশায় শহরে পাড়ি দিচ্ছেন।
আরও দেখুনঃ