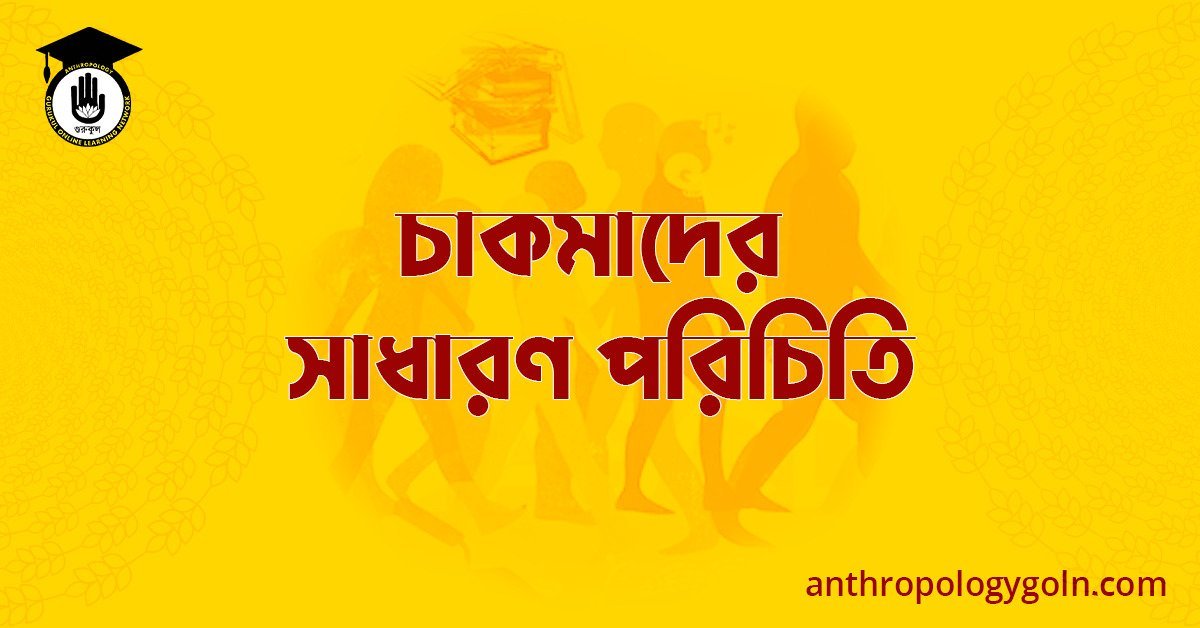আজকের আলোচনা চাকমাদের সাধারণ পরিচিতি নিয়ে। সাধারণভাবে ‘পাহাড়ী’ নামে পরিচিত যে ১১টি জাতিসত্তা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে চাকমারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সবচাইতে সুপরিচিত। অবশ্য আগেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষিতে নয়, গোটা বাংলাদেশেই চাকমারা হল বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায়।
চাকমাদের সাধারণ পরিচিতি
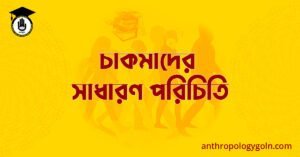
তবে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে নয়, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের তুলনায় এগিয়ে থাকার কারণে চাকমাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে কর্মসূত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে, এবং বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনেক চাকমা ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে, ফলে দেশে তাদের একটা সাধারণ পরিচিতি গড়ে উঠেছে।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্ত্ব শাসনের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের সূত্রে আন্তর্জাতিকভাবেও চাকমারা বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছে, যেহেতু পাহাড়ীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসাবে চাকমারাই এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল।
১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এদেশে চাকমা জনসংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষাধিক। তবে সেসময় ভারতে আশ্রিত শরণার্থীরা যারা পরে দেশে ফিরে এসেছে তাদের হিসাব ও স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির | মত বিষয় বিবেচনায় ধরলে এ সংখ্যা বর্তমানে আরো বেশী হবে। চাকমা জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের বসবাস রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলায়, এবং এরপর খাগড়াছড়িতে। বান্দরবান জেলায় চাকমাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। বর্তমানে বাংলাদেশের বাইরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশে অনেক চাকমা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, যাদের বড় অংশই কাপ্তাই বাঁধের ফলে স্থানচ্যুতিসহ বিভিন্ন কারণে পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলে অভিবাসিত হয়েছিল।
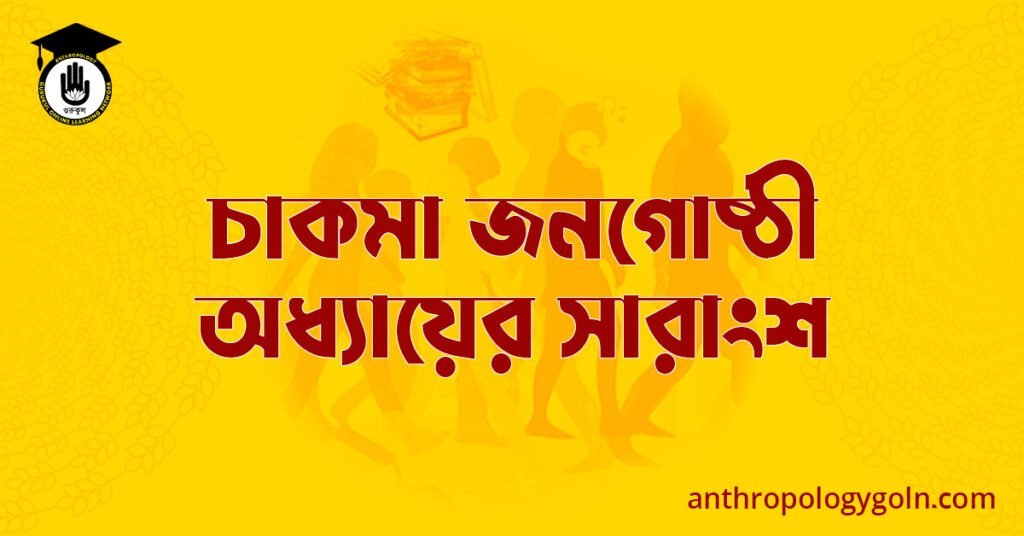
চাকমা জনগোষ্ঠী অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয় চাকমা জনগোষ্ঠী অধ্যায়ের সারাংশ – যা চাকমা জনগোষ্ঠী এর অর্ন্তভুক্ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত চাকমারা বাংলাদেশের বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায়, যারা শিক্ষাদীক্ষায়ও বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশেও চাকমাদের বসবাস রয়েছে, যাদের অনেকে কাপ্তাই বাঁধের ফলে স্থানচ্যুত হয়ে অভিবাসী হয়েছিল।
মুগল শাসনামল বা আরো আগে থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমাদের বসবাস ছিল, যেখানে কিংবদন্তী অনুসারে ‘চম্পকনগর’ নামক একটি স্থান থেকে তাদের আগমন ঘটেছিল। ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে অন্যান্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীদের মত চাকমারাও অর্থনৈতিকভাবে মূলতঃ জুমচাষের উপরই নির্ভর করত।
তবে ব্রিটিশ শাসনামলে চাকমাদের অনেকে লাঙল চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যাদের একটা বড় অংশ কাপ্তাই বাঁধের ফলে স্থানচ্যুত হয়েছিল। চাকমাদের বেশীরভাগ এখন আর জুমচাষ না করলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকমাদের সংস্কৃতি চেতনায় জুমিয়া ঐতিহ্যের গুরুত্ব রয়েছে। অন্য যে কোন সংস্কৃতির মত চাকমা সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন ঐতিহ্যের সমন্বয় লক্ষ্যণীয়।
চাকমা সমাজে বিভিন্ন গোত্র থাকলেও বর্তমানে গোত্র পরিচয়ের চাইতে শ্রেণীগত অবস্থানই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর বর্তমান চাকমা সমাজে ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থান নিরূপণে সামন্ত বা ঔপনিবেশিক আমলের বংশমর্যাদার চাইতে শিক্ষা, পেশা, বিত্ত ইত্যাদির গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।
চাকমাদের ইতিহাস
চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে কয়েক শতাব্দী আগের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত ও | বস্তুনিষ্ঠ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য শুধু চাকমাদের বেলাতেই নয়, অন্যান্য প্রায় সকল আদিবাসী জাতিসত্তা, এমন কি খোদ বাঙালী জাতির ক্ষেত্রেই কথাটা অনেকখানি প্রযোজ্য। কারণ, প্রথাগত ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন রাজা-বাদশা বা অন্যান্য সামন্তপ্রভুদের কর্মকান্ডের প্রতি যতটা মনোযোগ দেখা গেছে, সে তুলনায় সামগ্রিকভাবে একটা জাতিসত্তা কিভাবে গঠিত হয়, এর বিকাশ বা ঐতিহাসিক রূপান্তর কিভাবে ঘটে, এ ধরনের বিষয়ে তেমন গবেষণা হয় নি।
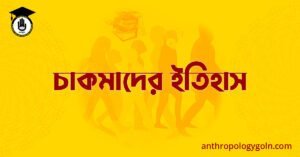
তার উপর একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসাবে অপরাপর আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের মতই চাকমারাও এদেশের মূলধারার ইতিহাস চর্চায় অনেকটাই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। চাকমাদের সম্পর্কে যেসব ঐতিহাসিক তথ্য আমরা পাই, তার অনেকটা মূলতঃ লিপিবদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের হাতে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে শিক্ষিত চাকমাদের একটা অংশও নিজেদের ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন, যাঁরা এই জাতির অতীত সম্পর্কে অজানা বা স্বল্প-জানা অনেক তথ্য, ধারণা বা তত্ত্ব হাজির করছেন, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসের সাথে কিংবদন্তী ও কল্পনার ভেদরেখা স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। যাহোক, নীচে বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে চাকমা জাতির ইতিহাসের কিছু সাধারণ দিকের উপর আলোকপাত করা হল।
ঠিক কবে থেকে ‘চাকমা’ পরিচয়ধারী একটি জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায় না, তবে মুগল শাসনামলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিশ্চিতভাবেই চাকমাদের বসবাস ছিল, এবং সেখানে তাদের আবির্ভাব আরো আগেই ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে চাকমাদের আদি বাসস্থান ছিল ‘চম্পকনগর’ নামক একটি স্থান, তবে এর সত্যতা বা সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। চাকমাদের একাধিক পালাগানে বিজয়গিরি নামে এক রাজার যুদ্ধাভিযান, বিশেষ করে তাতে অংশগ্রহণকারী সেনাপতি রাধামন ও তার প্রেমিকা ধনপুদির কাহিনী বিবৃত রয়েছে।
রাজা বিজয়গিরিকে চাকমা রাজাদের একজন আদিপুরুষ হিসাবে গণ্য করা হয়, তবে কিংবদন্তীর এই চরিত্র ও ঘটনাবলীর পেছনে কবেকার কোন্ ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে, তাও এখনো নিঃসংশয়ভাবে নিরূপিত হয় নি। অতীতে চাকমা রাজারা নিজেদের ‘শাক্য-বংশীয়’ (যে বংশে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল) হিসাবে দাবী করতেন, তবে এই দাবীর সামাজিক ও প্রতীকী তাৎপর্য থাকলেও তার পেছনে কোন বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে, এমন প্রমাণ নেই।
চট্টগ্রামে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যে দুইটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ছিল, আরাকান ও ত্রিপুরা, তাদের উত্থান পতনের সাথে চাকমা জাতির ইতিহাস অনেকটা সম্পর্কিত ছিল বলে মনে করা হয়। চাকমাদের একটা বড় অংশ একসময় আরাকান রাজ্যের প্রভাবাধীন চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল বাস করত বলে মনে হয়, তবে তার আগে তারা সেখানে উত্তর দিক থেকে গিয়ে থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানেও আরাকানে ‘দৈংনাক’ নামে অভিহিত একটি জনগোষ্ঠী রয়েছে বলে জানা যায় যেটাকে তঞ্চঙ্গ্যা তথা চাকমাদের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়।
(উল্লেখ্য, তঞ্চঙ্গ্যারা বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র উপজাতি হিসাবে বিবেচিত হলেও তারা চাকমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।) যাই হোক, ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে অর্থাৎ মোগল শাসনামলে চাকমাদের মূল আবাস ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে। চাকমা রাজারা মোগল শাসকদের ‘কার্পাস কর’ দিত, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তাদের অনেকে অভিজাত মুসলিম শাসকদের অনুকরণে “খাঁ’ পদবী সম্বলিত নাম ব্যবহার করতেন – যেমন, জন্মাল খাঁ, জান বক্স খাঁ প্রভৃতি। ‘রাজা’ হিসাবে অভিহিত হলেও তাঁরা অবশ্য পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলে মনে হয় না, তবে চাকমা জনগোষ্ঠীর উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল এবং কখনো কখনো চাকমা রাজারা মোগল ও পরবর্তীতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।
১৮৬০ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টির পর সেখানে যে তিনটি ‘সার্কেল’ চিহ্নিত করা হয়, তার একটি ছিল ‘চাকমা সার্কেল’ (যার সীমানায় বর্তমান রাঙ্গামাটি জেলার বেশীর ভাগ এলাকা এবং খাগড়াছড়ি জেলার কিয়দংশ অবস্থিত)। মূলতঃ চাকমা-অধ্যুষিত এই সার্কেলের চীফ পদটি স্বাভাবিকভাবেই চাকমা রাজ পরিবারের জন্য নির্ধারিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের গোড়াতে চন্দ্রঘোনা ছিল জেলা সদর, তবে ১৮৬৮ সালে তা রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত হয়, যে পদক্ষেপ চাকমা জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। রাজপরিবার সহ চাকমা জনগোষ্ঠীর মূল কেন্দ্র ছিল রাঙ্গামাটি, যেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ঐতিহাসিকভাবে চাকমা সমাজে সাক্ষরতা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে অন্যান্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীদের মত চাকমারাও অর্থনৈতিকভাবে মূলতঃ জুমচাষের উপরই নির্ভর করত। তবে ব্রিটিশরা বিভিন্ন পন্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষের পরিধি কমিয়ে তার পরিবর্তে লাঙল চাষের প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যে পরিবর্তনে চাকমা জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শামিল হয়েছিল।
বিশেষ করে রাঙ্গামাটিসহ কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা বরাবর বেশ কিছু সমৃদ্ধ চাকমা জনপদ গড়ে উঠেছিল। তবে ১৯৬০-এর দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে এই জনপদসমূহের অধিকাংশ হ্রদের নীচে তলিয়ে যায়, এবং এতে প্রায় এক লক্ষের মত যেসব মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছিল, তাদের অধিকাংশ ছিল চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত। সেসময় স্থানচ্যুত চাকমাদের অনেকে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন অংশসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়, এবং বাকীরা স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে যারা ভারতীয় কতৃপক্ষ কর্তৃক অরুণাচল প্রদেশে পুনর্বাসিত হয়েছিল, তারা এখনো সেদেশের পূর্ণ নাগরিকত্ব পায়নি।
১৯৯৭ সালে ‘শান্তি চুক্তি’ সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি নামক একটি সংগঠনের নেতৃত্বে পাহাড়ীরা স্বাধিকারের দাবীতে দুই দশকের বেশী সময় ধরে যে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়েছিল, অনেক বিশ্লেষকের মতে তার একটি অন্যতম উৎস নিহিত রয়েছে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ঘটনায়। এই বাঁধের ফলে ব্যাপক স্থানচ্যুতির অভিজ্ঞতাসহ পাহাড়ীদের চোখে তাদেরকে নিজভূমে পরবাসী করার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ তাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। পাহাড়ীদের মধ্যে এই শ্রেণীর বিকাশ সবচাইতে বেশী ঘটেছিল চাকমাদের মধ্যে, ফলে তাদের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে পাহাড়ীদের পরবর্তীকালের আন্দোলনের মূল স্রোত।
চাকমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি
পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে ভাষাগত দিক থেকে চাকমারা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই অর্থে যে, অন্য সকল গোষ্ঠীর ভাষাসমুহ “তিব্বতী-বর্মী’ (Tibeto- Burman ) | পরিবারভুক্ত হলেও চাকমা ভাষা বাংলার মতই ‘ভারতীয়-ইউরোপীয়’ (Indo-European) ভাষা পরিবারের অন্তর্গত (একথা অবশ্য তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যার সাথে চাকমা ভাষার বড় কোন | পার্থক্য নেই)। চাকমা ভাষার সাথে চট্টগ্রামী বাংলার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে চাকমা ভাষাকে বাংলার | একটি উপভাষা হিসাবে বিবেচনা না করে একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবেই গণ্য করা হয়।
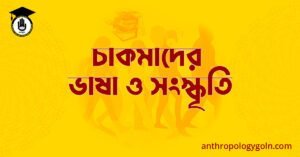
ধারণা করা হয়, একসময় চাকমাদের পূর্বসূরীদের ভাষাও তিব্বতী-বর্মী পরিবারভুক্ত ছিল, তবে কয়েক শতাব্দী আগে যে প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রামী বাংলার বিকাশ ঘটেছিল, সেই একই প্রক্রিয়ায় সমান্তরালভাবে চাকমা ভাষারও | আবির্ভাব ঘটে থাকতে পারে। ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে চাকমা ভাষার একটা | লিখিত রূপ প্রচলিত ছিল, যে কাজে ব্যবহৃত হরফ বর্মী বর্ণমালার অনুরূপ। বর্তমানে এই চাকমা বর্ণমালার কার্যকর কোন ব্যবহার নেই, যদিও চাকমা সমাজে অনেকে এটিকে নূতন করে চালু করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন।
এমনিতে চাকমা ভাষায় যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁরা মূলতঃ বাংলা হরফই ব্যবহার করেন। এখন পর্যন্ত চাকমা বা অন্য কোন পাহাড়ী ভাষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্কুলে শেখানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি, তবে অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে।
চাকমা লোক-সংস্কৃতির অনেক উপাদানে জুমচাষ-নির্ভর জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য চাকমাদের খুব কম অংশই (এক চতুর্থাংশের নীচে) জুমচাষের উপর নির্ভর করে। তথাপি শহুরে শিক্ষিত চাকমাদের শিল্প-সাহিত্য চর্চায় ফেলে আসা জুমিয়া জীবনের নান্দনিক উপস্থাপনার প্রয়াস লক্ষ্য | করা যায়। এই প্রেক্ষিতে চাকমা লোক-সংস্কৃতির অনেক উপাদান নূতন প্রেক্ষাপটে নূতন আঙ্গিকে শহুরে | মধ্যবিত্ত জীবনে অঙ্গীভূত হচ্ছে, যেমনটা অন্যান্য সমাজের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, এক সময় চাকমা নারীদের সাধারণ পোশাক ছিল ঘরে বোনা ‘পিনন’ (সেলাই বিহীন মোটা কাপড়ের ‘পেটিকোট) ও ‘খাদি’ (বক্ষবন্ধনী), যে ধরনের পোষাক তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা প্রভৃতি অন্যান্য পাহাড়ী সম্প্রদায়ও ব্যবহার করে।
শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকমা নারীরা অনেকে প্রাত্যহিক ভিত্তিতে এই পোশাক আর ব্যবহার করে না, তথাপি দেখা যায় নিজেদের চাকমা তথা পাহাড়ী পরিচয়কে তুলে ধরার লক্ষ্যে তারা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পিনন-খাদি পরিধান করে, যদিও ‘খাদি’র বর্তমান ব্যবহার অনেকটা ওড়নার সাথে তুলনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব পোশাক আর ঘরে নিজের হাতে বানানোও না, বরং বাণিজ্যিকভাবে বজ্রকলে উৎপাদিত পণ্য হিসাবে এগুলি বাজার থেকে কেনা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পিনন- খাদির উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রেক্ষাপট পাল্টে গিয়ে এই পোশাক শহুরে প্রেক্ষাপটে নূতন তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে।
চাকমা বর্ষপঞ্জীর সবচাইতে বড় উৎসবের নাম বিজু, যা চৈত্র্যের শেষ দুদিন ও বৈশাখের প্রথম দিন মিলে টানা তিন দিন ধরে চলে (মারমা ও ত্রিপুরারাও ভিন্ন নামে একই উৎসব পালন করে)। পুরানো বছরকে বিদায় দিয়ে নূতন বছরকে বরণ করা বিজু উৎসবের উপলক্ষ, তবে এর সামাজিক তাৎপর্য বাঙালী মুসলমানদের ঈদ বা বাঙালী হিন্দুদের শারদীয় দুর্গোৎসবের সাথে তুলনীয়।
অতীতে কৃষি-নির্ভর গ্রামীন জীবনের ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে বিজু উৎসব পালিত হত। তবে শহুরে প্রেক্ষাপটে বিজু এখন আর শুধুমাত্র পানাহার, বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো, বা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাতের আনন্দ ইত্যাদির মধ্যে সীমিত নেই। সামাজিক মিলন বা পুনর্মিলনের একটি সময় ছাড়াও বিজু এখন চাকমা তথা পাহাড়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সচেতন অনুশীলন তথা পুনঃনির্মাণের একটা উপলক্ষও বটে।
ধর্মীয়ভাবে চাকমারা মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তবে বহু প্রজন্ম ধরে বাহিত লোকায়ত বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক স্রোতধারাসমূহের বিভিন্ন প্রভাবও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লোকায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি একসময় কালীপূজাসহ বিভিন্ন “হিন্দু” আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রভাব চাকমা সমাজে পড়েছিল, পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম চাকমা সমাজে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তা অনেকটা স্তিমিত হলেও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। পক্ষান্তরে চাকমা রাজারা একসময় মুসলিম ধাঁচের নাম ব্যবহার করলেও ধর্মীয়ভাবে চাকমা সমাজে ইসলামের প্রত্যক্ষ বা ব্যাপক কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।
অবশ্য চট্টগ্রামের বাঙালী মুসলমান জনসমষ্টির ঐতিহাসিক আবির্ভাবে অতীতে চাকমা তথা অন্যান্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ শামিল হয়ে থাকতে পারে, যদিও এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। বলা বাহুল্য, অন্য যে কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মতই চাকমা সংস্কৃতিও একটি বহমান ব্যবস্থা, যেখানে সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে চলছে যেগুলোর কোনটা ভেতর থেকে উৎসারিত, কোনটা বাইরে থেকে আসা।
চাকমাদের সমাজ কাঠামো
চাকমা সমাজে ৪৬টি ‘গঝা’ বা গোত্র রয়েছে বলে জানা যায়, যেগুলির প্রতিটি আবার বিভিন্ন গুখি (গুষ্টি) বা উপগোত্রে বিভক্ত। (এই গোত্রগুলির মধ্যে একটির নাম হল ‘লারমা’, যেটি বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছে জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নামের অংশ হিসাবে। উল্লেখ্য, নামের অংশ হিসাবে গোত্র উপাধি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত চাকমা সমাজে বিরল)। একসময় চাকমা সমাজে গোত্র সংগঠন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবে সমকালীন প্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে, অন্ততঃ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকমাদের মধ্যে।
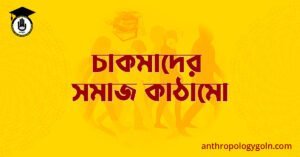
বস্তুতঃ চাকমাসহ সকল পাহাড়ী জনগোষ্ঠী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থার অধীনে চলে আসার পর থেকে গোত্র- সংগঠনের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল, যে প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ প্রাক-ব্রিটিশ আমলেই সূচিত হয়েছিল।প্রথাগতভাবে চাকমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা সামাজিক ক্রমোচ্চবিন্যাস ছিল যার শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করতেন চাকমা রাজা (বা রাণী)।
মোগল বা ব্রিটিশ আমলে রাজ পরিবারের ঠিক পরেই যেসব চাকমা পরিবার সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামোয় সাধারণ প্রজাদের চাইতে উচ্চ অবস্থানে ছিল, তাদের উত্তরসূরীরা এখনো বিভিন্ন সামন্তযুগীয় পদবী – দেওয়ান, তালুকদার, খীসা – ব্যবহার করে থাকেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে যে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছিল, তার একটি ছিল ‘চাকমা সার্কেল’, যেখানে চাকমা জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীভূত ছিল।
চাকমা সার্কেলের চীফ পদটি ছিল চাকমা রাজাদের জন্য সংরক্ষিত। তবে ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে চাকমা রাজাদের মর্যাদা যাই হয়ে থাকুক, অন্ততঃ ব্রিটিশ আমল থেকে ‘চাকমা রাজা’ পদটির অর্থ ‘চাকমাদের রাজা’ ছিল না, বরং তা ছিল “চাকমা সার্কেলের চীফ বা রাজা’। এই ব্যবস্থা অনুসারে ‘চাকমা সার্কেলে’ বসবাসরত সকল পাহাড়ী সম্প্রদায়ের উপর কিছু ক্ষেত্রে চাকমা রাজার কর্তৃত্ব স্বীকৃত রয়েছে, পক্ষান্তরে যেসব চাকমা পরিবার অন্যান্য সার্কেলে বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃত্ব প্রযোজ্য নয়।
সার্কেল চীফ বা রাজাদের কার্যাবলীর একটা ছিল নিজ নিজ সার্কেলের অধিবাসীদের কাছ থেকে রাজস্ব -বিশেষতঃ ‘জুম কর’- আদায় করা। সে সাথে প্রথাগত সামাজিক বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রেও সার্কেল প্রধানদের কর্তৃত্ব ছিল। প্রতিটা সার্কেল বিভক্ত রয়েছে অনেকগুলি মৌজায়। মৌজা প্রধান বা ‘হেডম্যান’দেরও রাজস্ব আদায় ও সামাজিক বিচারকার্য পরিচালনায় ভূমিকা ছিল।
প্রতিটা পাহাড়ী গ্রাম বা ‘পাড়া’য় রাজা-হেডম্যানদের অনুমোদিত একজন করে গ্রাম প্রধান বা ‘কার্বারী’ রয়েছে। প্রতিটা জুমচাষী পরিবার থেকে একটা নির্দিষ্ট হারে জুম কর আদায় করা হত, যার ভাগ রাজা ও হেডম্যানরা পেতেন (কার্বারীরা এই ভাগ পেতেন না, তবে তাদের বেলায় ‘জুম কর’ মওকুফ ছিল)। ব্রিটিশ আমলের প্রেক্ষিতে রাজা ও হেডম্যানরা সংগৃহীত রাজস্বের যে ভাগ পেতেন, তার যথেষ্ট অর্থমূল্য ছিল, যার ভিত্তিতে চাকমাসহ সকল পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভাজন গড়ে উঠেছিল।
ব্রিটিশ আমলে পাহাড়ী সম্প্রদায়সমূহের জন্য যে “প্রথাগত শাসনব্যবস্থা’ প্রণীত হয়েছিল, তা কাগজে | কলমে এখনো অনেকটা বহাল থাকলেও অনেক দিক থেকেই রাজা-হেডম্যান-কার্বারীদের কর্তৃত্বের | পরিধি বা গুরুত্ব হ্রাস হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে চাকমা তথা পাহাড়ী সমাজে কারো সামাজিক অবস্থান | নিরূপণে পূর্বতন বংশমর্যাদা একমাত্র বা প্রধানতম মাপকাঠি নয়, বরং ব্যক্তির শিক্ষা, পেশা, বিত্ত ইত্যাদি বিষয়ের উপর তা অনেকখানি নির্ভর করে। এদিক থেকে চাকমা সমাজ কাঠামোর বর্তমান গতি- | প্রকৃতি অন্যত্র বিদ্যমান সাধারণ প্রবণতা থেকে ভিন্ন নয়।