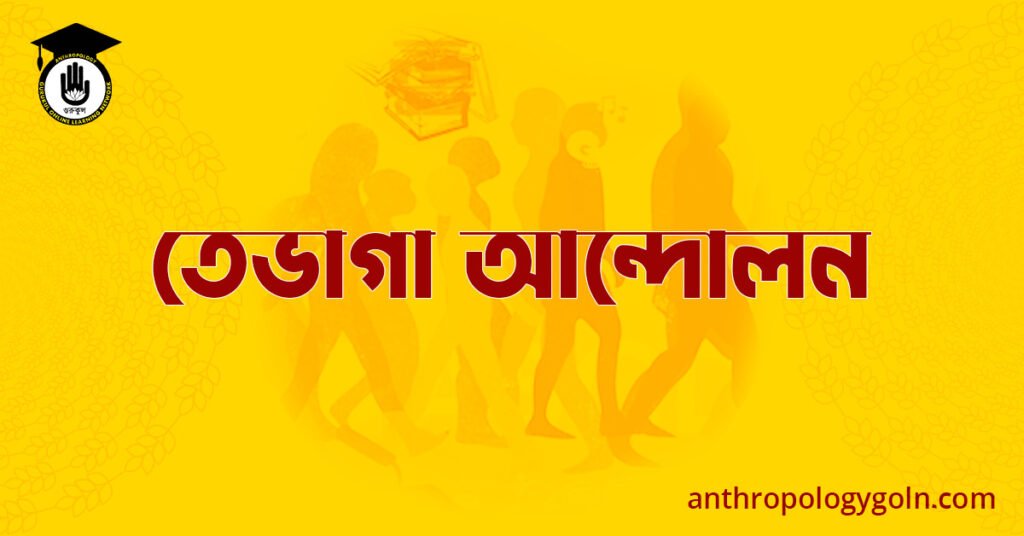আজকের আলোচনার বিষয় তেভাগা আন্দোলন – যা বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন এর অর্ন্তভুক্ত, তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল প্রধানত বাংলা অঞ্চলে। এর স্থায়িত্ব ছিল ‘৪০-এর দশকের শুরু হতে মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই আন্দোলন আপাতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদার কিংবা জোতদারদের বিপক্ষে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আবার চূড়ান্ত বিচারে এই আন্দোলনের লড়াইকারী শক্তির বিপক্ষ ছিল ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র। বিভিন্ন অঞ্চলে তখন জমিদার শব্দটির পাশাপাশি জোতদার শব্দটি ব্যবহৃত হ’ত। বিশেষভাবে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে জমির খন্ডকে জোত বলা হয়ে থাকে। জোতদার কথাটার তাই মানে দাঁড়ায় যার অনেক পরিমাণে জমি আছে।
অন্য ভাষায় জমিদার। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইতোমধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জমিদাররা বংশ পরম্পরায় জমির মালিক হয়ে গেছে। ফলে কৃষকদের জীবনের উপর আগের সময়ের তুলনায় আরো অনেক বেশি অত্যাচার নেমে এসেছিল। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের প্রতিবাদের মূল বিষয় ছিল ফসলের হিস্যা। এখানে আর একটি পরিবর্তনের কথা বলা প্রয়োজন। জমির মালিকানার বদলের পাশাপাশি লাভজনক শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধারণ কৃষকদের হাতে জমি ছিল খুব সামান্যই। ফলে বর্গাচাষ পদ্ধতির প্রচলন ঘটে।
তেভাগা আন্দোলন
বর্গাচাষ পদ্ধতির সাথে তেভাগা আন্দোলনের যোগাযোগ খুবই নিবিড়। তাই তেভাগা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বর্গাচাষ ব্যবস্থা নিয়ে ধারণা থাকা দরকার। এটা খুবই পরিষ্কার যে মালিকানার নিশ্চিত ব্যবস্থা না হলে বর্গাচাষ ব্যবস্থা পোক্ত হ’ত না। অর্থাৎ কাগজে কলমে জমির মালিক দেখা দিল বলেই সেই মালিকের কাছ থেকে জমি বর্গা নেবার পরিস্থিতি তৈরি হ’ল। বর্গাব্যবস্থা হচ্ছে কোন জমির মালিকের কাছ থেকে চুক্তিতে জমি নিয়ে সেই জমিতে চাষবাস করা। এখানে চুক্তির প্রধান ব্যাপার হ’ল ফসলের হিসাব করা। তেভাগা আন্দোলনের আগে উৎপাদিত ফসলের বড় অংশই জমির মালিক নিয়ে নিতেন। সেটার পরিমাণ ছিল মোটামুটি তিন ভাগের দুই ভাগ ।
এই রকম পরিমাণে ফসল দিয়ে দিতে হত বলে চাষীর অবস্থা দিন দিন নাজুক হতে থাকল। শরীরের পরিশ্রম, হালের বলদ খাটিয়ে চাষী পেতেন সামান্য পরিমাণ ফসল। আর কোন পরিশ্রম না করেই জমির মালিক বা জোতদার পেতে থাকলেন সিংহভাগ ফসল। বর্গাচাষীদের সকলেরই পূর্বসূরীরা ছিলেন রায়ত কৃষক। আগে খাজনা দিতে হ’ত। নতুন ব্যবস্থায় সেটা জমির দাম বা ভাড়া হিসাবে দেয়া লাগল । আর তাতে পরিমাণটাও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছিল। অনেক ক্ষেত্রে বর্গার উপচুক্তিও হ’ত। অর্থাৎ এক পরিবার বর্গা নিয়ে আরো দরিদ্র পরিবারকে সেই কাজ দিচ্ছে এবং লাভের ফসল রেখে দিচ্ছে।
এই মধ্যসত্ত্বভোগী কৃষক শ্রেণীর কারণে চাষী কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গেল। এর মধ্যে দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, ফসল না হওয়ার মত প্রাকৃতিক আক্রমণ তো আছেই। এটা ঠিক যে বর্গাচাষীদের মধ্য থেকে অনেক পরিবার পরবর্তীকালে শহুরে লেখাপড়া করা সুবিধা পাওয়া শ্রেণীতে এসেছে। কিন্তু সেটা সাধারণ কোন অবস্থা নয়। সাধারণ কৃষকদের জীবন মৃত্যুতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে কৃষকদের মধ্যে এই জীবন বদলাবার দুর্দান্ত আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। এক সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষকরা বিদ্রোহ করতে শুরু করেন। খাতা কলমে প্রধান দাবী ছিল ফসলের তিন হিস্যার দুইটা দিতে হবে চাষীকে, যিনি শারীরিক পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে থাকেন।
কিন্তু এই সংগ্রাম ছিল আসলে জমির মালিক বড়লোক শ্রেণীর এবং রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। কৃষকদের । এই দাবী আদায়ের জন্য তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে সভা-সমিতি এবং বিক্ষোভ করতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে এই কর্মসূচী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। অবশ্য উত্তর বাংলাতে আন্দোলনটি বেগবান ছিল বলে লিখিত ইতিহাসে এই অঞ্চলের কথাই বেশি জানা যায় । এই পদক্ষেপ নেয়ার সাথে সাথেই জমির মালিকরা একদিকে পুলিশ এবং অন্যদিকে ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল দিয়ে কৃষকদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিল। অত্যাচার বলতে মারধোর, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়া, খুন, গুম এবং ধর্ষণ।
পুলিশ মারধোর করা ছাড়াও গ্রেফতার করে পুলিশী হেফাজতে নির্যাতন চালাতো কৃষকদের উপর। জমির মালিকরা আরেকটা কাজ শুরু করেছিল। লাঠিয়াল গুণ্ডা দিয়ে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল জমি থেকে কেটে নিয়ে আত্মসাৎ করত তারা। এর জবাবে কৃষকরাও দল বেঁধে উৎপাদিত শস্য তুলে নিয়ে আসতেন নিজেদের ভান্ডারে। ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ ইত্যাদি শ্লোগান জনপ্রিয় হয় তখন থেকেই। কৃষকদের উপর পুলিশী এবং গুাবাহিনীর আক্রমণ এতটাই তীব্র হয়েছিল যে বহু কৃষকের তখন দিনরাত পালিয়ে থাকবার দরকার পড়ত। বিশেষভাবে যাঁরা সংগঠক হিসেবে |
পরিচিত ছিলেন। কৃষকরা তখন নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পুলিশ ও জমির মালিকদের উপর | পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দেয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের বিরুদ্ধে কৃষকদের সাহসী লড়াইয়ের গল্প এখনও ছড়িয়ে আছে। এর সব যদিও সংরক্ষণ করা হয়নি। একদিকে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে পুলিশ, | অন্যদিকে কৃষকদের জীবন যাপনের দাবী ছাড়া আধুনিক অস্ত্র বলতে কিছু নেই। কৃষক শ্রেণীর মানুষজন তখন নিজেদের ঢাল, সড়কি, বল- ম নিয়েই একাধিক যুদ্ধে পুলিশকে পরাস্ত করেছে। তেভাগা আন্দোলনের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে নারীদের বা কিষাণীদের শক্তিশালী অংশগ্রহণ ছিল।
বহু অঞ্চলে পুরুষদের বেশির ভাগ পালিয়ে ছিলেন এবং পুলিশের সঙ্গে মূল লড়াই হয়েছে নারীদের। আর বাংলাভাষী ছাড়া অন্য জাতির মানুষ এই আন্দোলনের বড় নির্মাতা ছিলেন: সাঁওতাল, হাজং, বা খাসিয়া। এই কৃষক আন্দোলন দেখে একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসকরা ভীত হয়েছিল, অন্যদিকে ভীত হয়েছিল বাংলার জমি | মালিক শ্রেণী এবং উঠতি শহুরে শ্রেণী। কারণ কৃষকদের এই সংগ্রাম তাদের স্বার্থের বিপক্ষে ছিল পরিষ্কারভাবে। তবে জমির মালিক শ্রেণী এবং উঠতি শহুরে শ্রেণীর অনেক সদস্যই কৃষকদের এই ন্যায্য | দাবীর স্বপক্ষে ছিলেন। শহরের রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তাঁরা কৃষকদের দাবী দাওয়াকে সমর্থন দিতেন কেউ কেউ।
এ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ করতেন তাঁরা। এখানে প্রথমেই আসে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কথা। এই দলের বাইরেও অনেক সমাজতন্ত্রী কৃষকদের তেভাগা আন্দোলনকে সহায়তা করে গেছেন। তেভাগা আন্দোলনের কারণেই ইলা মিত্রের মত নেত্রীর নাম উচ্চারিত হয়। কিন্তু নাম না জানা বহু কৃষক-কিষাণী পুলিশের বা লাঠিয়ালদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আর অন্য অনেকে কঠিন নির্যাতনের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন যাঁদের নাম আমাদের জানার কোন সুযোগ হয়নি।
লিখিত ইতিহাসে এই আন্দোলনের নাম তেভাগা আন্দোলন। যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে এর নাম বিভিন্ন ছিল। যেমন এই আন্দোলন ছড়িয়েছিল বহু অঞ্চলে তেমনি এর ধরন, দাবী দাওয়া এবং নাম হয়েছিল বিবিধ। কোথাও সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোথাও হাজং বিদ্রোহ, কোথাও বা টংকা বিদ্রোহ। খাতা কলমে তেভাগা লড়াইয়ে কৃষকরা জিতেছেন। বাংলা অঞ্চলে ফসলের ভাগের একটা বন্দোবস্ত হয়। কৃষক আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা নেয়। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনের দাবীও জোরাল হয় এই আন্দোলন থেকেই। কিন্তু জমির মালিকানা কিংবা কৃষকের দুর্দশা তাতে বদলায় না।
চিত্র ১: অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের মানচিত্র
পরবর্তী কালে কৃষকদের দুর্দশা দেখে তা আমরা বুঝতে পারি। বাংলাদেশে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ ছাড়া গ্রাম থেকে ঘর হারানো মানুষ শহরে চলে আসছেন। সেখানে কাজ নেই। শহরে নিতান্ত অল্প মজুরির কাজ খুঁজছেন তাঁরা। সেটারও কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থাই বলে দেয় কৃষকদের অবস্থা। কিন্তু নিজেদের জীবনের বদল ঘটাবার জন্য উদ্যম ও লড়াই তাঁরা থামাননি ।
আরও দেখুনঃ