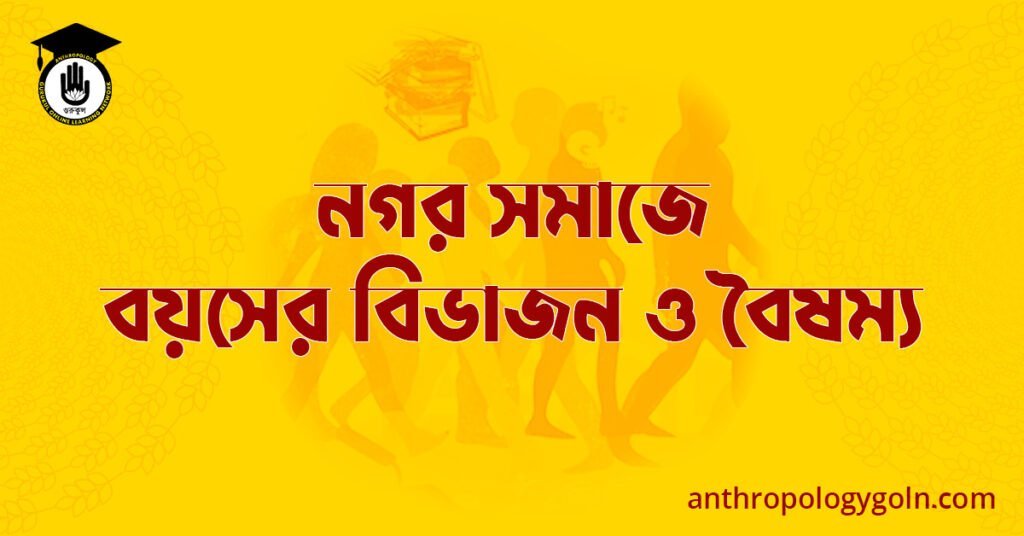আজকের আলোচনার বিষয় নগর সমাজে বয়সের বিভাজন ও বৈষম্য – যা বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন এর অর্ন্তভুক্ত, শহরাঞ্চলে বয়সের বিভাজন ঘটে থাকে আইনের মাধ্যমে। প্রচলিতভাবে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত নারী বা পুরুষ উভয়েই শিশু হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন। এই মুহূর্তে জাতিসংঘের মানদন্ড অনুযায়ী বয়সের সীমারেখাটি হচ্ছে ১৮ বছর। এই বয়সের পর কতকগুলি অধিকার স্বীকৃতি পায়। যেমন: ভোট দেয়ার অধিকার, কোন কিছু কেনার অধিকার ইত্যাদি। পশ্চিমা সমাজে এই বয়স হবার আরও কিছু সামাজিক মানে আছে। এই বয়সের পর আশা করা হয় সন্তানেরা বাবা-মার কাছ থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করবেন।
তাছাড়া এই বয়সের পর যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা আইনত দন্ডনীয় নয়। কিশোর- কিশোরী বয়স থেকে ‘যুবক-যুবতী’ হয়ে ওঠার মত নগর সমাজে প্রৌঢ়/বৃদ্ধ হয়ে ওঠার ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে পুরুষদের মধ্যে একটা সময়ে চাকুরি বা কাজ থেকে অবসর নেবার চর্চা আছে। আশা করা হয় এই সময়ে তিনি বিশ্রাম নেবেন এবং তাঁর পুত্র সন্তানেরা ব্যবসা সামলাবেন কিংবা চাকুরি করে রোজগার করবেন। নারীদের গেরস্থালি কাজ থেকে অবসর নেয়ার সুযোগ থাকে না। পাশাপাশি লক্ষ্য করার মত কিছু ব্যাপার আছে। হাসি-ঠাট্টা এবং আলাপ-আলোচনার মধ্যেও বয়সের বিভাজন ধরা পড়ে। যেমন: ‘এখন তো তুমি দাদা হয়েছ, তোমার কি এখন এসব মানায়?”
নগর সমাজে বয়সের বিভাজন ও বৈষম্য
সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে বয়সের ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ বা বৈষম্য আধুনিক সমাজে নেই। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে এই ধারণাটা ভ্রান্ত। পরিবারে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ আলাপ- আলোচনায় অল্প বয়সীদের কখনোই অংশ নিতে দেয়া হয় না। তাঁদের মতামত কিংবা ভাবনা-চিন্তাকে হাল্কাভাবে নেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে খাবার-দাবার কিংবা আসবাবপত্র ব্যবহারের বেলায়ও বঞ্চিত হয়ে থাকেন পরিবারের অল্প বয়সী সদস্যরা।
এসব ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থাও পুরুষদের তুলনায় নিমুখী। বাংলা ভাষায় সর্বনামের বেলায় দেখা যায় নি শ্রেণীর মানুষের জন্য ‘তুমি’ ব্যবহার করা হয়ে থাকে । পাশাপাশি অল্প বয়সীদের বেলায়ও তা করা হয়। বয়স ১৮ হওয়া মানেই এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে পারা নয়। প্রায়শই কাউকে ঘায়েল করার জন্য বলা হয় ‘তুমি তো আমার হাঁটুর বয়সী।’
বৈষম্যের এই চিত্র কেবল এখানেই সীমিত নয়। চাকুরি কিংবা পেশাগত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে একটা শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন নিয়োগকর্তাই বর্তমান নগর – সমাজে চাকুরি দিতে চান না। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা সকলের একরকম না। বৈষম্য এখানেই। পেশাদার জগতে সাধারণত অভিজ্ঞতার কথা গর্বের সঙ্গে বলা হয়েও থাকে। এটা আধুনিক সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয় যে কোন সামাজিক প্রসঙ্গে মতামত দেয়া বা আলাপ-আলোচনার জন্য বয়স্ক এবং পুরুষদের বাড়তি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এখানে কোন তরুণ-তরুণী বা কিশোর- কিশোরীর তীক্ষ্ণ বিশে- ষণ থাকলেও তা চাপা পড়ে যায়।
প্রচার মাধ্যমের যে সমস্ত কাজকে চিন্তাশীল ভাবা হয়ে থাকে তার প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব তুলনামূলকভাবে বয়স্ক পুরুষদের হাতে। তা সে টেলিভিশনই হোক আর পত্রিকার রাজনীতি-অর্থনীতি পাতাই হোক। বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাতে গুরুত্ব দিয়ে কিশোর-কিশোরীর ছবি ছাপা হয় কেবল মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে। সেখানেও তাঁদের সাফল্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে তাঁদের বাবা-মার ভূমিকার কৃতিত্ব দেয়া হতে থাকে । এগুলো কেবল কিছু উদাহরণ বয়স ভেদে বৈষম্যকে বোঝার জন্য ।
আধুনিক সমাজে বয়সের দিক থেকে অল্প বয়সীরাই যে কেবল বৈষম্যের শিকার তা নয়। এখানে বৃদ্ধরাও বৈষম্যের শিকার। সমাজের ঘটনাবলী তলিয়ে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। বয়সে যাঁরা অনেক প্রবীণ তাঁদেরকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে বোঝা মনে করা হয়। প্রবীণদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করার সামাজিক প্রবণতা আছে। কেউ কেউ বলে থাকেন প্রবীণেরা যদি অনেক সম্পত্তিবান হন তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় না। সেক্ষেত্রে সম্পত্তির ওজনে মানুষের মর্যাদা মাপা হচ্ছে। নারীরা এই পরিস্থিতিতে আরও করুণ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে থাকেন।
কারণ সামাজিকভাবে নারীর সম্পত্তির নজির কম। শহুরে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারে অবসরপ্রাপ্ত এই মানুষজন নানাবিধ অবজ্ঞা আর চাপের মধ্যে থাকেন। সেই হিসেবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই সমাজে গ্রহণযোগ্যতা আছে কেবল একটা নির্দিষ্ট বয়সের এবং অবশ্যই নির্দিষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতার পুরুষদের। কারণ তাঁরাই কেবল সমাজে অন্য শ্রেণীর, অন্য লিঙ্গের এবং অন্য বয়সের মানুষদের অবস্থান ঠিক করে দিতে পারেন। তাঁদের কথার মূল্যায়ন করতে পারেন, সঠিক-বেঠিক নির্ধারণ করতে পারেন, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটা নিশ্চিতভাবেই বৈষম্য।
আরও দেখুনঃ