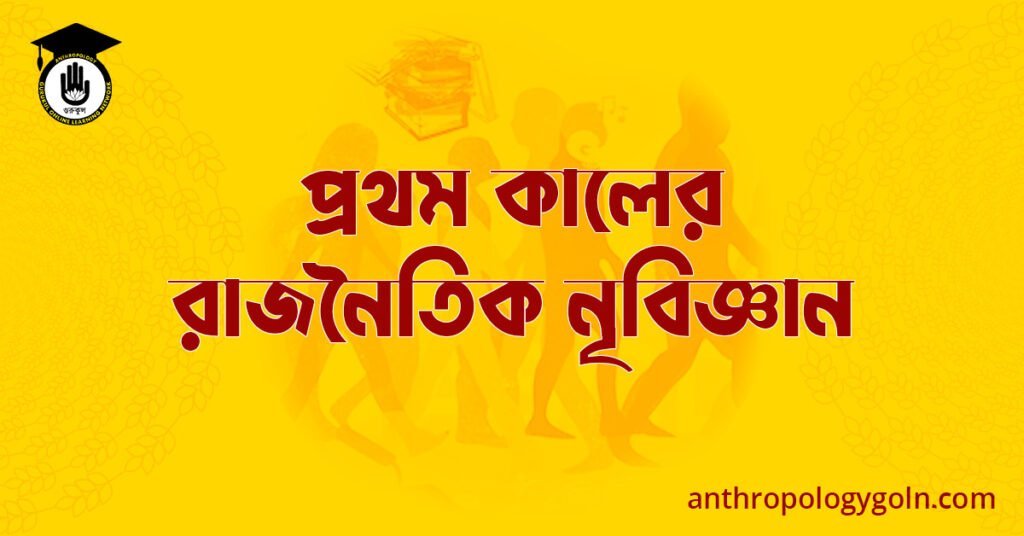আজকের আলোচনার বিষয় প্রথম কালের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান – যা রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এর অর্ন্তভুক্ত, আগের আলোচনা থেকেই আপনারা দুটো স্পষ্ট ব্যাপার জানেন। তা হ’ল: এক, প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিন্তা-ভাবনা থেকে ভিন্ন ভাবে নৃবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন; দুই, ‘৪০ – ৬০ এর দশকে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের মূল সময়কাল ছিল। কিন্তু পুরো বিষয়টা এত সহজ নয়। নৃবিজ্ঞানে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে সেই শুরুর কাল থেকেই। সেই হিসেবে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পর্বকালকে তিন ভাগে ভাগ করা সুবিধাজনক।
প্রথম কালে লুইস হেনরি মর্গান, হেনরি মেইন, এমনকি হার্বার্ট স্পেন্সার-এর নাম চলে আসে। প্রথম কালের চর্চাকে অনেকেই রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান না বলে ‘রাজনীতির নৃবিজ্ঞান’ বলতে চেয়েছেন। এর একটা কারণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে এইসব নৃবিজ্ঞানীদের অনেককেই একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেটা হ’ল: আমেরিকান ইন্ডিয়ান বা রেড ইন্ডিয়ান সমাজের উপর গবেষণা। এটা তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটা বিরাট মাথাব্যথা ছিল। কারণ এই সব আদিবাসীদের জমি দখল করবার পর এবং তাঁদেরকে আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্রের সাহায্যে বাগে আনার পর মার্কিন সরকার তখন সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়েছে।
প্রথম কালের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান
এই ব্যবস্থার মানে হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এবং সরকারী পরিকল্পনার অধীনেই কেবল এই আদিবাসীদের জীবন যাপন করতে হবে। এরকম পরিকল্পনা নেবার কারণে সরকারের জন্য খুব জরুরী হয়ে দেখা দিল শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্ন এবং আদিবাসীদের ‘উন্নয়নের’র প্রশ্ন। ফলে মূলত আইন বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দেয়া হ’ল যাতে তাঁরা আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব সংগঠন ও আইন-কানুন পর্যবেক্ষণ করেন এবং সরকারের সাথে আদিবাসীদের বিভিন্ন ‘চুক্তি’ খতিয়ে দেখেন। এভাবে প্রথম পর্যায়ে যে সকল কাজ পাওয়া যায় তার সবগুলিই আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের উপর করা গবেষণা কাজ।
এখানে আলাদা করে উলে- খ করা দরকার মেইন-এর ‘এনশিয়েন্ট ল’ এবং মর্গান-এর ‘এনশিয়েন্ট সোসাইটি’ গ্রন্থের নাম। বিশেষভাবে মর্গানের নাম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই গবেষণা কাজ থেকে পরবর্তীতে নৃবিজ্ঞানে বিবর্তনবাদী চিন্তার ভিত্তি তৈরি হয়। মর্গান দেখেছেন কিভাবে গোত্র সংগঠন থেকে ধীরে ধীরে সমাজে আধুনিক সরকারের কাঠামো তৈরি হয়ে থাকে। অর্থাৎ মর্গানের যুক্তি ছিল প্রথমে গোত্র সংগঠনই ছিল সরকারের আদিরূপ। হেনরি মেইনের কাজ অবশ্য আইনের বিবর্তন নিয়ে ছিল।
পরবর্তী সময়কালে রেড ইন্ডিয়ানদের বাইরে বেশ কিছু গবেষণা চলতে থাকে। এখানে মনে রাখা দরকার যে ইউরোপের তখন প্রায় সারা দুনিয়া ব্যাপী উপনিবেশ ছিল। তারা তখন আফ্রিকার প্রায় সকল অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য এবং ওশেনিয়াতে গবেষণা চালিয়েছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গবেষণা চলেছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে, হাওয়াই এলাকায় কিংবা ফিলিপাইনে। এই সব গবেষণাতে কখনোই কিন্তু এই বিষয়টা গুরুতরভাবে আসেনি যে ইউরোপের এবং মার্কিনের রাজনৈতিক শক্তি কিভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের উপর চেপে বসে আছে।
এ ধরনের সমালোচনা এসেছে আরো পরে। সত্যিকার অর্থে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নানান দেশ ঔপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তি পেয়েছে, এবং আরো পরে যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হারলো। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সারা পৃথিবী ব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ প্রতিরোধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তার সঙ্গেও এটার নিবিড় সম্পর্ক আছে। যাই হোক, যে সময়ের কথা হচ্ছে সেই সময়ে ফ্রাঞ্জ বোয়াস এবং ব্রনিল ম্যালিনোস্কি-এর শিক্ষার্থীদের নাম চলে আসবে। কারণ তাঁরা তখন এই সব ফরমায়েশী গবেষণার কাজ করছেন। এই সকল গবেষণা হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকদের এবং বাণিজ্য করতে চাওয়া বড় বড় মার্কিন-ইউরোপীয় কোম্পানির চাহিদা অনুযায়ী; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের দেয়া অর্থে।
সেটা হ’ল ২০ ও ৩০-এর দশকের কথা। বোয়াসের শিক্ষার্থীরা মূলত আমেরিকান আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের অথবা ইউরোপের অধিকৃত কোন ভূখন্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের ওপর কাজ করেছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই গবেষণা কাজগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল: এগুলো আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করেছে। কোনভাবেই সেগুলো রাজনৈতিক সম্পর্ক ও পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠেনি। এই সমস্ত কাজের কেন্দ্রে সংস্কৃতির ধারণাই কাজ করেছে, ক্ষমতার ধারণা নয়।
দু’ একটা গবেষণা আগ্রহী ছিল ইন্ডিয়ানদের সাথে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের সংঘর্ষ বা শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণকে চিহ্নিত করতে। সেই কাজগুলো কোনভাবেই সম্মুখভাগে আসতে পারেনি। এমন একজন গবেষক ছিলেন উইলিয়াম ক্রিস্টি ম্যাকলিওডএবং আরেকজন হচ্ছেন মনিকা হান্টার। বরং দেখা গেছে রবার্ট রেডফিল্ডের মত গবেষকগণ মেক্সিকোতে যখন রাজপথে বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে তখন স্থান-কালহীন ‘লোক’সমাজের গল্প নিয়ে এসেছেন। এখানে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, ‘নেটিভ’ মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ, শাসন এবং পর্যুদস্ত করবার বাস্তব সমস্যা থেকে এবং তাদের মধ্যকার ইতিহাসের যে ভিন্নতা তার আগ্রহ থেকে ঔপনিবেশিক সময়কালে নৃবিজ্ঞানে রাজনীতি বিষয়ক কিছু গবেষণা কাজ দানা বেঁধেছিল ।
আরও দেখুনঃ