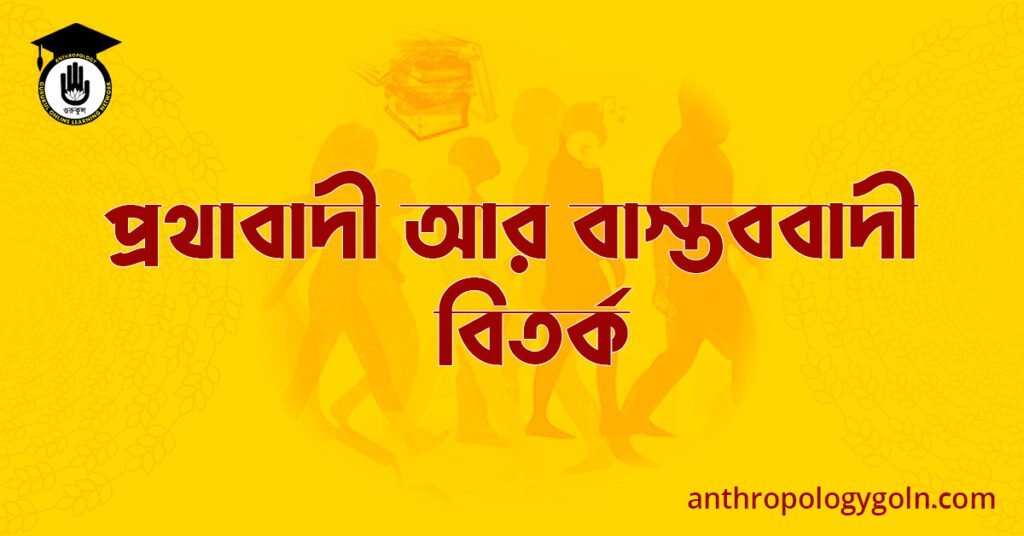আজকের আলোচনার বিষয় প্রথাবাদী আর বাস্তববাদী বিতর্ক – যা অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এর অর্ন্তভুক্ত, এতক্ষণের আলোচনায় এটা বোঝা গেছে যে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান কোন একটি সমাজের উৎপাদন এবং বণ্টন সংক্রান্ত নানাবিধ দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে। যেহেতু উৎপাদনের সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ বিষয় জড়িত তাই অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পরিধি মোটেই সংক্ষিপ্ত নয়। কিন্তু দীর্ঘ সময়কাল ধরে নৃবিজ্ঞানীরা একেবারেই অপশ্চিমা সমাজে কাজ করে গেছেন। ফলে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের আলাপ- আলোচনায় কেবলমাত্র এমন ধরনের সমাজ বিবেচিত হয়েছে যা কিনা শিল্পভিত্তিক নয়।
কিন্তু প্রাক্-শিল্প সমাজের গবেষণার মধ্যেও ব্যাপক বিতর্ক দেখা দেয়। এই বিতর্কের মূল জায়গা হচ্ছে: প্রচলিত অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়ে অন্যান্য অপশ্চিমা সমাজের আর্থব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা। আগেই জেনেছেন ইউরোপের নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এইসব সমাজ ছিল “সরল” বৈশিষ্ট্যের।
প্রথাবাদী আর বাস্তববাদী বিতর্ক
ম্যালিনোস্কি ছাড়াও ব্রিটেনের রেমন্ড ফার্থ এবং অন্ডে রিচার্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেলভিন্স হার্সকোভিস এবং সল ট্যাক্স অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। এটা ঠিক যে, , ম্যালিনোস্কি যখন কাজ করেন তখন একটা শাখা হিসেবে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পরিচয় গড়ে ওঠেনি। কিন্তু সমগ্র সমাজের বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানে আর্থব্যবস্থা প্রসঙ্গ এসেছে।
প্রথম পর্যায়ের এই সকল তাত্ত্বিক- চিন্তুকরাই স্পষ্টভাবে প্রচলিত অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়ে অপাশ্চাত্যের সেইসব সমাজের আর্থব্যবস্থা বুঝতে চেয়েছেন। তাঁদের ভাষায় “উপজাতীয়” (ট্রাইব্যাল) এবং কৃষক আর্থব্যবস্থা। যে সকল নৃবিজ্ঞানীরা অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত তত্ত্ব ও সূত্র দিয়ে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের আর্থব্যবস্থা বুঝতে চেয়েছেন তাঁদেরকে ফর্মালিস্ট বা প্রথাবাদী বলা হয়ে থাকে। বিতর্কের জোরালো সূচনা ঘটে যখন কার্ল পোল্যানয়ি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ট্রেড এ্যান্ড মার্কেট ইন আর্লি এম্পায়ার প্রকাশ করেন। এখানে তিনি পূর্বসূরী সকল অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানীদের কঠোর সমালোচনা করেন যে তাঁরা কোনরকম সমালোচনা ছাড়াই যাবতীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বকে সকল সমাজের জন্য প্রযোজ্য মনে করেছেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেন পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের আমূল ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা কেবল অগ্রসরতার নয় বলে তিনি যুক্তি দেখান, বরং একেবারে অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজার মুখ্য, প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পোল্যানয়ির মতে, উপহার বা নানান আনুষ্ঠানিক বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছে। এই প্রেক্ষিতে তিনি বিনিময় পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করেন: পারস্পরিক লেনদেন, পুনর্বণ্টন এবং বাজার । তাঁর যুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক পদ্ধতিকে বুঝবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধারণাগত রাস্তা ও সূত্রাবলী প্রয়োজন । বিনিময় পদ্ধতি পোলেনি এবং তাঁর অনুসারীদের কাছে (যেমন, জর্জ ড্যাল্টন, মার্শাল সাহলিন্স) কেন্দ্ৰীয় স্থানে রয়েছে।
তাঁদের চিন্তাধারাকে সাস্ট্যান্টিভিস্ট বা বাংলায় বাস্তববাদী বলা হয়েছে। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। ফর্মালিস্ট ও সারস্ট্যান্টিভিস্ট শব্দদুটোর বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে প্রথাবাদী ও বাস্তববাদী। এই তর্জমা খুবই বিভ্রান্তিকর। বাংলায় এই শব্দদুটোকে যথাক্রমে ‘অর্থশাস্ত্রীয়’ ও ‘সংসৃতিমুখিন’ বা ‘সংসুতিবাদী’ বললে আরও সুবিধা হত। তবে বর্তমান লেখায় প্রচলিত শব্দদুটোই ব্যবহার করা হয়েছে।
এখানে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন বিশেষ কোন্ ব্যাখ্যাতে বাস্তববাদী এবং প্রথাবাদীরা ভিন্ন। অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত চিন্তাভাবনাতে খুবই জরুরী একটা ধারণা হচ্ছে যৌক্তিক আচরণ। যৌক্তিক আচরণ প্রসঙ্গ বুঝতে গেলে নয়া ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের একটা জায়গা লক্ষ্য করতে হবে। তা হচ্ছে: এখানে সকল ভাবনাচিন্তার কেন্দ্রে আছে এককের ধারণা। এর মানে হচ্ছে কখনো একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এবং কখনো কোন একটা মাত্র উৎপাদন কারখানাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে যৌক্তিক আচরণ বলতে স্পষ্টভাবে সর্বোচ্চকরণের (maximisation) ধারণা জড়িত।
অর্থনীতির তত্ত্বে দেখা হয় ক্রেতা বা ভোক্তা হিসেবে কোন ব্যক্তি তাঁর সর্বোচ্চ লাভ নিশ্চিত করতে চান। একইভাবে কোন উৎপাদন কারখানা চায় কোন দ্রব্য উৎপাদন করে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করতে। এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই একটা আর্থব্যবস্থা জারী থাকে। সারাংশে এই হচ্ছে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও সূত্রের একটা মূল বক্তব্য। প্রথাগত অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেছেন যে, এই প্রক্রিয়াটি সমানভাবে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানেই বাস্তববাদীদের আপত্তি। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে: কোন একটি সমাজের, বিশেষভাবে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের, মানুষের আর্থনীতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে ঐ সমাজের নির্দিষ্ট কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতি-নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত।
জ্ঞাতিসম্পর্ক বা ধর্মের মত বিষয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে থাকে। এক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজের উদাহরণ টেনেছেন। যেমন, ম্যালিনোস্কির কাজে কুলাপ্রথাকেও তাঁরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার কোয়াকিউটাল সমাজে পুনর্বণ্টনকেও উদাহরণ হিসেবে টেনেছেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী পাঠে কিছু আলাপ করার সুযোগ রয়েছে। একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। উৎপাদন অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় ভাবনা হলেও প্রথাবাদী ও বাস্তববাদীদের চিন্তাভাবনার পার্থক্য খেয়াল করা যায় বিনিময়ের প্রশ্নে। যেখানে প্রথাবাদীদের আগ্রহের মূল জায়গা হচ্ছে ব্যক্তির আচরণ সেখানে বাস্তববাদীদের আগ্রহের জায়গা হচ্ছে বিনিময়ের ধরন। ব্যক্তির আচরণ সেখানে সমাজের নিয়ম-নীতির বাইরের বিষয় নয়।
আরও দেখুনঃ