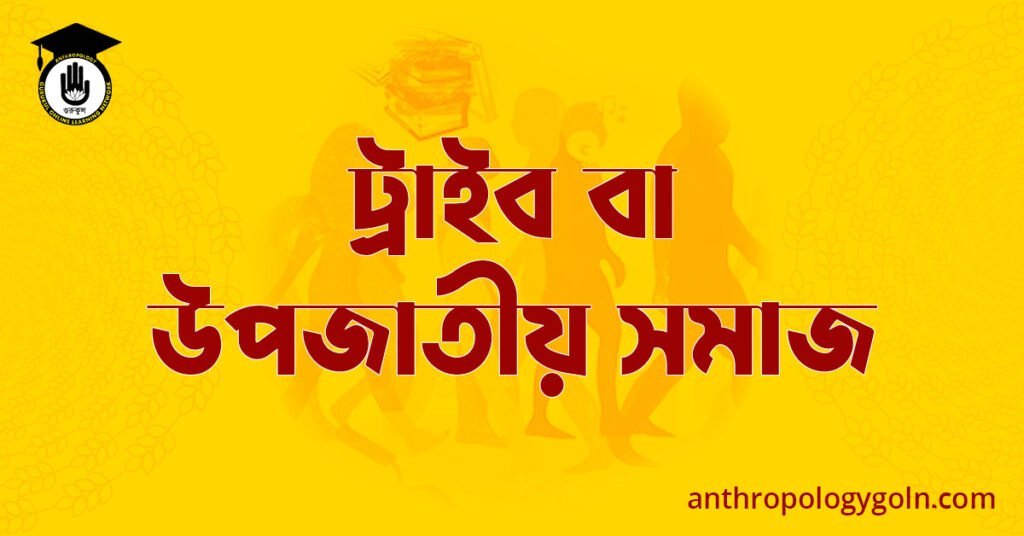আজকের আলোচনার বিষয় ট্রাইব বা উপজাতীয় সমাজ – যা রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থা এর অর্ন্তভুক্ত, ব্যান্ড সমাজের সঙ্গে এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমাজের পার্থক্যের মূল জায়গা হ’ল: এখানে সমাজের মধ্যে কতগুলো সংঘ কাজ করে।
অর্থাৎ, ব্যান্ড সমাজে যেমন ব্যান্ডই হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একক, এখানে সদস্যদের নানাবিধ সার্বভৌম সংঘ থাকে আর সেই সংঘগুলোর নানাবিধ রাজনৈতিক দায়িত্ব বা ভূমিকা থাকে।
ট্রাইব বা উপজাতীয় সমাজ
“উপজাতীয়” রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেই সংঘগুলো রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে। আবার সেই সংঘগুলোর সমন্বয়ে খোদ ট্রাইবটির রাজনৈতিক কার্যাবলী চলে । সেই হিসেবে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বহুস্থানীয় রাজনৈতিক সংহতি বলা যেতে পারে। তবে সেই সংহতিকে স্থায়ী বলা যায় না।
বরং কোন সমস্যা বা বহিঃ আক্রমণের কালে এই সংহতি কাজ করে। এই সংঘগুলোর মধ্যে যোগাযোগ থাকে সমস্যাটা যতদিন আছে ততদিনই। তারপর নিজ সার্বভৌম এলাকায় সংঘগুলো আবার ফিরে যায়।
নৃবিজ্ঞানীরা ট্রাইব বলতে বুঝিয়েছেন কতকগুলি ব্যান্ডের সমন্বয় যেখানকার সদস্যরা একই ভাষায় কথা বলে, একই সংস্কৃতি তাদের এবং একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশে অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী ট্রাইবের পরিভাষা হিসেবে ‘উপজাতি’ বলে থাকেন। এটা সরকারেরও ভাষ্য।
ইংরেজি ‘ট্রাইব’ কিংবা বাংলা ‘উপজাতি’ – দুই শব্দেরই রাজনৈতিক সমালোচনা আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত উপজাতি নিয়ে রাষ্ট্রের ব্যাখ্য এবং আচরণ এই সমালোচনার কারণ। তাছাড়া নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই রাষ্ট্রের এবং শক্তিশালী জাতির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন বলে সেটাও সমালোচনার কারণ হয়েছে।
ট্রাইবের সদস্য সংখ্যা ব্যান্ড-এর তুলনায় অনেক বেশি। কতকগুলির আকার বেশ বড়। আফ্রিকার টিভদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। আবার নুয়েরদের সংখ্যা ইভান্স প্রিচার্ডের গবেষণার সময়কালে প্রায় ২ লক্ষাধিক ছিল। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী মনে করেন ক্ষুদ্র-জাতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমাজ মূলত পশুপালন এবং চাষবাষ কেন্দ্রিক। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্বও ব্যান্ড-এর তুলনায় বেশি।
ব্যান্ড সমাজের মত এখানেও জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা খুবই ব্যাপক। নৃবিজ্ঞানীরা ট্রাইব সমাজের রাজনৈতিক চালিকা শক্তির মূল কেন্দ্র মনে করেছেন জ্ঞাতিসম্পর্ককে। আগেই উলে- খ করা হয়েছে যে, এর সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এখানে নানাবিধ সংঘ রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে।
ট্রাইব বা “উপজাতি” মধ্যকার এইসব সংঘের মূল ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞাতিসম্পর্ক। গোত্র (ক্লান) হচ্ছে এ ধরনের সংঘের একটা ধরন। আরেকটি ধরন হচ্ছে খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন (সেগমেন্টারি লিনিয়েজ সিস্টেম)। রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হবার ক্ষেত্রে এই দুই সংঘের ব্যাপক গুরুত্ব। এ ছাড়াও সমবয়সীদের দল (এজ সেট) খুবই তৎপর বলে মনে করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা।
বিশেষভাবে পূর্ব ইউরোপের “উপজাতি” সমূহের (ট্রাইব) মধ্যে এর কাজ আলাদা করে ধরা পড়ে। সমবয়সী-দলের কাজ হচ্ছে জাতির বিভিন্ন স্থানীয় অংশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা, সমন্বয় করা।
বিশেষ করে কোন বহিঃজাতির আক্রমণের সময়ে। তবে নৃবিজ্ঞানীরা এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন বিভাজিত গোষ্ঠী ব্যবস্থাকে। নৃবিজ্ঞানী মার্শাল সাহলিন্স (১৯৬১) এবং তারও আগে ইভান্স প্রিচার্ড (১৯৪০) আফ্রিকার টিভ এবং নুয়ের সমাজের উপর এ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন।
খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন হচ্ছে গোত্রের মধ্যকার আরও ক্ষুদ্রতর বিভাজন। যেমন: নুয়েরদের মধ্যে মোটামুটি ২০ টির মত গোত্র খুঁজে পাওয়া গেছিল। প্রত্যেকটি গোত্র একাধিক গোষ্ঠী বা লিনিয়েজ-এ বিভাজিত। গোত্রের প্রথম ভাগকে নৃবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ম্যাক্সিমাল গোষ্ঠী।
এরপর ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকলে পাওয়া যায় মেজর গোষ্ঠী, মাইনর গোষ্ঠী এবং মিনিমাল গোষ্ঠী। এক একটা মাইনর লিনিয়েজ ৩ থেকে ৫টা প্রজন্মের মানুষজনকে ধারণ করে থাকে। সংহতির ব্যাপারটা হচ্ছে: যদি দুইটা মিনিমাল লিনিয়েজ পরস্পরের সাথে গোলমাল করে তাহলে অন্য মিনিমাল গোষ্ঠী নাক গলাবে না।
কিন্তু গোলমালটা যদি হয় এমন কোন দলের সাথে যাদের সাথে আরো পুরোনো প্রজন্মের সম্পর্ক তাহলে গোটা মাইনর গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে যেতে পারে। এভাবে পুরো প্রক্রিয়াটা চলে। পরিশেষে সমস্ত ক্ষুদ্র- জাতি বা ট্রাইব একত্রিত হয়ে যেতে পারে যদি আক্রমণ আসে অন্য কোন জাতি হতে।
এরকম ধ্রুপদী একটা উদাহরণ হচ্ছে নুয়ের এবং ডিংকাদের মধ্যকার দীর্ঘকাল ব্যাপী লড়াই। সংঘর্ষ এবং লড়াইয়ের এই প্রসঙ্গ থেকে সহজেই বোঝা যায় ব্যান্ড সমাজের চেয়ে এই ধরনের সমাজে সামরিক চর্চা জোরদার ছিল। মার্শাল সাহলিন্স মনে করেছেন যে খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন শক্তিশালী ট্রাইবকে নিজেদের এলাকা বাড়াতেও সাহায্য করেছে।
কোন একটা শক্তিশালী “উপজাতি” তুলনামূলকভাবে দুর্বল জাতির বসবাস এলাকাকে পছন্দ করলে সেটা দখল করবার চেষ্টা করতে পারত এই বৃহৎ গোষ্ঠীর আত্মীয় সম্পর্কের কারণে। এ ছাড়াও বহু জাতির মধ্যে বছরে কোন সময়ে একত্রে কোন উৎসবে যোগ দিয়ে সংহতি প্রকাশ করা এবং আনন্দ করবার চল ছিল। বিশেষত ইউরোপ এই সব অঞ্চল দখল করবার আগে ।
ব্যান্ড সমাজের মত এখানেও নেতৃত্ব কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। ক্ষমতার তুলনায় এখানেও প্রভাবই মূল চালিকাশক্তি। সাধারণত দক্ষতা, বিচক্ষণতার মাপকাঠিতেই নেতা বা প্রধান থাকতেন কেউ। নুয়েরদের মধ্যে গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র অংশে বংশের কেউ একজন নেতা থাকতেন যিনি তাঁর স্থানীয় বংশ সদস্যদের কোন রকম শাসন করতে পারতেন, কিংবা দলের জন্য ক্ষতিকর পদক্ষেপের কারণে কাউকে একঘরে করবার উদ্যোগ নিতে পারতেন।
আমেরিকার আদিবাসী জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকম নেতা রাখবার রেওয়াজ ছিল। যেমন শেয়েনে জাতির মধ্যে যুদ্ধের প্রধান এবং শান্তির প্রধান ছিল। কানাডার ওজিবোয়াদের মধ্যে যুদ্ধের নেতা, শিকারের নেতা, উৎসবের নেতা এবং গোত্র নেতা ইত্যাদি বিভাজন ছিল।
কিছু ক্ষেত্রে নেতার পদ ছিল আরও ক্ষমতাধর এবং আরও বেশি সদস্যদের উপর চর্চা করবার মত। যেমন, দক্ষিণ ইরানের বাসেরি যাদেরকে পশুপালক যাযাবর বলা হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের জন্য অনাড়ম্বর ব্যবস্থা ছিল এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যস্থতা করে এগুলো হ’ত। সংঘাত যদি “ট্রাইবে”র ভেতরকার সদস্যদের মধ্যেই ঘটে থাকে, তাহলে নেতাগণ বিবাদকারী পক্ষকে আলোচনা করিয়ে নিষ্পত্তি করে দেন। যদি খুন বা এরকম বড় কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যাতে ক্ষতিপূরণ পায় তার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।
সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে গবাদি পশু ছিল মাধ্যম, যেহেতু মূলত পশুপালন সমাজ এগুলো। আর যদি কোন সদস্য এমন কিছু করে থাকে যাতে খোদ জাতিটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তার ব্যবস্থা হয় ভিন্ন। এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।
শেয়েনে জাতি যখন মহিষ শিকারে বের হয় তখন যাতে কেউই মহিষদের আগে ভাগে সতর্ক করে না দেয় বা ভাগিয়ে না দেয় তার জন্য প্রহরীর ব্যবস্থা আছে। তাঁদের কাজ কাউকে শান্তি দেয়া নয়।
তাঁরা কেবল নজরদারি করেন। এরপরও এই ধরনের অপরাধী কেউ থাকলে প্রহরী বাহিনীর কাজ হচ্ছে সেই লোক যাতে নিজ সমাজের নিয়ম মানে তার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে চাবুক মারার শান্তি হতে পারে, কিংবা ঘোড়ার কান কেটে নেয়া যেটা খুবই লজ্জাকর হিসেবে বিবেচিত।
এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা জরুরী। রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জোর দিয়েছেন: ক) দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের প্রক্রিয়ার উপর; খ) শান্তি- শৃঙ্খলা রক্ষা করবার পদ্ধতির উপর; গ) সমাজের সামরিক প্রস্তুতির উপর। এতে করে মনে হতে পারে অ-ইউরোপীয় সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।
পরবর্তী কালের অনেক নৃবিজ্ঞানীই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, এই সব গবেষণায় গবেষক আগে থেকেই ধরে নিয়েছেন ‘সরল সমাজের’ মানুষেরা যথেষ্ট শৃঙ্খলাপরায়ন নন। তাঁদের যুক্তিতে এই সব সমাজের “উপজাতি”সমূহের মধ্যকার অধিকাংশ দাঙ্গাই ইউরোপীয় হস্তক্ষেপে তৈরি হয়েছে।
কারণ সমাজে সম্পদের উপর তখন টান পড়েছে। উপরন্তু এসব সমাজে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ সামাল দেবার জন্য তাদের যথেষ্ট কায়দা কানুন জানা ছিল।
তাঁরা এই যুক্তিও দেখিয়েছেন যে ইউরোপের সামরিক প্রস্তুতির সামনে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার এই সব জাতি এতটাই অসহায় ছিল যে তাদের মধ্যকার সামরিক প্রস্তুতি আর হাঙ্গামা না দেখে ইউরোপের ভূমিকা দেখাই নৃবিজ্ঞানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারত। যেহেতু রাজনীতির অর্থ, তাঁদের মতে ক্ষমতার পার্থক্য এবং ক্ষমতার সম্পর্ক।
আরও দেখুনঃ