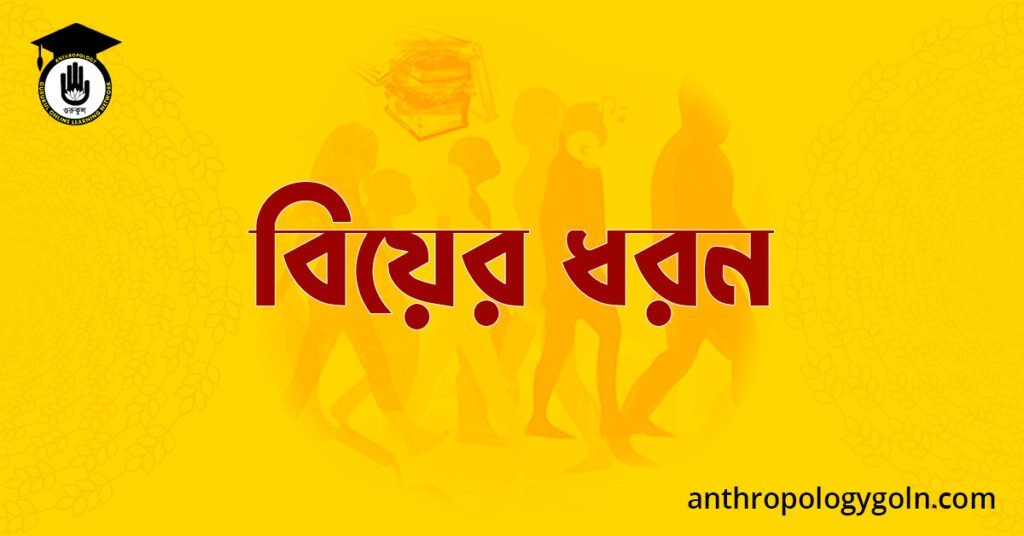আজকে আমরা আলোচনা করবো বিয়ের ধরন নিয়ে । চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা বিয়ে ব্যবস্থার শ্রেণীকরণ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে: বিবাহ সঙ্গী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোত্রের গুরুত্ব, পতি-পত্নী সংখ্যা, পতি কিংবা পত্নীর ভাই/বোন বিবাহ সঙ্গী হতে পারে কি না, এবং বিবাহে মূল্যবান সামগ্রীর আদান-প্রদান ।
বিয়ের ধরন
অন্তঃর্গোত্র ও বহিঃর্গোত্র বিবাহ
বিবাহ-সঙ্গী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোত্র সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই গুরুত্বকে স্পষ্ট করে তোলেন বৃটিশ আইনজীবী ম্যাকলেনান। তিনি প্রথমে অন্তর্গোত্র (endogamy) এবং বহির্গোত্র (exogamy) পদ দুটির প্রবর্তন করেন। স্পষ্টতই, প্রথমটি ইঙ্গিত করে গোত্রের ভেতরে বিয়ে আর দ্বিতীয়টি ইঙ্গিত করে গোত্রের বাইরে বিয়ে। প্রশ্ন জাগতে পারে: গোত্র বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? এই গোত্র কি সকল সমাজে এক? এখানে, গোত্র বলতে নৃবিজ্ঞানীরা বোঝাচ্ছেন একটি জ্ঞাতিভিত্তিক সামাজিক দল। এর সদস্যপদ, নির্দিষ্ট সমাজের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা অনুসারে, এক সমাজ হতে আরেক সমাজে ভিন্ন হতে পারে।
নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, বিবাহ ব্যবস্থা কেবলমাত্র দুই ধরনের হতে পারে: অন্তর্গোত্রীয় কিংবা বহির্গোত্রীয়। এ ধারণা যে ভ্রান্ত তার প্রতি নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান ফরাসী নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রস। তিনি বলেন, সকল বিবাহ ব্যবস্থা একই সাথে অন্তর্গোত্রীয় এবং বহির্গোত্রীয়। এ কথা বলার পিছনে লেভি-স্ট্রসের যুক্তি ছিল: যে কোন বিয়ে ব্যবস্থা একটি দলের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করে, এবং আরেকটি দলের মধ্যে বিয়ে অনুমোদন করে (এ বিষয়টি ২ নং ইউনিটের ৫ নং পাঠে আলোচিত হয়েছে)।
অন্তর্গোত্রীয় বিয়ের সবচাইতে প্রচলিত ধরন হচ্ছে কাজিন-বিবাহ। কাজিন বিবাহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু সমাজে আছে আড়াআড়ি কাজিন বিবাহ নীতি। এখানে বিয়ে সংগঠিত হয় আড়াআড়ি কাজিনদের মাঝে: ফুপাত-মামাত ভাই ও বোন। আবার কিছু-কিছু সমাজে সমান্তরাল কাজিনদের মধ্যে বিয়ে বাঞ্ছনীয়: চাচাত-খালাত ভাই ও বোন।
সমান্তরাল কাজিন বিয়ের প্রচলন দেখা যায় উত্তর আফ্রিকার মুসলমান আরবদের মধ্যে। বর্হিগোত্রীয় বিবাহ প্রথা অনুসারে গোত্র বা দলের বাইরে বিবাহ বাঞ্ছনীয়। ট্রব্রিয়াও সমাজের বাসিন্দারা বিয়ে করেন নিজ গোষ্ঠী ও গোত্রের বাইরে। লেভি-স্ট্রস অনুসরনে কিছু নৃবিজ্ঞানী বিয়েকে দেখেন মৈত্রী স্থাপনের একটি উপায় হিসেবে। তাঁরা বলেন, বিয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, সম্ভব হতে পারে এমন দ্রব্য ও সম্পদের বিনিময় যা সে এলাকায় পাওয়া যায় না।
ভারতবর্ষে অন্তর্গোত্রীয় বিয়ের ভাল উদাহরণ হচ্ছে জাতিভিত্তিক (caste) বিবাহ। অন্য কথায়, জাতির (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ) ভেতরে বিবাহ-সঙ্গী বাছাই বাঞ্ছনীয়। তবে, মনে রাখা জরুরী যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার এবং পুঁজিবাদ জাতিভিত্তিক বিবাহ ব্যবস্থায় বদল ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে। নৃবিজ্ঞানীরা একমত যে বহির্গোত্রীয় এবং অন্তর্গোত্রীয়, এই দুই নীতির সাথে অন্যান্য বিষয় যুক্ত যেমন কিনা স্থানিক দল, – জ্ঞাতি দল, শ্রেণী, জাতিবর্ণ এবং হয়তো অপরাপর সামাজিক বিভাজন।
আধুনিকায়নপন্থী নৃবিজ্ঞানীরা বহির্গোত্রীয় এবং অন্তর্গোত্রীয় বিয়েকে দেখেন “ঐতিহ্যবাহী”, পিছিয়ে পড়া, জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের রীতিনীতি হিসেবে। তাঁরা বলেন, আধুনিক, শিল্পভিত্তিক সমাজে জ্ঞাতিত্বের মতন আদিম সম্পর্কের স্থান নেই, এ ধরনের সমাজে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হচ্ছে যৌক্তিকতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা, অনুভূতি বা বংশ-পরম্পরায় আঁকড়ে ধরা বিশ্বাস নয়। আধুনিকায়নের সাথে সাথে, শিল্পায়নের সাথে সাথে এ ধরনের সম্পর্কের উচ্ছেদ ঘটতে বাধ্য।
সাম্প্রতিক কালে, নৃবিজ্ঞানে (এবং অন্যান্য জ্ঞানকান্ডে) এ ধরনের পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক ও মতাদর্শিক ধ্যান- ধারণা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, হচ্ছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানের আধুনিক ইউরোপে অন্তর্গোত্রীয় বিবাহের প্রচলন ইউরোপের রাজবংশের মধ্যে বিদ্যমান। কঠোরভাবে পালিত না হলেও বলা চলে, নিজ গোত্রের মধ্য থেকে বিবাহ-সঙ্গী বাছাই করা কাম্য হিসেবে বিবেচিত এবং এটি বাড়বে অনুশীলিত।
নিজ গোত্রের মধ্যে বিয়ে করা যে কাম্য, এটি লিখিত রূপে কোথাও নেই বা বারবার জনসমক্ষে উচ্চারিতও হয় না। কিন্তু ইউরোপভিত্তিক রাজবংশগুলোর সামাজিক সংগঠনের এটি একটি মূলনীতি। এক্ষেত্রে “গোত্র” বা “দল” হচ্ছে সর্ব-ইউরোপব্যাপী রাজবংশ (এটি অবশ্য অখন্ড কিছু নয়, এর কোন একটি মাত্র উৎস নেই) এবং অধিকাংশ বিয়ে রাজবংশের কোন না কোন শাখা-উপশাখার মধ্যেই ঘটে থাকে।
আরো উদাহরণ দেয়া সম্ভব। নরবর্ণকে যদি আমরা একটি সামাজিক দল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি (আলবত, যেই দলের সংজ্ঞা করা হয়ে থাকে জৈবিকতার ভিত্তিতে) তাহলে ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকার অধিকাংশ বিয়েকে অন্তর্গোত্রীয় মনে হতে পারে, যেহেতু শ্বেতাঙ্গরা পরস্পরকে বিয়ে করে। যদিও ইউরোপ ও আমেরিকায় মিশ্র-বর্ণ বিয়ে ঘটে কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের প্রধান ধারা হচ্ছে বর্ণভিত্তিক, অর্থাৎ অন্তর্গোত্রীয়।
বিয়ের ধরন অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয় বিয়ের ধরন অধ্যায়ের সারাংশ – যা বিয়ের ধরন এর অর্ন্তভুক্ত, নৃবিজ্ঞানীরা চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে বিয়ে -ব্যবস্থার শ্রেণীকরণ করেছেন: বিবাহ সঙ্গী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোত্রের গুরুত্ব, পতি-পত্নী সংখ্যা, পতি কিংবা পত্নীর ভাই/বোন বিবাহ সঙ্গী হতে পারে কি না, এবং বিবাহে মূল্যবান সামগ্রীর আদান-প্রদান। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, অপাশ্চাত্য সমাজগুলোর ভিন্নতা সত্ত্বেও বিয়ের বন্ধন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধন স্থাপন করে।
পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য সমাজের ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থায়, বিয়ে হচ্ছে দুই ব্যক্তির মাঝে সম্পর্ক স্থাপন। তবে, মাথায় রাখা জরুরী যে, পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিষ্ঠানাদি ও সংস্কৃতির প্রসার (ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে, উপনিবেশ-উত্তর সময়ে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে) অপাশ্চাত্যের সমাজে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তন বিয়ের সম্পর্ককে পুনর্গঠিত করেছে।
আরও দেখুনঃ