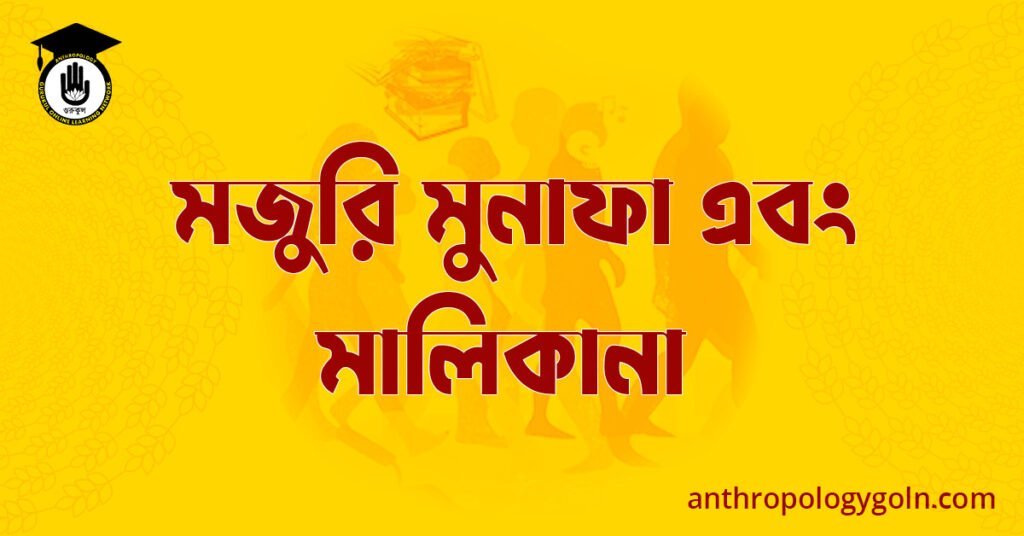আজকের আলোচনার বিষয় মজুরি মুনাফা এবং মালিকানা – যা শ্রেণী ও জাতিবর্ণ স্তরবিভাজ এর অর্ন্তভুক্ত, শ্রেণীর সঙ্গে এই ধারণাগুলো খুবই সম্পর্কিত। আগেই বলেছি যে সম্পদশালী শ্রেণী অনায়াসে সম্পদহীন শ্রেণীর শ্রম খরিদ করে নিতে পারে। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে সকল কিছু উৎপাদন হবার জন্যই শ্রম প্রয়োজন পড়ে। আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে অনেক সমাজে উৎপাদন হয় সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, সকলের শ্রমে। সেই রকম ব্যবস্থায় যে উৎপাদন হয় তার বিশেষ কোন মালিকানা থাকে না। যে কারো ভোগদখলের জন্য সেই সামগ্রীর ব্যবহার সম্ভব হয়। এভাবে উৎপাদনের শরীকী ব্যবস্থা টিকে থাকে।
আবার ভোগের ক্ষেত্রেও শরীকী। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবসার উৎপাদনের প্রক্রিয়া একেবারেই ভিন্ন। এখানে কোন দ্রব্যের উপর মালিকানা আছে। অর্থাৎ উৎপাদিত সকল দ্রব্যেরই দাবীদার থাকেন। আধুনিক সমাজে এই দাবীদারের দাবীকে আইনও সমর্থন করে। সম্পদশালী শ্ৰেণী যখন শ্রমিককে শ্রমের একটা মজুরি দিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ উৎপাদিত দ্রব্যটির মালিকানা তার হয়ে যায়। সেই দ্রব্যটি আর সেই মজুর দাবী করতে পারেন না। এই প্রক্রিয়ায় সম্পদশালী শ্রেণীর হাতে আরও সম্পদ জমতে থাকে । বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করা যায়।
মজুরি মুনাফা এবং মালিকানা
এখানে শ্রমের প্রসঙ্গটাকে আবার ভাবা দরকার। আমরা এমন একটা কিছুর কথা ভাবতে পারি না যার পিছনে কোন শ্রমিকের শ্রম নেই। একটা আলপিন থেকে শুরু করে বড় বড় ইমারত পর্যন্ত সকল কিছু। এখন শ্রমিকের মজুরি দিয়ে দেবার পর সেই দ্রব্যটি মালিকের হয়ে যায় যিনি শ্রমের একটা মজুরি দিয়েছেন। এই দ্রব্যটি তখন খোলা বাজারে বিক্রি করে মালিক দ্রব্যটির দাম পাবেন। দ্রব্যটির দাম তিনি যা মজুরি দিয়েছেন তার থেকে ঢের ঢের বেশি। এই বাড়তি যে টাকা তিনি লাভ করলেন এটাই তার মুনাফা। মালিকের যত উৎপাদন হতে থাকবে ততই তাঁর মুনাফা।
অবশ্যই বিক্রি হতে হবে। একদিকে মালিকের যত উৎপাদন ততই মুনাফা বা লাভ। অন্যদিকে, শ্রমিকের ততই ক্ষতি। কারণ ঐ দ্রব্যটা উৎপাদন করবার জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন ছিল তা তিনি দিয়েছেন, কিন্তু সেই শ্রমের মজুরি দিয়ে ঐ দ্রব্যটা কেনার আর কোন উপায় নেই তাঁর। ঐটার দাম এখন তাঁর প্রাপ্য মজুরির থেকে বহু পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। তাহলে চিন্তা করলে বোঝা যায় প্রত্যেকটা জিনিস উৎপাদন করা বা বানাবার সাথে সাথেই সেই জিনিসের সঙ্গে শ্রমিকের দূরত্ব বাড়তে থাকে। মানে সেটার খদ্দের থাকা তখন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ।
প্রত্যেকটা দ্রব্যের পেছনে যেমন শ্রমিক আছেন, তেমনি মালিকও আছেন। এভাবে সমাজে দুই শ্রেণীর বৈষম্য বাড়ছেই। এটা সত্যি যে মালিকের কাঁচামাল খরিদ করতে হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এই একই চক্র। একটা পর্যায়ে সকল কাঁচামালই প্রকৃতিতে ছিল। ফলে দ্রব্যের উপর থেকে শ্রমিকের দাবী হারানোর ব্যাপারটাকে সমর্থন করবার মত তেমন যুক্তি থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে শ্রমিক শ্রম দিয়ে আরো নিগামী অবস্থায় চলে যাচ্ছেন।
অন্যদিকে মালিক কোন শ্রম না দিয়ে আরো ঊর্দ্ধগামী অবস্থা অর্জন করছেন। উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্কের কারণে ধনী গরিব শ্রেণীর নাম কখনো কখনো বলা হয় – মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ককে শোষণের সম্পর্ক বলা হয়। কারণ শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়েই মালিক শ্রেণীর মুনাফা হতে থাকে।
দরিদ্র শ্রেণীর মানুষজনের উপর নানা ধরনের নির্যাতনের এটা একটা দিক মাত্র। এই যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে শ্রমিকেরা বারংবার আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁদের জীবনে এখন পর্যন্ত খুব একটা বদল আসেনি – সেটা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এখানে এই আলোচনাটি একভাবে খুব সহজভাবে করা হয়েছে। সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের বিষয়গুলো এর থেকে ঢের কঠিন। যেমন এই আলোচনায় একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তা হচ্ছে: মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহলে কোথায় গেল? তাছাড়া একটা যুক্তির সমস্যাও দেখা দেয়। সেটা হ’ল: সমাজে সকল মানুষ স্পষ্টভাবে মালিক কিংবা শ্রমিক-এর কাতারে পড়েন কিনা ।
আরও দেখুনঃ