আজকের আলোচনার বিষয় মহাপ্রাণবাদ ও মানা – সর্বপ্রাণবাদ- মহাপ্রাণবাদ ও মানা এর অর্ন্তভুক্ত, ধর্মের উৎপত্তি ও মৌলিক রূপ সম্পর্কে টায়লর-প্রদত্ত ব্যাখ্যার বিকল্প অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবার্ট ম্যারেট নিয়ে আসেন animatism-এর ধারণা, যার বাংলা করা হয়েছে ‘মহাপ্রাণবাদ’।
মহাপ্রাণবাদ ও মানা
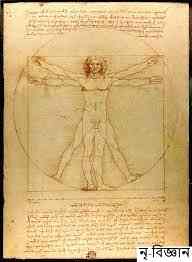
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উনিশ শতকের বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞানীরা ধর্মের আদিরূপ ও উৎপত্তি সম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা এ ধরনের কিছু ধারণা ও তত্ত্বের সাথে পরিচিত হব। বিবর্তনবাদীদের দৃষ্টিতে তথাকথিত ‘আদিম’ সমাজসমূহের অবস্থান ছিল বিবর্তনের নিম্নতর ধাপসমূহে, ফলে সে হিসাবে চিহ্নিত সমাজসমূহের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের প্রতি তাদের নজর বেশী মাত্রায় কেন্দ্রীভূত ছিল।
ধর্মের উৎপত্তি, আদিরূপ বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিবর্তনবাদীদের প্রণীত বিভিন্ন তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা পরবর্তীতে আর ব্যাপকভাবে অনুসৃত না হলেও তাদের ব্যবহৃত কিছু মৌলিক প্রত্যয় এখনো নৃবিজ্ঞানে চালু রয়েছে। এরকমই দুটি প্রত্যয় হল ‘সর্বপ্রাণবাদ’ (animism) ও ‘মহাপ্রাণবাদ’ (animatism)। নীচে এগুলির উপর আলোচনা করা হল।
ধর্ম হচ্ছে আত্মা-রূপীয় বিভিন্ন সত্তায় বিশ্বাস, টায়লরের এই সংজ্ঞাকে ম্যারেট অতি সংকীর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অনেক ধর্মেই এমন কিছু শক্তি বা ক্ষমতার ব্যাপারে বিশ্বাস দেখা যায় যেগুলিকে সরাসরি কোন অতিপ্রাকৃত সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখা হয় না। বিভিন্ন কিছুর মধ্যে এ ধরনের বিশেষ শক্তির উপস্থিতি বা প্রভাব সংক্রান্ত বিশ্বাসকে ‘সর্বপ্রাণবাদ’ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, মেলানেশীয় ও পলিনেশীয় সমাজসমূহে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ক্ষমতার ব্যাপারে ব্যাপক বিশ্বাস দেখা যায়। এই শক্তিকে একাধিক মেলানেশীয় ভাষায় “মানা’ (mana) বলা হয়, যে শব্দটা নৃবিজ্ঞানীরা অনুরূপ সকল ধারণাকে সাধারণভাবে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করে (দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কৃষ্ণকায় আদিবাসী-অধ্যুষিত বেশ কিছু দ্বীপপুঞ্জকে একত্রে মেলানেশিয়া বলা হয়, যার অন্তর্গত রয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি প্রভৃতি। অন্যদিকে হাওয়াইসহ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য আরো কিছু দ্বীপপুঞ্জকে একত্রে পলিনেশিয়া বলা হয়)।

‘মানা” বলতে এমন একটা বিশেষ শক্তি বা গুণকে বোঝায় যা বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মেলানেশীয় ও পলিনেশীয় বিশ্বাস অনুসারে এই গুণের অধিকারী ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি হয়ত মাছ ধরার কাজে সবসময় বা প্রায়ই বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। সেক্ষেত্রে বলা হয় যে, সে অন্যদের চেয়ে বেশী ‘মানা’র অধিকারী। অথবা, কোন জমিতে খুব ভাল ফসল হওয়ার কারণ হিসাবে হয়ত ‘মানা’-গুণ সম্পন্ন বিশেষ কোন বস্তু, যেমন অসাধারণ আকৃতির কোন পাথরের উপস্থিতিকে বিবেচনা করা হয়।
“মানা’র পেছনে কোন দৈবসত্তা বা ইশ্বররূপী কারো হাত রয়েছে, এমনটা ভাবা হয় না। বিশেষ বিশেষ উপায়ে, নির্দিষ্ট কিছু জাদুধর্মী আচার-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে, ‘মানা’ অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। ম্যারেট মনে করেন যে, আত্মা, ভূত-প্রেত, দেব-দেবী প্রভৃতি ধারণার আবির্ভাবের আগেই ‘মানা’ জাতীয় শক্তির উপস্থিতি ও ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মেছিল।
এ ধরনের বিশ্বাসের পেছনে বিশেষ কোন যুক্তি কাজ করে না, যতটা যুক্তি হয়ত আত্মা বা ভূত-প্রেত সংক্রান্ত বিশ্বাসের বেলায় দেখা যায়। ‘একেশ্বরবাদ” যদি হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের সবচাইতে বিবর্তিত ও যুক্তিসিদ্ধ রূপ, তাহলে ‘মহাপ্রাণবাদ’ হবে এর আদিমতম রূপ, অন্ততঃ ম্যারেটের মতে। অবশ্য সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস শুধুমাত্র তথাকথিত আদিম মানুষদের মধ্যেই সীমিত নয়।

একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, “মানা’র মত ধারণা আমাদের কাছেও একেবারে অপরিচিত নয়। যেমন, বিশেষ কোন ব্যাট হাতে বা বিশেষ কোন জার্সি গায়ে খেললে ভাল রান তোলা বা বেশী উইকেট পাওয়া সম্ভব, এ কথা যদি কোন ক্রিকেটার বিশ্বাস করে বাস্তবে যে ধরনের অনেক উদাহরণ আমরা দেখি – তা হবে অনেকটা ‘মানা” সম্পর্কে মেলানেশীয় বিশ্বাসের অনুরূপ।
আরও দেখুনঃ
