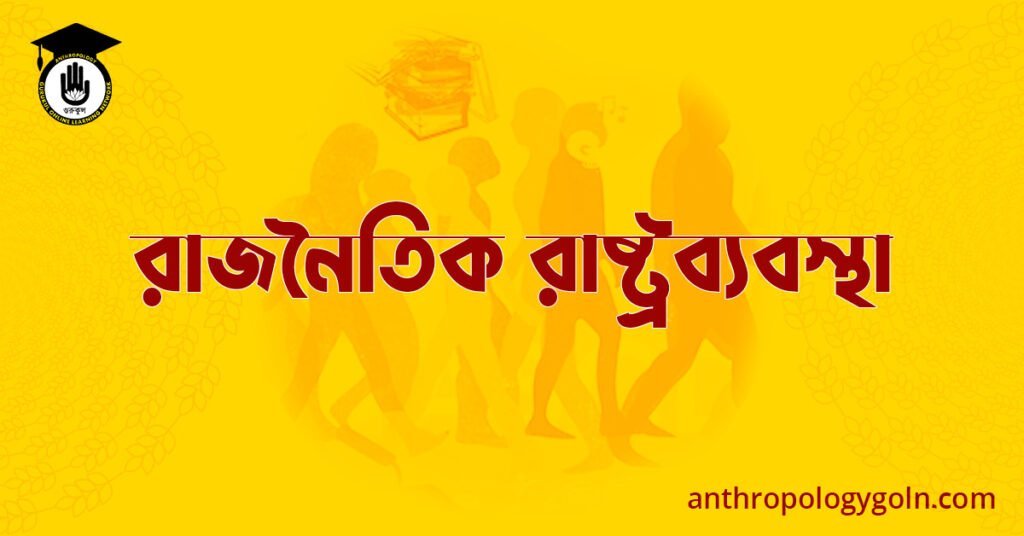আজকের আলোচনা রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে। আমরা যে সময়কালে জন্মেছি সেই সময়কালে রাষ্ট্রের অর্থ দুনিয়া ব্যাপী বিস্তার হয়েছে। রাষ্ট্র ছাড়া কোন সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করাই অসম্ভব এখন । কেবল তাই নয়, সকল সমাজে রাষ্ট্রের চেহারা একই রকম দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো যখন দুনিয়া জুড়ে বাণিজ্য করতে বের হয়েছে। এর মানে এই নয় যে বাইরের শক্তি আসবার আগে পৃথিবীর সকল স্থানে একই রকম অবস্থা ছিল। বরং, তখন এক এক অঞ্চলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেহারা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সেটা ভাল না মন্দ তা ভিন্ন প্রসঙ্গ।
বোঝার বিষয় হ’ল: আধুনিক কালে সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা কাঠামোর দিক থেকেও, আবার সাধারণ মানুষের চিন্তা- ভাবনার দিক থেকেও। আর এটা ঘটেছে ইউরোপীয় শক্তির বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থেকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের চারটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:
রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা
ক) রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষমতার একটা কেন্দ্রীভূত এবং ক্রমোচ্চ ব্যবস্থা। অর্থাৎ পূর্বতন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে নানা প্রকার শিথিলতা ছিল, এবং ক্ষমতা কোন নির্দিষ্ট একটা জায়গায় জড়ো ছিল না, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা জড়ো হয়েছে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানে। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চীফডমও বটে। তবে রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে একেবারে চূড়ান্ত উদাহরণ।
আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানাবিধভাবে ক্ষমতার নানা স্তর থাকে। কখনো সেটা সরাসরি নানান দপ্তরের মাধ্যমে, কখনো অনানুষ্ঠানিকভাবে। আর সম্পদের ভিত্তিতে ক্ষমতা এখানে নিশ্চিত হয়েছে। যাবতীয় সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম। কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেমন: সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান – কিউবা ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। কিংবা সম্পদ বলতে খুব সামান্য জিনিসই আবিষ্কার হয়েছিল।
খ) রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পদশালীর অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। ক্ষমতা এবং মর্যাদা উভয়েই সম্পদের পাশাপাশি বেড়ে যায় এখানে। এর মানে এই নয় যে অন্য কোন উপায়ে এখানে মর্যাদাবান হবার পথ নেই। কিন্তু সম্পদ যেহেতু ব্যক্তির হাতেই থাকতে পারে – তাই সম্পদের বাড়তি সুবিধা ব্যক্তির পক্ষে নেয়া সম্ভব হয় এই ব্যবস্থায়। ফলে ব্যক্তিগত মনোভাব বেড়ে যায়। আগের ব্যবস্থায় যেখানে সামাজিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব ছিল অধিক, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।
গ) রাষ্ট্রে শক্তি বা বল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং অনেক শক্তিশালীভাবে কাজ করে। সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের হাতে নানান শক্তি সঞ্চিত থাকে। রাষ্ট্র সেটা প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করতে পারে। সাধারণভাবে ভাবা হয় কোন অশুভ শক্তির বিপক্ষে এই সব বাহিনী কাজ করে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাস বলে যে এই সব শক্তি মূলত ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ মানুষের বিপক্ষে। উপরন্তু, নানাবিধ আধুনিক অস্ত্রের আবিষ্কার রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে পোক্ত করেছে।
ঘ) রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় লিখিত আইনের শক্তি বিশাল। আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে যাবতীয় কথ্য ঐতিহ্য বিলীন এবং গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। আগেকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক নিয়ম-কানুনের উৎস ছিল মানুষের বিচার বুদ্ধি এবং কথ্য অভিজ্ঞতা। আধুনিক রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম লিখিত আইন দ্বারা পোক্ত করা হয়।
সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর পক্ষে হত্যাযজ্ঞ করাও সম্ভব হয়। আর তা আইনের দ্বারা অনুমোদন পায়। লেখ্য ব্যবস্থার শক্তি বুঝতে চাইলে আর একটি বিষয় উলেখ করা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রের সীমারেখা খুবই গুরুত্ব বহন করে। বহু দেশের মধ্যে এই সীমারেখার সঠিক মাপ নিয়েই যুদ্ধ হবার নজির আছে। আর এই সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় ভূগোলবিদের অঙ্কনের মাধ্যমে। কখনো কখনো রাষ্ট্র বলতে আমরা ঐ আকা ছবিটাই মনে করতে পারি কেবল।
রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি:
রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বা রাজগতি বা রাজবুদ্ধি হলো হল দলীয় বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, উদাহরণস্বরুপ সম্পদের বণ্টন হল এমন একটি কর্মকাণ্ড। রাজনীতি এ্যাকাডেমিক অধ্যয়নকে রাজনীতিবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ হলো রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করা।
রাজনীতি একটি বহুমুখী শব্দ। এটি আপোষের ও অহিংস রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে ইতিবাচক অর্থে, অথবা সরকার বিষয়ক বিজ্ঞান বা কলা হিসেবে বিশদভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি এটি প্রায়শই একটি নেতিবাচক অর্থও বহন করে। উদাহরণস্বরুপ, উচ্ছেদবাদী উইনডেল ফিলিপস ঘোষণা দেন “আমরা রাজনৈতিক চাল চালি না, দাসপ্রথার বিরোধিতা নিয়ে হাসি তামাশা করা আমাদের স্বভাবে নেই।” রাজনীতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন পরিসরে মৌলিকভাবে এবিষয় নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে, যেমন এটি কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, বিস্তৃতভাবে নাকি সীমিতভাবে, রাজকীয়ভাবে নাকি সাধারণভাবে, এবং কোনটি এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীঃ সংঘাত নাকি সমবায়।
রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যার মধ্যে আছে কারও নিজস্ব রাজনৈতিক অভিমত মানুষের মাঝে প্রচার করা, অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময়, আইন প্রনয়ন, এবং বলপ্রয়োগের চর্চা করা, যার মধ্যে আছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা লড়াই। সামাজিক বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত পরিসরে রাজনীতির চর্চা করা হয়, ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থাসমূহের গোত্র ও গোষ্ঠী থেকে শুরু করে আধুনিক স্থানীয় সরকার, ব্যবসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সার্বভৌম রাষ্ট্র, এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত। আধুনিক জাতি রাষ্ট্রগুলোতে, মানুষ প্রায়ই নিজস্ব মতবাদ তুলে ধরতে রাজনৈতিক দল গঠন করে। কোন দলের সদস্যগণ প্রায়শই বিভিন্ন বিষয়ে সহাবস্থানের ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করে এবং আইনের একই পরিবর্তন ও একই নেতার প্রতি সমর্থনে সহমত হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন হল সাধারণত বিভিন্ন দলের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা।
রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয় রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অধ্যায়ের সারাংশ – যা রাজনৈতিক- রাষ্ট্রব্যবস্থা এর অর্ন্তভুক্ত, অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতার একটা কেন্দ্রীভূত এবং ক্রমোচ্চ ব্যবস্থা।
রাষ্ট্রের অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এখানে সম্পদশালীর অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত থাকে, বল বা শক্তি প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় লিখিত আইনের শক্তি ব্যাপক। সম্পদের ভিত্তিতে ভেদাভেদ বা শ্রেণী এখানে খুবই শক্তিশালী ব্যবস্থা।
ভোগ্যপণ্য, আরাম-আয়েশ এবং অবকাশ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষজনই কেবল পেতে পারেন। এসব সুবিধা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনে সকল ধরনের বলপ্রয়োগ করে থাকে। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের পাশাপাশি রাষ্ট্রে নানান রূপে এবং পরিধিতে ক্ষমতা-সম্পর্ক জন্ম নেয় ।
আরও পড়ুন:
রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি:
রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বা রাজগতি বা রাজবুদ্ধি হলো হল দলীয় বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, উদাহরণস্বরুপ সম্পদের বণ্টন হল এমন একটি কর্মকাণ্ড। রাজনীতি এ্যাকাডেমিক অধ্যয়নকে রাজনীতিবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ হলো রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করা।
রাজনীতি একটি বহুমুখী শব্দ। এটি আপোষের ও অহিংস রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে ইতিবাচক অর্থে, অথবা সরকার বিষয়ক বিজ্ঞান বা কলা হিসেবে বিশদভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি এটি প্রায়শই একটি নেতিবাচক অর্থও বহন করে। উদাহরণস্বরুপ, উচ্ছেদবাদী উইনডেল ফিলিপস ঘোষণা দেন “আমরা রাজনৈতিক চাল চালি না, দাসপ্রথার বিরোধিতা নিয়ে হাসি তামাশা করা আমাদের স্বভাবে নেই।”
রাজনীতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন পরিসরে মৌলিকভাবে এবিষয় নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে, যেমন এটি কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, বিস্তৃতভাবে নাকি সীমিতভাবে, রাজকীয়ভাবে নাকি সাধারণভাবে, এবং কোনটি এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীঃ সংঘাত নাকি সমবায়।
রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যার মধ্যে আছে কারও নিজস্ব রাজনৈতিক অভিমত মানুষের মাঝে প্রচার করা, অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময়, আইন প্রনয়ন, এবং বলপ্রয়োগের চর্চা করা, যার মধ্যে আছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা লড়াই।
সামাজিক বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত পরিসরে রাজনীতির চর্চা করা হয়, ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থাসমূহের গোত্র ও গোষ্ঠী থেকে শুরু করে আধুনিক স্থানীয় সরকার, ব্যবসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সার্বভৌম রাষ্ট্র, এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত। আধুনিক জাতি রাষ্ট্রগুলোতে, মানুষ প্রায়ই নিজস্ব মতবাদ তুলে ধরতে রাজনৈতিক দল গঠন করে। কোন দলের সদস্যগণ প্রায়শই বিভিন্ন বিষয়ে সহাবস্থানের ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করে এবং আইনের একই পরিবর্তন ও একই নেতার প্রতি সমর্থনে সহমত হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন হল সাধারণত বিভিন্ন দলের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা।
রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল কোন কাঠামো যা কোন সমাজের মধ্যকার গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক পদ্ধতিসমূহকে সংজ্ঞায়িত করে। রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় প্রাথমিক প্রাচীন যুগে, যেখানে প্লেটোর রিপাবলিক, এরিস্টটলের রাজনীতি, চাণক্যর অর্থশাস্ত্র ও চাণক্য নীতি (খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী), এবং কনফুসিয়াসের লেখার ন্যায় দিগন্ত উন্মোচনকারী কাজগুলো পাওয়া যায়।
রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদ:
রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদ বা বস্তুতন্ত্রবাদ বা রাজনৈতিক বস্তুতন্ত্রবাদ বা রাজনৈতিক বাস্তববাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিদ্যার একটি বিশেষ শাখা। এটি কোন রাষ্ট্রের এমন বিশেষ রাজনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা দেয় যে আচরণের ফলে রাষ্ট্র নৈতিকতা, আদর্শ, সামাজিক পূণর্গঠন ইত্যাদি বিষয়াবলীকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র ও যেকোন উপায়ে জাতীয় স্বার্থ কায়েম ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নীতি নির্ধারণ করে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় বস্তুতন্ত্রবাদ ও ক্ষমতার রাজনীতিকে ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
বস্তুতন্ত্রবাদের মতে- আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যত নৈরাজ্যবাদমূলক; প্রতিটি রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোকে প্রাধান্য দেয় এবং পদক্ষেপগুলো রাষ্ট্রের স্বতঃস্ফুর্ততা ও গতিময়তার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়; রাষ্ট্রের এরূপ নীতিমালার জন্য মানবকূল পরস্পরের প্রতি সাংঘর্ষিক মনোবৃত্তি ধারণ করে; ব্যক্তি পর্যায়ের নৈতিক আদর্শগুলোর দ্বারা রাষ্ট্রসমূহের কূটনীতিকে মূল্যায়ন করা যায় না কেননা রাষ্ট্রসমূহ যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন তা তারা ব্যক্তি হিসেবে নয় বরং একেকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে হয়; রাজনৈতিক নীতিমালার ভিত্তি যতটা না আদর্শ, তার চেয়ে বেশি স্বার্থ ও ক্ষমতা; টিকে থাকার লড়াই ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র এককভাবে দায়ী।
রাজনৈতিক বাস্তববাদ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বসমূহের মধ্যে একটি চিন্তাধারা, যা প্রারম্ভিক আধুনিক ইউরোপের বাস্তব-রাজনৈতিক ধারণার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়েছিল। এই চিন্তাধারা মূলত এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে যে, বিশ্ব রাজনীতি চূড়ান্তভাবে সবসময় এবং অপরিহার্যভাবে ক্ষমতান্বেষণকারীদের দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্র। এই প্রত্যাখ্যান-অযোগ্য দ্বন্দ্বের উৎস্য কী – সেই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক বাস্তববাদীদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ধ্রুপদী বাস্তববাদীগণ মনে করেন এর উৎস্য মানব প্রকৃতি বা প্রবৃত্তিতেই নিহিত।
নব্যবাস্তববাদীগণ নৈরাজ্যময় রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোকে এই দ্বন্দ্বের উৎস্য বলে মনে করেন। এদিকে নব্য-ধ্রুপদী বাস্তববাদীগণ এর উৎস্য হল মানব প্রকৃতি ও নৈরাজ্যময় রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামো দুটোই, ও সেই সাথে কিছু নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় আভ্যন্তরীন চলক। এছাড়াও বিশ্ব রাজনীতির পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রগুলোকে কিরকম কাজ করা উচিত তা নিয়েও নব্যবাস্তববাদীরা দুইভাগে বিভক্ত: প্রতিরক্ষামূলক বাস্তববাদ ও আক্রমণাত্মক বাস্তববাদ। বাস্তববাদীরা দাবি করেন, প্রাচীন যুগের থুসিডাইডিসের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত রাজনীতির ইতিহাসের সকল সময়ে রাজনৈতিক বাস্তববাদের ঐতিহ্য বজায় রয়েছে।
আরও দেখুনঃ