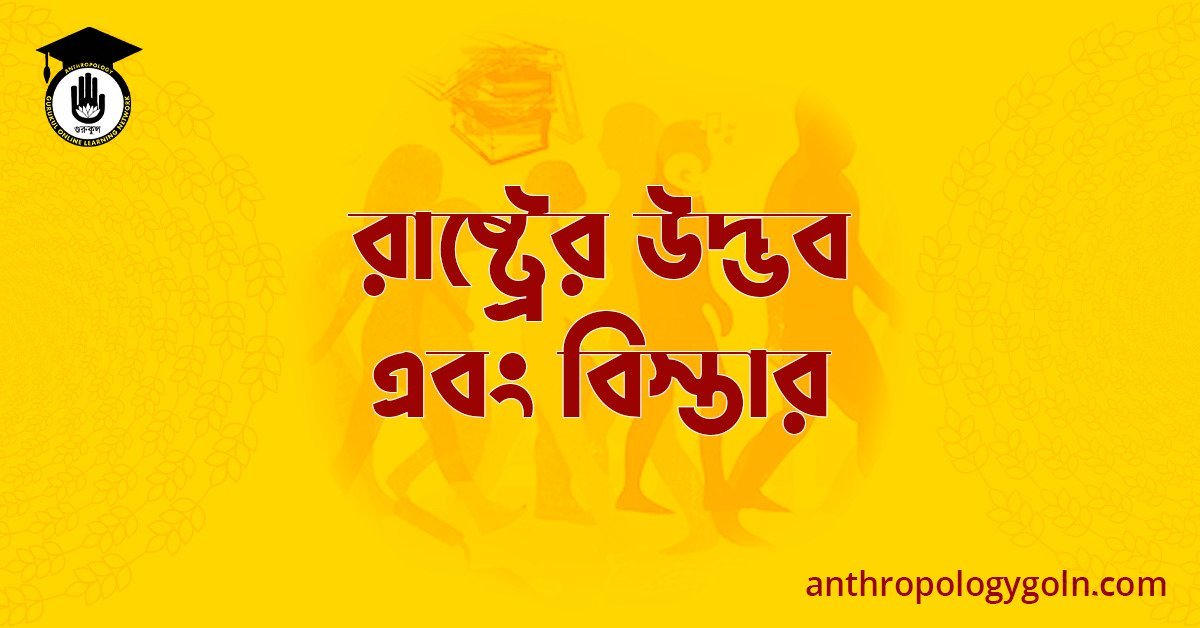যা রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এর অর্ন্তভুক্ত, রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে লেখাপড়ার জগতে বিতর্ক আছে। বিতর্কটা বহুদিন ধরেই চলছে। বিতর্কটার প্রেক্ষাপট হচ্ছে রাষ্ট্রের ভূমিকা। এর মানে হ’ল রাষ্ট্র মানুষের জন্য কল্যাণকর কিনা সেই তর্কের উপরেই ব্যাখ্যাগুলো দাঁড়িয়ে আছে।
অনেকেই মনে করেন রাষ্ট্র মানুষের উপকার করে থাকে, তাদের সেবা দিয়ে থাকে। অন্যদের যুক্তি হচ্ছে: রাষ্ট্র প্রধানত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করে এবং ধন-সম্পদশালীদের সম্পত্তি পাহারা দিয়ে থাকে।
রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং বিস্তার
এই দুই অবস্থান থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে বড়- সড় দুইটা ঘাঁটি লেখাপড়ার জগতে আছে। একদিকে, কোন কোন পন্ডিত ব্যাখ্যা দেন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, চুক্তির মাধ্যমে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রকে যাঁরা দমনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে থাকেন তাঁদের ব্যাখ্যা হচ্ছে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে সমাজের শক্তিশালীদের সংঘ হিসেবে।
নৃবিজ্ঞান এবং প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে বেশ কিছু তাত্ত্বিক এর থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। তাঁরা প্রযুক্তি এবং পরিবেশকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সেটা শুরুতে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় হলেও পরবর্তীতে নানারকম সমালোচনার মধ্যে পড়ে। সমালোচকগণ এই ব্যাখ্যার অসারতাগুলো চিহ্নিত করেন। এই মুহূর্তে নৃবিজ্ঞানে চলমান বিতর্কগুলোকে বিবেচনা করলে মোটামুটি তিন ধরনের চিন্তাধারা পাওয়া যায়।
প্রথমটি প্রযুক্তি ও পরিবেশ ধারা। এই ধারার চিন্তাবিদদের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে মূলত পরিবেশ এবং প্রযুক্তির বদলের কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। পরিবেশের দিক থেকে চিন্তা করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জনসংখ্যা বাড়বার কারণে মানুষের পক্ষে ছোট দলের সমাজ ব্যবস্থাতে থাকা সম্ভব হয়নি।
প্রযুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে, কারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেড়ে উঠেছে কৃষিভিত্তিক সমাজের সাথে সাথে। তাই কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা হ’ল কৃষির উন্নতির সাথে সাথে উৎপাদন বেড়ে গেল। একই সঙ্গে তা জটিল ব্যবস্থারও হয়ে গেছে। ফলে সমাজের ব্যবস্থাপনা করা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
সেচ বা এই ধরনের সুযোগ কৃষি কাজে সরবরাহ করবার জন্যও সাংগঠনিক কাঠামোর দরকার পড়েছিল। রাষ্ট্রের মত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এইসব তাগিদ থেকেই। তাঁদের ব্যাখ্যার পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো হয়ে থাকে। তা হচ্ছে: পৃথিবীর আদি সভ্যতার সবগুলিই কোন না কোন নদীর পাশে।
যেমন: সিন্ধু সভ্যতা সিন্ধু নদের পাড়ে। মিশর সভ্যতা নীল নদের পাড়ে, আর চীনের সভ্যতা হোয়াং হো’র পাড়ে অবস্থিত। এর মাধ্যমে বোঝা যায় সেচ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে। এই ধারার চিন্তা-ভাবনা থেকে আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না।
দ্বিতীয় ধারার নাম দেয়া যেতে পারে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র (political economy) ধারা। এই ধারাতে ভাবা হয়ে থাকে সমাজে সম্পদের ধরন বদলাবার সাথে সাথে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবার একটা দল তৈরি হয়েছে। সমাজে এভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানা তৈরি হয়েছে। সম্পদ জড়ো করা এই দলকে ধনী শ্ৰেণী বা মালিক শ্ৰেণী বলা হয়ে থাকে।
কিন্তু অন্য শ্রেণী শ্রম দেয় এবং সেই সম্পদ তৈরি করে থাকে। আপনারা অর্থনৈতিক সংগঠন অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা দেখেছেন। সম্পদ যখন কোন শ্রেণীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে তখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করবার। এ ছাড়াও বঞ্চিত শ্রেণী যেহেতু পরিশ্রম করে সেগুলো উৎপাদন করে, তারাও মালিকদের সম্পত্তিকে দখল করতে চাইতে পারে।

ফলে উঁচু শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিল। আর তারা নিজেদের এই আয়েশী উৎপাদন না করা জীবন রক্ষা করতেও চাইল। এভাবে সমাজে প্রহরী রাখার ব্যবস্থা চালু হ’ল। এই প্রহরী দলই সামরিক বাহিনীর সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণীকে চাপে রাখা এবং দমন করে রেখে নিজেদের সুবিধা বজায় রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।
দমন করবার সেই প্রাথমিক ব্যবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে বহু দপ্তর তৈরি হয়েছে। এই চিন্তাধারা থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে অন্য রাষ্ট্রকে কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করে। ইউরোপে শিল্পের বিকাশের পর মালিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর সম্পদ জড়ো হয়েছে। কৃষির পর শিল্প আসার পর মুনাফা বা লাভের নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়।
মুনাফার লোভে নতুন দেশ থেকে কাঁচামাল পাবার জন্য আক্রমণ করার নজির আছে। তাছাড়া আছে কোন উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিয়ে লড়াই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এর ভাল উদাহরণ। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেছনে উগ্র জাতীয়তাবাদ কাজ করেছে, সেই সাথে আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারও আছে। এই ধারার চিন্তুকগণ জাতীয়তাবাদকেও উচ্চ শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত করে দেখেছেন।
তৃতীয় ধারাকে আমরা ঐতিহাসিক ধারা বলতে পারি। এই ধারার প্রধান আগ্রহ ঔপনিবেশিক ইতিহাস নিয়ে। উপনিবেশ গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। এর মাধ্যমে পৃথিবী ব্যাপী, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন। ঔপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে জড়ো করতে চেয়েছে।
এর জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি তারা অর্জন করেছিল। উপনিবেশ স্থাপন করবার আগের সময়কালে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছে। বাস্তবে এই পার্থক্যটাই অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বড় পার্থক্য ছিল। উপনিবেশ স্থাপনার মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ জড়ো হয়েছে ইউরোপে।
শিল্প উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল পেয়েছে তারা উপনিবেশ থেকে। আর এভাবে উপনিবেশের সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই দুর্বল কাঠামোর উপরেই ইউরোপের দর্শন এবং চিন্তা-ভাবনা সমেত আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সকল এলাকা থেকে উপনিবেশ সরে গেছে তখন এই রাষ্ট্র কাঠামো থেকে গেছে।
তখন অন্য দেশগুলো হতে বাণিজ্যের মাধ্যমে সুবিধা বজায় রেখেছে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যেহেতু শিল্পভিত্তিক উৎপাদনের চাহিদা তখন এইসব রাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে। ফলে একটা দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পাঠ করা দরকার বলে এই ধারা যুক্তি দেখায়।