আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় রোমক সভ্যতা। রোম (Rome) নগরী, কিম্বদন্তী অনুযায়ী এটি ৭৫৩ খ্রীঃপূঃ ইটালীর তিবর (টাইবার) নদীর তীরস্থ বাম পার্শ্ববর্তী টিলাগুলোর উপরে, মোহনা থেকে ২৫ কিমি দূরে সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এটির সাম্রাজ্য ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়ে উত্তর দিকে ইউরোপ পর্যন্ত দূর-প্রাচ্যে বিস্তারলাভ করেছিল। আর শতাব্দীর পর শতাব্দী এটি সভ্য জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।
রোমক সভ্যতা
কিম্বদন্তী রয়েছে, ল্যাটিন ভাষাভাষী রাজ্যের কোন একটির রাজা নিজের এক আত্মীয়ার দু‘ই শিশু পুত্র সন্তান রোমলুস ও রেমুসকে তিবর নদী গর্ভে বিসর্জন দেবার হুকুম জারী করেন। কেননা, তার ভয় ছিল এরা বড় হয়ে তার সিংহাসন কেড়ে নেবে। বিসর্জন দেবার পরে তিবর নদীতে বন্যা আসায় যে ঝুড়িতে করে শিশু দু‘টিকে পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়, তা বন্যার পানিতে ভেসে গিয়ে এক গাছের ডালে আঁটকে যায়। এভাবে শিশু দু‘টির প্রাণ বাঁচে। তারপর তারা একটি নেকড়ে বাঘের হাতে পড়ে এবং নেকড়ে মায়ের দুধ খেয়েই তারা বড় হচ্ছিল।
পরে এক রাখাল তাদের দেখতে পেয়ে স্বগৃহে নিয়ে এসে দু‘ভাইকে মানুষ করতে থাকে। ভ্রাতৃদ্বয় যথারীতি (গল্প কাহিনীতে যেমন হয়) অমিত বিক্রম যোদ্ধারূপে বড় হয়ে ওঠে। তারপর ঐ রাজার বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ পরিচালনা করে রাজাকে হত্যা করে। অত:পর তারা উভয়ে নগর পত্তন করতে চায়, কিন্তু কোথায় নগর গড়া হবে এবং কে তার পরিচালনার ভার নেবে তাই নিয়ে দু‘ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এই বিবাদে রোমলুস রেমুসকে হত্যা করে।

রোমক সভ্যতা
গ্রীসীয়-সভ্যতা যখন বিকাশের উচ্চস্তরে প্রবেশ করেছে, তখন ভূমধ্যসাগরের মধ্য অঞ্চলে এ্যাপেনাইন উপদ্বীপ তথা ইটালীয় উপদ্বীপকে আশ্রয় করে আরেকটি সভ্যতার উদয় ঘটেছিল। এটাই সুবিখ্যাত রোমক সভ্যতা। গ্রীসীয় উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত এ্যাপেনাইন উপদ্বীপ ইটালি এবং সিসিলি দ্বীপ ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সেতুরূপে বিরাজ করছে।
ইটালীয় উপদ্বীপের মধ্যভাগ দিয়ে তার দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত রয়েছে এ্যাপেনাইন পর্বতশ্রেণী। এ উপদ্বীপ পার্বত্য হলেও গ্রীসের মত দুর্গম নয়। পর্বতের উভয় পাশে, পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অংশে, চাষাবাদ ও পশুপালনের উপযোগী বিস্তৃত উপত্যকা ছিল।

ইটালীয় প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল কাঠ ও ধাতু (বিশেষত তামা ও টিন)।
উপদ্বীপের মধ্যভাগে রয়েছে টাইবার নদী। পাহাড়ে এর উৎপত্তি এবং পশ্চিমাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটা সমুদ্রে পড়েছে। উত্তরে অবস্থিত আস্ পর্বতশ্রেণী এ উপদ্বীপকে উত্তরের শীতল বায়ুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, এর আবহাওয়া তাই উষ্ণ। গ্রীসের চেয়ে এখানে বৃষ্টিপাত বেশি এবং জমিও বেশি উর্বর। দক্ষিণের সিসিলি দ্বীপের আবহাওয়া উষ্ণতর এবং ফসলও সমৃদ্ধতর।

রোমক আদি অধিবাসী
পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, অন্ততপক্ষে উচ্চতর পুরোপলীয় যুগে ইটালিতে লোকবসতি ছিল। এ সময় দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্রোমানিয়ন জাতির সমগোত্রীয় মানুষ এখানে বাস করত। নবোপলীয় যুগে আফ্রিকা, স্পেন ও গল থেকে নতুন জাতির মানুষ এখানে আগমন করে। অতপর ব্রোঞ্জযুগের শুরুতে একাধিক নতুন অভিযান ঘটে। আপস্-এর উত্তরাঞ্চল থেকে ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা এখানে এসে বাস স্থাপন করে।
এ সকল নবাগত কৃষিজীবী পশুপালক গোষ্ঠী ইটালিতে প্রথম ঘোড়া ও ঢাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন করে। এদের সংস্কৃতি ছিল ব্রোঞ্জভিত্তিক, যদিও ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর এরা লোহার ব্যবহার আয়ত্ত করে। এ সকল ইণ্ডো-ইউরোপীয় আক্রমণকারীরাই ছিল রোমকসহ সকল ইটালির জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। জাতিগতভাবে এরা ছিল সম্ভবত গ্রীস আক্রমণকারীদের সাথে সম্পর্কিত।

এ ইণ্ডো-ইউরোপীয়দের একটা প্রধান শাখার নাম ছিল ল্যাটিন; এরা টাইবার নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত সমভূমিতে বাস স্থাপন করেছিল এবং এ সমগ্র অঞ্চলটা ল্যাাটিয়াম নামে পরিচিত হয়েছিল। উক্ত জাতির অন্যান্য শাখা ইটালীয় উপদ্বীপের মধ্যে ও পূর্বাঞ্চলে বাস স্থাপন করে।
সর্বশেষ আরও দুটো নবাগত জাতি ইটালীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশ অধিকার করে।
১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই এটুস্কান জাতি উত্তরাঞ্চলের পো নদীর অববাহিকায় বাস স্থাপন করে এবং তার দক্ষিণাংশে অধিকার বিস্তার করে। তাদের অধিকৃত অঞ্চল এটুরিয়া নামে পরিচিত হয়। গ্রীকরা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে দক্ষিণ ইটলির উপকূলবর্তী অঞ্চলে এং সিসিলির পূর্বাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে।
ব্যাপকসংখ্যক গ্রীক উপনিবেশের উপস্থিতির জন্য এ অঞ্চল একদা ম্যাগনা গ্রীসিয়া বা বৃহত্তর গ্রীস নামে পরিচিত হয়েছিল। গ্রীকরাই প্রথম এ্যাপেনাইন উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের নামকরণ করে ইটালীয়া। কালক্রমে সমগ্র উপদ্বীপটিই এ নামে পরিচিত হয় ।

রোমক ঐতিহ্য
রোমান প্রজাতন্ত্র তথা সাম্রাজের পতনের ইতিহাস এক দীর্ঘস্থায়ী মর্মবেদনার কাহিনী । রোমান সভ্যতার সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করলেই এর পতনের কারণসমূহ অতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। আপাত- দৃষ্টিতে রোমের সভ্যতা যতই বর্ণাঢ্য মনে হোক না কেন এর মননশীলতার জগৎ ছিল নিঃস্ব ও রিক্ততায় পরিপূর্ণ।
সমাজের অধিকাংশ মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে রেখে তাদের ক্রীতদাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে কোনো সভ্যতাই যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, উপরন্তু তা নিজের সঙ্কটকে ডেকে আনে— রোমের ইতিহাস পাঠে আমরা সে সত্যই অবগত হই। বিশাল রোমান সভ্যতা তার সাতশত বছরে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিশেষ কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। শিল্প ও সাহিত্যে তার অগ্রগতি যতখানি হয়েছিল, সে তুলনায় বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সে বিন্দুমাত্র অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়নি।
উপরন্তু গ্রীকদের আবিষ্কৃত কারিগরি জ্ঞান বা বিজ্ঞানকে সে কাজে লাগায়নি। এর কারণ আর কিছুই নয়, রোমান উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি এর ব্যর্থতার মূল কারণ। অবক্ষয়িত, অপ্রচলিত, বাতিল হয়ে যাওয়া দাসপ্রথাকে জোর করে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে সে শুধু সভ্যতার সংকটই সৃষ্টি করল না, তার সমস্ত শক্তি আর অহমিকা নিয়ে ভেঙে পড়ল । গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল নতুন পাথরের যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগের কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে কেন্দ্র করে।
কিন্তু এই তিনটি যুগের মিলিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের সুফলগুলি গ্রীকরা পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে পারেনি তাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও ভাবাদর্শের উপস্থিতির দরুন। ব্রোঞ্জযুগের শেষ পর্বে যে উৎপাদন সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল লৌহযুগের আবির্ভাবে।
কিন্তু লৌহযুগের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কার ও তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল ক্রীতদাসপ্রথা বাতিল করে একটি মুক্ত সমাজ তৈরি করা, যে সমাজের মুক্ত মানুষ তার স্বাধীনতা ও শ্রমকে কজে লাগিয়ে একটি স্বাধীন অর্থনীতি ও উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু তা হতে পারেনি কারণ, যে ঘৃণিত ও অবক্ষয়িত দাসপ্রথা ব্রোঞ্জযুগের সাথে সাথেই বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, গ্রীকরা তা টিকিয়ে রেখেছিল ।
তার ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল দুটি বিপরীত শ্রেণী—দাসমালিক ও ক্রীতদাস। দাসমালিকগণ সর্বপ্রকার শারিরীক শ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখত। অন্যদিকে ছিল নিপীড়িত বঞ্চিত অসহায় ক্রীতদাস— উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েও উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো সুফলই তাদের কাজে লাগত না। কাজেই উৎপাদিকাশক্তির বিকাশেরও তারা কোনো অবদান রাখতে পারেনি। এ অসঙ্গতির দরুনই গ্রীকযুগে উৎপাদিকাশক্তির যতখানি বিকাশ ঘটা সম্ভব ছিল, তা হতে পারেনি।
রোমানরা তাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপরে, সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রহণ করেছিল গ্রীকদের উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা। প্রথম থেকেই রোম সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। একের পর এক দেশ জয় করে রোম তার রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেছিল। শেষ পর্যন্ত এর ফল হয়েছিল ভয়াবহ। একটির পর একটি রাজ্য জয় করে সেখান থেকে রোম সংগ্রহ করেছিল বিপুলসংখ্যক ক্রীতদাস।
খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইতালিতে ক্রীতদাসের সংখ্যাই ছিল দু কোটিরও বেশি—যেটা সমগ্র স্বাধীন জনসংখ্যার প্রায় তিনগুণ। এ সকল ক্রীতদাসদের উৎপাদনের সর্বস্তরে নিয়োগ করার ফলে স্বাধীন কৃষক ও শ্রমিকরা হয়ে পড়ল বেকার ও অন্যদিকে সমাজে দাসদের, বিশেষত দাসনারীর উপস্থিতি নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা করল। ক্রীতদাস প্রথার বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা ক্রমাগত এর মূল উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ দাসদের ধ্বংস সাধন করত।
অধিক মাত্রার পরিশ্রমের ফলে ক্রীতদাসগণ অতি অল্পদিনেই মারা যেত এবং সেখানে নতুন দাস যোগাড় করতে গিয়ে আবার নতুন রাজ্য জয় করতে হত। এভাবে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে গিয়ে রোমানরা তাদের সামরিক শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলল। এর ফল ফলল মারাত্মকভাবে, যা আমরা পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি।
আমরা দেখেছি সামরিক অধিনায়কগণ কিভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে রোমে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ ডেকে এনেছিলেন এবং কিভাবে তাঁরা শেষ পর্যন্ত রোম প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দাস-মালিকগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সামরিক অধিনায়কের শাসনই উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করল। যতদিন পর্যন্ত রোমের সাম্রাজ্যবিস্তার অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন পর্যন্ত দাসপ্রথা টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল।
কিন্তু যখনই সাম্রাজ্য বিস্তার বন্ধ হল তখনই বিজিত দেশ থেকে যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসরূপে আমদানি করা বন্ধ হয়ে গেল। এর ফলে দেখা দিল আসল সংকট। উৎপাদনে দাসপ্রথা কিভাবে সংকট সৃষ্টি করেছিল তা আমরা রোমক ঐতিহ্য পূর্বেই আলোচনা করেছি। দাস অর্থনীতি এমনই পশ্চাৎপদ যে এটা ফলিত বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধন করতে পারে না। অথচ ক্রমাগত যান্ত্রিক ও কারিগরি আবিষ্কারের মাধ্যমে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ না ঘটালে কোনো সভ্যতাই শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে না।
দাসতন্ত্রের উচ্চতম পর্যায়ে, রোমান যুগে কোনো যান্ত্রিক আবিষ্কার তো ঘটেইনি, উপরন্তু আগে যে সকল কাজে গাধা বা ঘোড়ার ব্যবহার হত, সুসভ্য রোমান যুগে সে সকল কাজে দাসদের নিয়োগ করা হত। এভাবে দাসতন্ত্র উৎপাদন প্রথার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে বসে থাকে।
ফলে উৎপদনের সকল স্তরে সংকট প্রকটভাবে দেখা দেয়। বাইরে থেকে দাসের যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ক্রীতদাস ধরে রাখার চেষ্টা করল।
তাদের উপর শোষণের মাত্রা পূর্বের অপেক্ষা বেড়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই ক্রীতদাসগণ বিদ্রোহ শুরু করল। দাসবিদ্রোহ ব্যাপক হারে দেখা ছিল। অনেক দাসই পালিয়ে গেল এবং রোমক ঐতিহ্য তাদের আর ধরে আনা সম্ভব হল না; বাকি যারা রইল তাদের দিয়ে আর আশানুরূপ কাজ না পাওয়ার ফলে দাসপ্রথা আর কোনোক্রমেই লাভজনক রইল না। এ সংকট এড়ানোর একমাত্র উপায় ছিল দাসপ্রথাকে বিলুপ্ত করে, উৎপাদন সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে, উৎপাদিকাশক্তির অভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটানো।
কিন্তু অধিকাংশ দাস-মালিকই দাসপ্রথার বিলুপ্তি সাধনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সংকট আরও ঘনীভূত হতে লাগল। সংকট দেখা দিল সর্বত্র— কৃষি ও শিল্পে দিন দিন উৎপাদন কমতে শুরু করল; ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমে অচল হয়ে উঠল। অর্থনীতির অবক্ষয়ের ফলে সর্বত্র অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। রোগ ও মহামারীতে প্রচুর লোকক্ষয় ঘটতে শুরু করল। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর জনশূন্য হয়ে গেল মহামারীতে।
এর উপর শুরু হল বৈদেশিক আক্রমণ। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে এ আক্রমণ এত মারাত্মকভাবে দেখা দিল যে, বিশাল রোমান সামরিক বাহিনী দিয়েও তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হল না। রোমান সৈন্যবাহিনীতে বিদেশী সৈন্যদের ভর্তি করা হলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় দিন দিন বেড়ে চলল। কিন্তু এত সংকটের মধ্যেও রোমান সম্রাটদের বিলাসিতা এতটুকু কমেনি। এক হিসাবে দেখা যায় যে, এ বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ সোনা ও অর্ধেক পরিমাণ রূপা ভারতবর্ষে চালান হয়ে গেছে।
এমনকি মুদ্রা তৈরির জন্য এখন উপযুক্ত পরিমাণ সোনা-রূপার ঘাটতি দেখা দিল। এ ঘাটতি মেটানো হল খাদ মেশানো মুদ্রা তৈরি করে। খাদের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মুদ্রার শতকরা সাড়ে আটানব্বই ভাগই খাদ। এ খাদ মেশানো মুদ্রায় আস্থা না থাকায় শেষ পর্যন্ত মুদ্রাপ্রথাই বাতিল হয়ে গেল। অর্থনীতি আবার ফিরে গেল বিনিময় প্রথায় । এ সংকটময় পরিস্থিতিতে দাসপ্রথা অচল হয়ে উঠল।
গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন কৃষিখামারে বা শহরে কারখানায় বা খনিতে কোথাও দাসপ্রথা আর লাভজনক রইল না। ব্যাপকহারে উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রকৃতপক্ষে লোপ পেয়ে গেল। শহরের কারখানা ও খনিগুলি ক্রমে অচল হয়ে উঠল। গ্রামে অবশ্য অনেক ভূস্বামী তাদের বড় বড় কৃষি খামারগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো করে অনেক ক্ষেত্রে ক্রীতদাসদের মুক্ত করে তাদের মধ্যেই জমি বন্টন করে দেন।
দাসশ্রমের দ্বারা কৃষিখামার পরিচালনার পরিবর্তে স্বাধীন কৃষকদের উৎপন্ন ফসলে ভাগ বসানোই তাদের কাছে অধিক লাভজনক বলে মনে হয়। গ্রামে ভিলা বা দুর্গ তৈরি করে অনেকে কৃষকদের নিরাপত্তার ভার স্বহস্তে তুলে নেন। ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক আক্রমণের মুখে নিষ্ক্রিয় রোমান সম্রাটের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যখন ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকে, তখন স্থানীয় ভূস্বামীগণই কৃষকদের জান ও মাল অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করেন। রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে এভাবেই দাসপ্রথা আপনা আপনি ভেঙে পড়ে।
শহরগুলি পূর্বেই অচল হয়ে গিয়েছিল। কিছু সংখ্যক শ্রমিক ও কারিগর শহর থেকে গ্রামে চলে আসে এবং ভূস্বামীদের আশ্রয় গ্রহণ করে একটি স্বনির্ভর ম্যানর অর্থনীতি বা গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কৃষিজীবীরাই প্রধান হলেও কামার, কুমার,নাপিত, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, মুচি ও দর্জি— এদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে পরবর্তী সামন্ত অর্থনীতির ভিত্তি। রোমান সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী বর্বর জাতিরা এ ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়েছিল।
তাদের মধ্যে দাসপ্রথার কোনো প্রচলন ছিল না বলেই স্বাধীন স্বনির্ভর সামন্ত অর্থনীতি গড়ে তুলতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।
এভাবেই রোমান সামাজ্য তার অবক্ষয়িত দাসপ্রথা নিয়ে চিরতরে ভেঙে পড়ল। মানবজাতির চরম অবমাননার ইতিহাস দাসপ্রথার ইতিহাস।
এ অবমাননাকর প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে রোমানগণ নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে সবচেয়ে বেশি। ঘুণে ধরা রোমান সাম্রাজ্য বর্বর আক্রমণের অনেক আগেই অস্তমিত হয়েছিল। বর্বর আক্রমণ এ অবক্ষয়িত রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটিয়ে মানবজাতির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেয়।

রোমক সাম্রাজ্যের পতন
তৃতীয় শতাব্দী থেকেই রোমের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটতে থাকে। রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস-এর মৃত্যুর পর থেকেই রোম সংকটের গহ্বরে পতিত হয়। অগাস্টাস কর্তৃক সৃষ্ট প্রিটোরিয়ান গার্ডবাহিনী এখন রোমের শাসনক্ষমতায় সর্বেসর্বা। তারা তাদের ইচ্ছামতো রোমান সম্রাট নিযুক্ত করত, ইচ্ছামতো তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করত। সম্রাটদের মধ্যে অনেকে হয়তো রোমের রাজপ্রাসাদেও প্রবেশ করেননি, তার পূর্বেই তাঁরা আততায়ীর হাতে নিহত হন।
এরূপ চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে শুরু হল অভ্যন্তরীণ অন্যান্য সংকট। প্রথমত গৃহযুদ্ধ, যার ফল ছিল হত্যা, গুপ্তহত্যা ও অজস্র লোকের প্রাণনাশ। দ্বিতীয়ত শিল্প ও বাণিজ্যের সংকট। উৎপাদন কমতে শুরু করল, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্ষেত্রেও সংকট সৃষ্টি করল। ঠিক এ সময়েই বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করে।
পশ্চিম দিকে ফ্রাঙ্ক ও এ্যালেমানিগণ গল আক্রমণ করে ও স্যাক্সনগণ ব্রিটেন দখল করে নেয়। ইতিমধ্যে আফ্রিকান মুরগণ স্পেনের বিরাট অংশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। অন্যদিকে কৃষ্ণসাগরের উপকূলস্থ অঞ্চলগুলিতে শুরু হয় বিভিন্ন গথজাতির আক্রমণ। রোমান বহিনীর পক্ষে এ সকল আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তার কারণ ঠিক একই সময়ে তাদের রোমের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে ব্যাপৃত থাকতে হয়।

এরই সুযোগ নিয়ে পূর্বদিকে পারসিক বাহিনী রোমের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। রোমের বৈদেশিক অক্রমণের কালেই এর অভ্যন্তরীণ সংকট চরমে পৌঁছে। রোমের শ্রেণীসংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। এ শ্রেণীসংগ্রাম শুধু ক্রীতদাস ও দাস-মালিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শোষিত নিপীড়িত অন্যান্য শ্রেণীদের বিক্ষোভ এ সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলে।
এ বিদ্রোহ প্রথমত শুরু হয় আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরে, পরে তা ছড়িয়ে পড়ল স্পেনে। এসব প্রদেশের দাসবিদ্রোহের সাথে কৃষকবিদ্রোহ একই সাথে সংঘটিত হয় এবং সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের শান্তি ও স্থিতি বিনষ্ট করে তোলে। রোমের এই চরম অরাজকতার দিনে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচয় দেয়। অভ্যন্তরীণ সংকট ও বহিঃশত্রুর আক্রমণরোধে এর চরম ব্যর্থতা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে দেয়।
এরূপ সংকটজনক পরিস্থিতিতে ২৩৮ খ্রিস্টাব্দে ডায়োকেশিয়ান রোমের সম্রাট নিযুক্ত হন। তিনি এসে রোমের নামেমাত্র পরিচিত গণতন্ত্রের চিহ্নকে লুপ্ত করে দেন। সিনেটকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হল। ডায়োকেশিয়ান নিজেকে ডোমিনেট বা লর্ড বলে ঘোষণা করেন। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডায়োকেশিয়ান এখন থেকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত রোম প্রজাতান্ত্রিক রোম নামেই পরিচিত ছিল।)
শাসনকার্যের সুবিধার্থে রোমকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। রোমান সম্রাট নিজের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধারণ করে বাকি তিনটি ভাগে তাঁর অধীনস্থ তিনজন শাসক নিযুক্ত করেন। এ তিন বিভাগকে আবার বারোটি ডায়োসেস (Diocese) এবং সেগুলিকে সর্বমোট ১০১টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। এছাড়া ডায়োক্লেশিয়ান করপ্রথার সংস্কার সাধনকল্পে জমির উপর খাজনা নির্দিষ্ট হারে বেঁধে দেন।
তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বেঁধে দিয়ে মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থায় একটি স্থিতিশীলতা আনয়নেরও প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ডায়োক্লেশিয়ান সাম্যাজ্যের সংকট এড়াতে পারেননি। কারণ প্রাচ্যদেশীয় রাজন্যবর্গের অনুকরণে রোমের রাজপ্রাসাদে যে বিলাসব্যসনের প্রবর্তন তিনি করে গিয়েছিলেন— তা তাঁর সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্কারকেই বানচাল করে দিয়েছিল। ডায়োক্লেশিয়ানের মৃত্যুর পর কনস্টানটাইন রোমের সম্রাট হলেন।
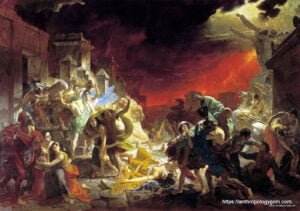
তিনি প্রায় ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে কনস্টানটাইন বসফরাস- এর তীরে রোমের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করলেন। সাম্রাজ্যকে এখন থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা হল : পূর্ব রোমান সাম্রার্জ ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য। সম্রাটের নামানুসারে নতুন রাজধানীর নামকরণ করা হল কনস্টান্টিনোপল। প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ বাইজেন্টিয়াম ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।
পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের উপর ক্রমাগত বর্বর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টধর্মকে রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত ধর্মের সমান মর্যাদা দান করেন। উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিলাসিতার কেন্দ্রভূমিরূপে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যই এখন থেকে প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হল এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশ একে একে বর্বরদের হাতে অধিকৃত হতে লাগল ।

কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কনস্টানটাইনাস ও পরে পৌত্র জুলিয়ান পূর্ব রোমান সম্রাট নিযুক্ত হন। জুলিয়ান খ্রিস্টধর্মকে অগ্রাহ্য করে রোমের প্রাচীন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁর এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং রোমান সাম্রাজ্য তার পতনের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়। পরবর্তীকালের দেড়শত বছরের রোমান সাম্রাজ্যের ইতহাস এক চরম অবক্ষয়ের ইতিহাস। একের পর এক প্রায় চল্লিশজন সম্রাট রোমের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হন।
এদিকে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন বর্বর জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে প্রায় সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য বর্বরদের হাতে চলে যায়। অবশেষে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে বর্বর নেতা অডোএকার সর্বশেষ রোমান সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টাসকে সরিয়ে দিয়ে রোমের সিংহাসন দখল করেন। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে তখনও একজন সম্রাট অধিষ্ঠিত থাকলেও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য চিরতরে অস্তমিত হয়। অডোএকার কর্তৃক রোমের সিংহাসন দখলের সাথে সাথে সাত শত বছরের রোম সাম্রাজ্যের চির অবসান ঘটে।
আরও দেখুন :
