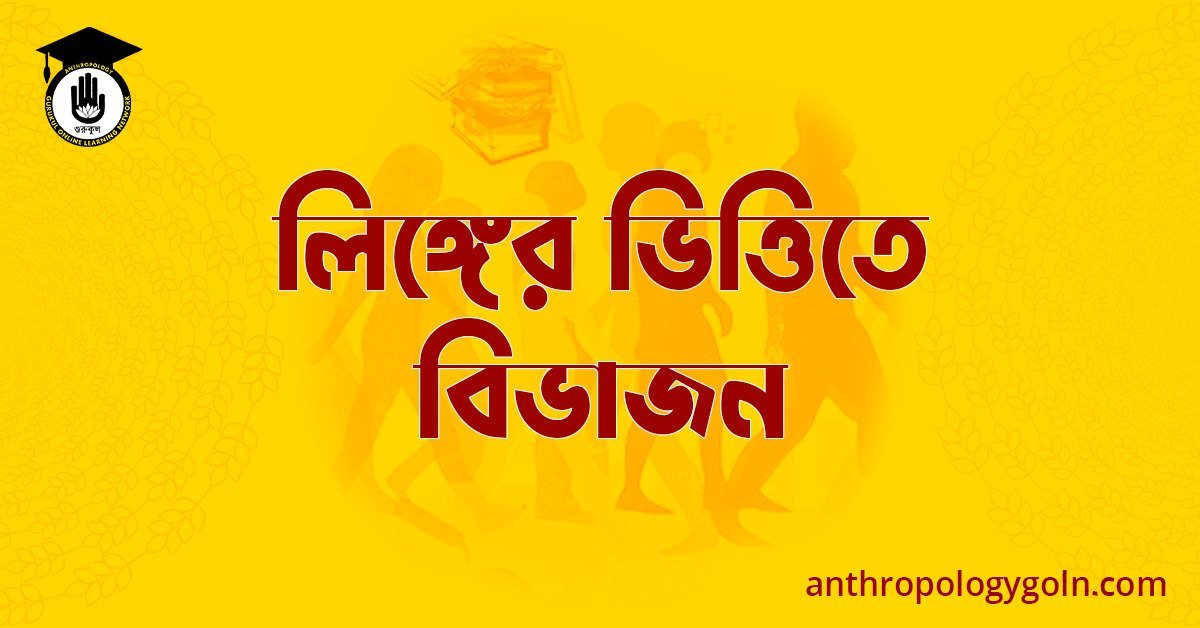আজকে আমরা আলোচনা করবো লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন নিয়ে। দৈহিক নৃবিজ্ঞান (physical anthropology) চর্চার প্রারম্ভিক কালে নারী ও পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য বা প্রভেদকে শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করা হ’ত। নারী ও পুরুষের শরীরের গড়নের ভিন্নতা নিয়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনার সূচনা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় সমাজে নারী-পুরুষের ক্ষমতা, মর্যাদা কিংবা অন্যান্য সুযোগের পার্থক্য বোঝা যায় না।
লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন
সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান তাই গোড়া থেকেই অন্য উপায়ে সমাজের মধ্যকার নারী-পুরুষের পার্থক্য দেখবার চেষ্টা করেছেন। খেয়াল রাখা দরকার নৃবিজ্ঞানের | প্রাথমিক কালে গবেষণা করা হ’ত কেবল অ-ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে। তাই প্রাথমিক নৃবিজ্ঞানে দেখা | হ’ত কোন সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে কি ধরনের ভিন্নতা আছে: দায়িত্বের দিক থেকে, কোন র-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের দিক থেকে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের দিক থেকে, কিংবা আচার- | সমাজে মর্যাদার দিক থেকে। প্রাথমিক কালের নৃবিজ্ঞানের বই-পত্রে এই বিষয়ে আলাপ পাওয়া যেত।
আর এই অধ্যয়নকে বলা হ’ত নারী-পুরুষের প্রভেদ। কিন্তু এখানে আরও একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখার আছে। তা হ’ল: ‘৬০ ‘৭০ দশকে পৃথিবী জুড়ে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে ভীষণ বিতর্ক – ওঠে। এই বিতর্ক তোলেন নারীর পক্ষে আন্দোলনের কর্মীরা এবং নারীর অবস্থান নিয়ে চিন্তিত শিক্ষাবিদেরা। এই বিতর্কে নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় মর্যাদা, | ক্ষমতা এবং সম্পদের বিষয়গুলোকে। সেটা করতে গিয়েই মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা চলে আসে। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

এই বিতর্কের তোলপাড় বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডে এসে পড়ে। নারী বিষয়ক মনোযোগ তাতে একেবারে বদলে যায়। নৃবিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। এই সময়ে এসে নারী বিষয়ক পড়াশোনাকে নারী চিন্তাবিদেরা আর | নারী-অধ্যয়ন (women’s studies) বলতে চাইলেন না। তাঁদের পরিষ্কার কিছু যুক্তি ছিল। যেহেতু নারীর অবস্থান সমাজে পুরুষের অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই নারী ও পুরুষের অবস্থানের পার্থক্য | একটা তুলনামূলক ব্যাপার। একই সঙ্গে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝাটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্কে মনোযোগ দিতে চাইলেন তাঁরা।
এতে নতুন একটা ধারণা বা প্রত্যয় দেখা গেল। ইংরেজীতে তা হচ্ছে জেন্ডার (gender) । সেক্স ( sex ) শব্দটা দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যকার শারীরিক বা জৈবিক পার্থক্য বোঝাতো। সেটা এখনও বোঝায়। কোন দরখাস্ত পূরণ করতে গেলে দেখা যায় সেখানে ‘সেক্স’ জানতে চাওয়া হয়। বিতর্কের পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজি ভাষায় জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার শুরু হ’ল। এই শব্দ দ্বারা সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যকে কিংবা সামাজিক অবস্থানকে বোঝানো হয়। ‘৮০-এর দশকে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের কর্মী ও চিন্তাবিদেরা মিলে এই জেন্ডার শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ বাছাই করেছেন ‘লিঙ্গ’।

তাই লিঙ্গীয় সম্পর্ক বলতে নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক বোঝায়। আর লিঙ্গীয় বৈষম্য বলতে নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক অসমতা বোঝায়। এখানে অসমতা বলতে সহজভাবে ক্ষমতা, মর্যাদা আর সম্পদের পার্থক্যকে বোঝা যেতে পারে। তবে নারী ও পুরুষ ছাড়া আরও একটি লিঙ্গ সমাজে আছে। তাঁদের কথা স্মরণে না রাখলে চলবে না। কারণ তাঁরাও হিজড়া একটা সুবিধা বঞ্চিত লিঙ্গ এবং নির্যাতিত।
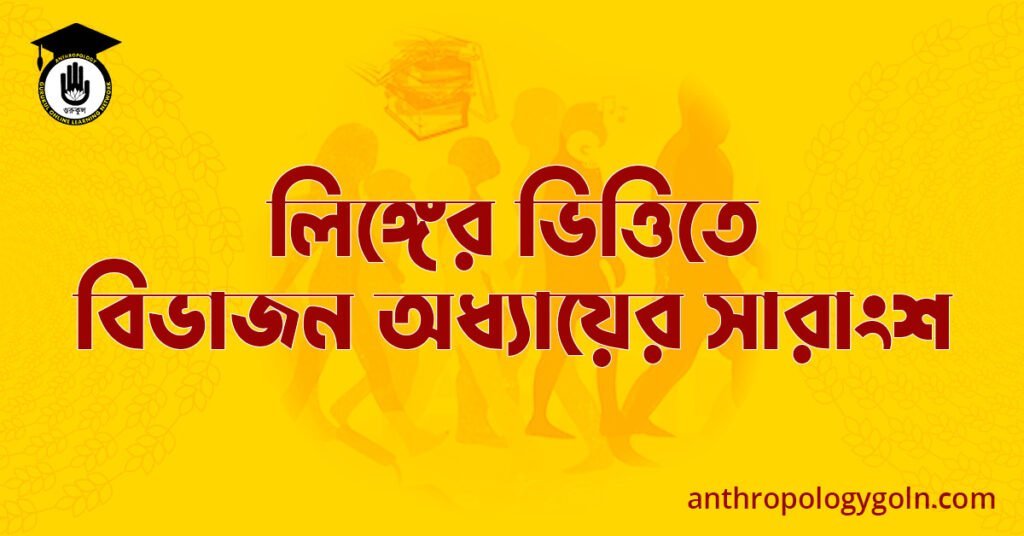
লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয় লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন অধ্যায়ের -সারাংশ – যা লিঙ্গের- ভিত্তিতে বিভাজন এর অর্ন্তভুক্ত, অধিকাংশ সমাজেই নারী-পুরুষের মধ্যে নানান ধরনের সামাজিক বৈষম্য রয়েছে। তা নিয়ে সমাজ-চিন্তুক এবং নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন।
প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞারীরা মনোযোগ দিয়েছেন উৎপাদন কাজে নারীদের অংশগ্রহণ, সম্পদের উপর তাঁদের অধিকার এবং মান-মর্যাদার উপর। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছেন এক সময়ে পৃথিবীতে নারীকেন্দ্রিক সমাজ ছিল। গত ৩/৪ দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের লড়াই-সংগ্রাম জোরাল ছিল। এতে নৃবিজ্ঞান সহ অন্যান্য জ্ঞানকান্ডে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে যুক্তি-তর্ক নতুন রূপ পেয়েছে। কেবল সম্পদের উপর দখল নয়, সমাজে যে ভাবনা-চিন্তা, মূল্যবোধ চালু সেটাও নারীর বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল বলে গবেষকরা দেখাচ্ছেন।
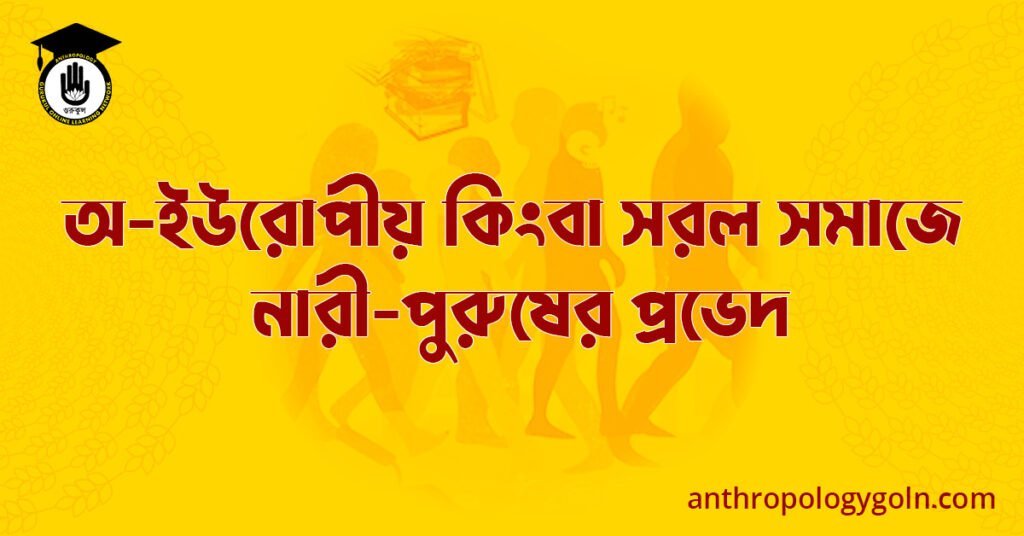
অ-ইউরোপীয় কিংবা সরল সমাজে নারী-পুরুষের প্রভেদ
আজকের আলোচনার বিষয় অ-ইউরোপীয় কিংবা সরল সমাজে নারী-পুরুষের প্রভেদ – যা লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন এর অর্ন্তভুক্ত, আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে প্রথম কালের নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন ইউরোপের বাইরের সমাজে। সাধারণভাবে যে সকল সমাজ শিল্পোন্নত কিংবা প্রযুক্তি নির্ভর ছিল না, নৃবিজ্ঞানের আগ্রহ ছিল সেই সব সমাজ নিয়ে। আফ্রিকা, এশিয়া কিংবা আমেরিকার আদিবাসীদের এই সব সমাজকে প্রথম পর্যায়ের নৃবিজ্ঞানে আদিম সমাজ বলা হ’ত। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃবিজ্ঞানীরা এই সব সমাজের নাম দেন ‘সরল’ সমাজ।
প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানে সামাজিক বিভাজন দেখতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা মূলত কাজ কর্মের ভাগাভাগির পদ্ধতির উপর মনোযোগ দিয়েছেন। কোন সমাজে কাজ কর্মের ভাগাভাগির প্রক্রিয়াকে সামাজিক বিজ্ঞানে শ্রম বিভাজন বলা হয়। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন মানুষ কি কি দায়িত্ব পালন করবে তার একটা ব্যবস্থা থাকে। এভাবেই সমাজে উৎপাদন হয়। এখানে নারী-পুরুষের বিভাজনের কথা হচ্ছে। এখানে মনে রাখা দরকার নৃবিজ্ঞানীরা যে সব সমাজে গবেষণা চালিয়েছেন সেই সময়ে তার অনেকগুলোতেই আজকের যুগের মত বৈষম্য ছিল না । তা সে নারী পুরুষের মধ্যেই হোক, আর সমাজের মানুষে মানুষে হোক। তাছাড়া আজকের যুগে সম্পদের রকম অনেক বেড়ে গেছে।
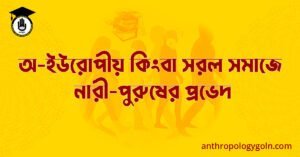
ফলে সম্পদের ভিত্তিতে ভেদাভেদ তৈরি হবার পরিস্থিতি এখন অনেক তীব্র। সমাজে এক সময় মাতৃ-অধিকার ছিল বলে সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন। মাতৃ- অধিকারের ধারণা দিয়েছেন বাকোফেন, এঙ্গেলস, মর্গান প্রমুখ। এই ধারণার সারাংশ হচ্ছে: এক সময়ে পুরুষের হাতে ক্ষমতা ছিল না। সমাজ এবং পরিচালনার যাবতীয় কর্তৃত্ব ছিল নারীর হাতে। কেবল তাই নয়, সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হ’ত মায়ের দ্বারা। মায়ের বংশই স্বীকৃত হ’ত। সেই সমাজের নাম দেয়া হয়েছে আদি সাম্যবাদী সমাজ। এই ধারণার পক্ষে নানান যুক্তিও তাঁরা হাজির করেছেন।
সামাজিক বিজ্ঞানে এই ধারণা যুগান্তকারী হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে নারীর লড়াইয়ে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের জন্য এটা একটা বিরাট উদ্যম হিসেবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই চিন্তার যাবতীয় দুর্বলতা ধরা পড়ে। প্রথমত, কোন এক কালে এই ব্যবস্থা ছিল – এটা একটা অনুমান করা ব্যাখ্যা। যখন – থেকে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা চলছে তখন এর তেমন কোন উদাহরণ পাওয়া যায়নি। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমাজে মায়ের পরিচয় ধরেই আত্মীয়তা বা আবাস-বাড়ি গড়ে উঠছে। কিন্তু মাতৃ-অধিকারের ধারণা থেকে তা খুবই ভিন্ন।
বরং বিভিন্ন সমাজে নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব, কিংবা নিপীড়নের নানা রকম ধরন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এ কথা ঠিক, সমাজভেদে তা ভিন্ন, এবং অধিকাংশ অতীতের সমাজে এর নজির খুবই কম। দ্বিতীয়ত, মাতৃ-অধিকার যদি থেকেই থাকে তাহলে তা কেন সহসা বদলে গেল তার কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, অনেক নারী আন্দোলনকারী মনে করেন: এ রকম কাল্পনিক একটা তত্ত্ব ধরে নিয়ে এগোলে বর্তমান কালের পুরুষের ক্ষমতা এবং পুরুষকেন্দ্রিক ব্যবস্থা অনুমোদন পায়।
মানে ‘এক সময়ে যেহেতু নারীর ক্ষমতা ছিল – এখন তাহলে পুরুষের ক্ষমতার দোষ কি!’ তাঁদের ব্যাখ্যা হচ্ছে: যদি নারীকেন্দ্রিক সমাজ কখনো থেকেই থাকে – তার গড়ন আজকের – মত আক্রমণাত্মক ছিল না। সেটা সমাজ ইতিহাস বিশে ষণ করলে বোঝা যায়। নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণাতে লক্ষ্য করা গেছে সকল সমাজেই নারী-পুরুষের কাজ কর্মের মধ্যে ভিন্নতা আছে। এর মানে হ’ল খাদ্য উৎপাদনের কাজে পুরুষের কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্ব আছে আর নারীর কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্ব আছে। উৎপাদনের কাজে নারী ও পুরুষের দায়িত্বের বিভাজনকে লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন বলা হয়।
যে সব সমাজকে শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ বলা হয়ে থাকে সেখানে প্রায়শই পুরুষরা শিকারী এবং নারীরা সংগ্রহকারী। এর মানে হচ্ছে শিকারের কাজ কিছু পুরুষরা করে থাকেন এবং নারীরা এবং অন্যরা – যেমন বয়স্করা, বাচ্চারা ফলমূল সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু এই ধারণার বিপরীতে নানান উদাহরণও আছে। যেমন: হাডজা এবং ভারতের পলিয়ানদের মধ্যে পুরুষরা নিজেদের জন্য বৃক্ষজাত খাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আর নারীরা নিজেদের এবং বাচ্চাদের জন্য একই খাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আবার যেখানে শিকার একটা যৌথকাজ হিসেবে বিবেচিত সেখানে দেখা যায় ভিন্ন ব্যাপার।
যেমন: স্মৃতিদের মধ্যে নারী ও পুরুষরা একত্রে জন্তু জানোয়ারকে তাড়া করে শিকারের এলাকাতে নিয়ে যায়। অবশ্য বৃহৎ জন্তুর বেলায় সেটা শিকারের দায়িত্ব পুরুষরাই পালন করে থাকে। উদ্যান-কৃষির সমাজেও নারী পুরুষের শ্রম বিভাজনের নজির পাওয়া যায়। কোন কোন গবেষণাতে দেখা গেছে, পুরুষরা জমি সাফ করার কাজটা সাধারণত করে থাকেন। আর চাষবাসের কাজটা নারী পুরুষ একত্রে করেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীরাই প্রধান খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। যেমন: নিউ গিনিতে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মিষ্টি আলু উৎপাদন করে থাকেন নারীরা।
পুরুষরা সেখানে উৎপাদন করেন চিনি, কলা যেগুলো অন্যত্র বিনিময় করা হয়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সাধারণভাবে উৎপাদনের প্রাথমিক কাজগুলো পুরুষরা করে থাকেন। আর উৎপাদন প্রক্রিয়াজাত করণ সমেত রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজ নারীরা করে থাকেন। তবে এই চিত্রের সাধারণ কোন প্রমাণ নেই ।
বাংলাদেশের কৃষিতেও উৎপাদন কাজে নারীরা ব্যাপকভাবে অংশ নিয়ে থাকেন। পাশাপাশি রান্না-বান্নার পুরোটাই এবং ফসল প্রক্রিয়াজাত করণের পুরোটাই তাঁদের উপর গিয়ে বর্তায়। এভাবে নানা উদাহরণ দিয়ে দেখানো সম্ভব যে বিভিন্ন সমাজে নারী ও পুরুষের কাজ আলাদা আলাদা থাকে। কিন্তু এ দিয়ে কোন কিছু বুঝতে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ কোন একটা সমাজে যেটা নারীদের কাজ অন্য সমাজে সেটাই হয়তো পুরুষের কাজ। যেমন: সূতোতে বোনার কাজটা আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের জাতিসমূহের মধ্যে নারীরা করেন, কিন্তু আফ্রিকাতে পুরুষরাই করে থাকেন। আবার ভারত, মধ্য আফ্রিকাতে মাটির পাত্র বানাবার কাজটা পুরুষের এবং পশ্চিম আফ্রিকা কিংবা আমেরিকান ভূখন্ডের আদিবাসীদের মধ্যে এটা নারীদের কাজ।
অধিকাংশ অ-ইউরোপীয় সমাজ বা প্রথম যুগের নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায় সরল সমাজে বাচ্চা দেখাশোনার কাজ মায়েরা যেমন করে থাকেন, তেমনি তা অন্যদের অবসরের কাজও বটে। বয়স্ক লোকজন, একটু বেশি বয়সের বাচ্চারা কিংবা জোয়ান পুরুষরা যাঁরা উৎপাদন কাজে যাচ্ছেন না তাঁরা যে কেউই এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বরং অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীই এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে এই সব সমাজে আর্থিক এবং ক্ষমতার দিক থেকে কোন উঁচু-নিচু ভেদ ছিল না। ফলে কাজের ভিন্নতা দিয়ে সমাজে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বুঝতে যাওয়া ঠিক হবে না। ভেদাভেদ বলতে এখানে সুযোগ-সুবিধার বঞ্চনা বোঝানো হচ্ছে।
কোন কোন তাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে নারীরা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় সমাজে কাজ-কর্মের এই হেরফের, এবং এ কারণেই নারী পুরুষের তুলনায় বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু এই যুক্তি খুবই একপেশে এবং দুর্বল। প্রথমত, শারিরীকভাবে প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষের চেয়ে বলশালী অনেক প্রাণী আছে। আর তাছাড়া বহু সমাজে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকেই এমন প্রমাণ মিলেছে যে সমাজে নারীরা মোট কাজের বেশির ভাগ করে থাকেন। আরেক ধরনের যুক্তি হচ্ছে নারীরা ঐতিহাসিকভাবে বাচ্চা লালন-পালনের সাথে যুক্ত বলে এবং বাচ্চা হওয়ার সময়ে লম্বা বিরতি দিতে হয় বলে নারীরা ‘কম’ গুরুত্বের কাজগুলো করে থাকেন এবং সে কারণে সমাজে তাঁদের বঞ্চনা।
এই যুক্তিরও বড় ধরনের দুর্বলতা আছে। প্রথমত, নারীরা যে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন তা নয়। বরং, আগেই আলোচিত হয়েছে, উৎপাদনের সিংহভাগ কাজই তাঁরা হরে থাকেন অধিকাংশ সমাজে। আর ঘর-গেরস্থালির কাজ প্রায় পুরোটাই, বিশেষ করে বর্তমান সমাজে।
বরং দেখা যায়, নারীর কাজকে অল্প গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, বহু সমাজেই বাচ্চা পেটে নিয়ে নারীরা কাজ করে থাকেন। আর বর্তমান কালে বাচ্চা হওয়া কমানোর প্রক্রিয়াতেও নারীর নিপীড়ন চলছে। পরিবার পরিকল্পনার যাবতীয় পদ্ধতি, বিশেষভাবে যেগুলো রাসায়নিক, চরম একপেশে যেমন ধরুন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি যার থাকতে পারে বিভিন্ন রকমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এ সমস্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সহজেই বোঝা যায় সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদ বা বৈষম্যের উৎস অন্য কোথাও। সমকালীন নগর সমাজের বাস্তবতার দিকে তাকালে সেটা আরও সহজে বোঝা যায়।
বর্তমান কালের লিঙ্গীয় বৈষম্য
আজকের আলোচনার বিষয় বর্তমান কালের লিঙ্গীয় বৈষম্য – যা লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন এর অর্ন্তভুক্ত, বর্তমান কালে নারী-পুরুষের বৈষম্যের কতগুলি স্পষ্ট দিক খেয়াল করা যায়। আগেই আলোচনা করেছি যে, অ-ইউরোপীয় সমাজে বৈষম্যের উপাদান কম ছিল। পক্ষান্তরে, বর্তমান সমাজে নানাবিধ সম্পদ ও সুবিধা থাকাতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের উপকরণ হিসেবে সেগুলি কাজ করে।
বর্তমান কালে গেরস্তালির কাজের বাইরে সকল কাজই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে করে থাকেন। শিল্প উৎপাদনের জন্য নারী শ্রমিক এখন নিয়মিত ব্যাপার। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প এর ভাল উদাহরণ হতে পারে। এছাড়া নির্মাণ শিল্পে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আছে। কিন্তু নারীর প্রতি বৈষম্য আর নিপীড়নও সমান তালে চলছে। প্রথমেই মজুরির কথা বলা যায়।
গার্মেন্টস কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা নারী শ্রমিকের মজুরি পুরুষ অপেক্ষা কম। অনেক গবেষণায় দেখা যায় নারীকে কম মজুরি দেবার ইচ্ছে থেকেই অনেক শিল্পে নারীকে বেশি করে নিয়োগ দেয়া হয়। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয় নারীকে। এমনিতেই শ্রমিক শ্রেণীর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত নেই। ফলে নানা ধরনের হয়রানির মুখোমুখি হয় শ্রমিকেরা। কিন্তু নারীর জন্য বাড়তি নিপীড়ন হচ্ছে যৌন হয়রানি। এর মধ্যে থেকেই কাজ করতে হয় নারী শ্রমিককে। কিন্তু রোজগার করার কারণে নারী তাঁর ঘর-গেরস্তালির কাজ হতে মুক্তি পান না। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করে তাঁকেই আবার রান্না-বান্না, বাচ্চা দেখা শোনা কিংবা অন্যদের সেবা যত্ন করতে হয়।
নারীরা
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক,
সমগ্র কর্মঘন্টার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময়
তাঁদের কাজ করতে হয়,
তাঁরা রোজগার করেন পৃথিবীর মোট আয়ের
এক-দশমাংশ,
এবং পৃথিবীর ধন-সম্পদের
এক-শতাংশের ও কম আছে তাঁদের আয়ত্তে ।
সূত্র : ইউনাইটেড নেশনস রিপোর্ট, ১৯৮০
শিক্ষিত এবং স্বচ্ছল শ্রেণীর নারীদের বাস্তবতা কিছুটা ভিন্ন। সকল ধরনের পেশাতেই নারীরা কাজ করছেন। চাকুরিতে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো থাকাতে মজুরির নিপীড়ন এক্ষেত্রে ঘটে না। এখানে প্রাথমিক বৈষম্য কিছুটা ঘোরানো পথে হয়ে থাকে। অনেক চাকুরিতেই নিয়োগ দেবার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যদিও হয়তো নিয়োগ বিধিতে উভয় লিঙ্গকে সমান প্রাধান্য দেবার কথা বলা আছে। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গর্ভকালীন ছুটির কোন নিশ্চয়তা না থাকলেও উঁচু চাকুরিতে আছে। তবে গর্ভকালীন ছুটি নিতান্ত কম ।
নারী চাকুরি করুন বা নাই করুন স্বচ্ছল নারীদেরকেও ঘর-গেরস্তালির কাজ, বাচ্চাদের দেখাশোনা বা লেখাপড়া করানো, অন্যদের – বিশেষভাবে স্বামীকে দেখাশোনা করার কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে না – করতে চাইলে সেটা খুব নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সেই নারী ‘মন্দ’ বলে সাব্যস্ত হন । নানা রকম হয়রানির আতঙ্ক এই শ্রেণীর নারীদের কর্মক্ষেত্রেও রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় সে ব্যাপারে প্রচুর প্রতিবেদনও প্রকাশ পায় ।
বর্তমান সমাজে স্বচ্ছল বা শ্রমিক উভয় শ্রেণীতেই বিয়ের মধ্যেও নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বা বৈষম্য বোঝা যায়। উভয় শ্রেণীতেই যৌতুক দিয়ে নারীদের বিয়ে হয়। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যৌতুক কেবল দরিদ্র মানুষের মধ্যেই প্রচলিত। আসলে স্বচ্ছল মানুষজন যৌতুককে উপহার বলে চালিয়ে থাকেন। যৌতুকের কারণে শারীরিক নির্যাতন উভয় ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। নারী-পুরুষ অসমতার একটা প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ঘরের কাজ। এতে পুরুষের প্রায় কোন ধরনের অংশগ্রহণ থাকে না। বলা হয়ে থাকে পুরুষ রোজগার করে আর নারী সংসার চালায়। কিন্তু শহুরে স্বচ্ছল শ্রেণীতে এখন এই কথাটা খুব একটা খাটে না। নারীরাও সেখানে রোজগার করেন।
তাছাড়া ঘরের কাজের যদি মজুরি হিসাব করা হয় তাহলে পুরো চিত্রটা একেবারেই বদলে যাবে। এখানে একটা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করবার আছে। ঘরের কাজে যাবতীয় প্রকারে নারী শ্রম দিয়ে যাবেন। কিন্তু এই শ্রমকে অনুৎপাদনশীল মনে করা হয়। গৃহকাজে নারীর শ্রমের কোন মজুরী হিসেব করা হয় না এবং একে হালকা করে দেখা হয়। এভাবে নানান বস্তুগত উপায়ে নারীর উপর নিপীড়ন আছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনেও নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়ে থাকে। কোন কারণে বিয়ে ভেঙ্গে গেলে বাচ্চাদের ওয়ারিশ নিয়ে প্রচলিত আইন এবং সামাজিক অনুশীলন নারীর বিপক্ষে যায়।
বস্তুগত নানাবিধ নিপীড়নের পাশাপাশি আরেকটা বৈষম্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে: নারীকে নিরন্তর অবমূল্যায়ন করা হয়। নারীর কাজ, চিন্তা, জীবন সব কিছুকে উপেক্ষা করা হয়। এই অবমূল্যায়ন বা অমর্যাদাকে বিশে- ষণ করলে দেখা যায় এটা দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। সত্যিকার অর্থে এই উপেক্ষা করে থাকেন পুরুষেরা। তবে সমাজে একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠলে তাতে নারীরাও সামিল হয়ে যেতে পারেন।
তাই অনেক সময় দেখা যায় নারীর বিরুদ্ধে নারীও পদক্ষেপ নিয়ে বসতে পারেন। এ কারণে দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরুষের না বলে পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে: যে চিন্তা দ্বারা নারীকে অক্ষম মনে করা হয়, নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং নারীকে যাবতীয় সুবিধার বাইরে রাখার ব্যাখ্যা তৈরি করা হয়। গত তিন দশকে এই সব ভাবনা-চিন্তা নিয়ে শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে। এই আন্দোলন একদিকে সমাজে নারী-পুরুষের যে বস্তুগত অসমতা আছে (অল্প মজুরি, সম্পত্তি ভাগ, উত্তরাধিকার আইন, যৌন হয়রানি, যৌতুক ইত্যাদি) তার বিরুদ্ধে।
অন্যদিকে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির (উপেক্ষা, গেরস্থালির কাজে পুরুষের অংশ না নেয়া, আক্রমণাত্মক পরিবেশ গড়ে তোলা) বিরুদ্ধে। নারী আন্দোলনের কর্মীরা এবং চিন্তুকগণ নারীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পরিবেশ নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়েছেন এবং আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে ধর্ষণ বা এসিড নিক্ষেপ আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির সবচেয়ে ভয়ানক উদাহরণ। কিন্তু নারীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব আরও সূক্ষ্ম চোখে দেখার প্রয়োজন আছে। প্রচার মাধ্যমে নারীকে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয় সেটা ভেবে দেখা যেতে পারে।
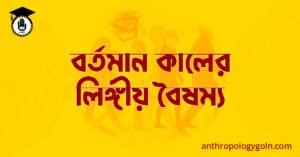
এমনকি ঈদের পত্রিকাতে যে সব কার্টুন আঁকা হয় সেখানেও নারীকে লোভী, গয়না পিপাসু হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। এতে আড়াল হয়ে যায় কিভাবে নারী সংসার চালাবার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে আসছেন। অন্য লিঙ্গের প্রতি পুরুষবাদী সমাজের মনোভাবের আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে হিজড়া সমাজ। তাঁদের জীবনের অবহেলা, আয়ের কোন পথ না থাকা এবং সর্বোপরি মর্যাদা না থাকা দেখে আমরা বুঝতে পারি আমাদের বর্তমান সমাজ কতটা একলিঙ্গবাদী – আর সেই লিঙ্গ হচ্ছে পুরুষ। ফলে পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বদল না ঘটলে নারী-পুরুষের সমতার পুরো লক্ষ্য অর্জিত হবে না। পুরো লক্ষ্য অর্জন হওয়া কেবল আইন বা আয় উপার্জন দিয়ে হবার নয় – সে কথাই নারী আন্দোলনের কর্মী এবং চিন্তকেরা বলছেন।