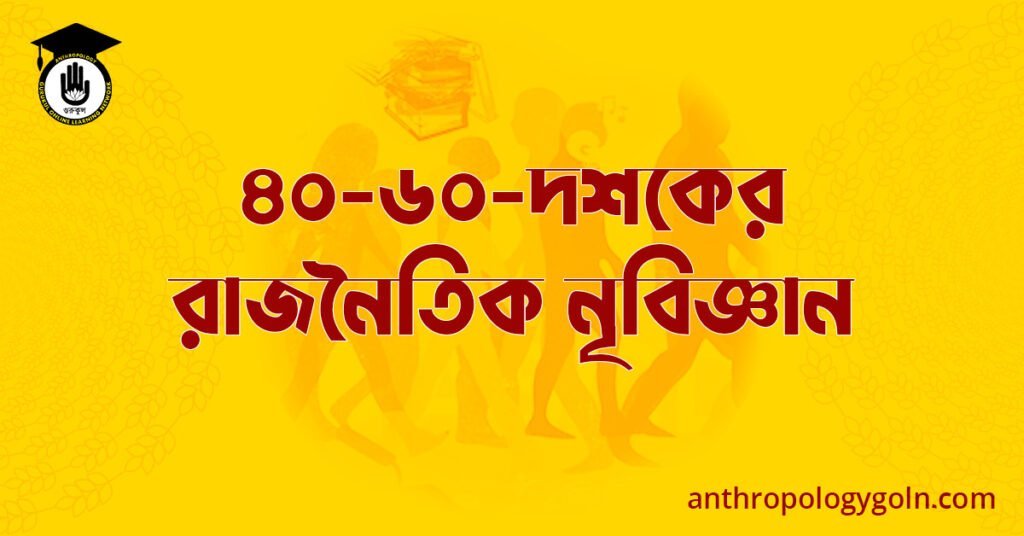আজকের আলোচনার বিষয় ৪০-৬০-দশকের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান – যা রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এর অর্ন্তভুক্ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় অনেক কিছু বদলে গেছে। রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানও তখন বদলেছে। সত্যিকার অর্থে একটা উপশাখা হিসেবে এই নামটা ‘রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান’ পাওয়া গেল তখনই। কিন্তু – বিস্ময়কর হ’ল তাতে আরো কট্টর ধরনের একটা শাস্ত্র দেখা দিল। আগে তবু দু’ একটা নমুনা ছিল যাতে কিছু সমালোচনা পাওয়া যায় ঔপনিবেশিক শাসনের। পরবর্তী কালে সেটাও আর তেমন দেখা দিল না।
বরং এই সময়কার কাজে মূলত ক্রিয়াবাদী ধারাতে সমাজ-সংস্কৃতির প্রথাগত ধারণা ঘুরপাক খেয়েছে। এই সময়কালের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানেও ক্ষমতা সম্পর্ক কিংবা রাজনৈতিক পরিবর্তনের আলোচনা অনুপস্থিত। এখানে মুখ্যত বিভিন্ন সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা এসেছে। বিভিন্ন সমাজ কথাটাকে এখানে একটু খতিয়ে দেখার দরকার আছে।
৪০-৬০-দশকের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান
আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই একটা পদ (term) ব্যবহার করতে থাকেন। তা হ’ল – সরল – সমাজ। যে সকল সমাজ আগে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্বাধীন হয়েছে তাদের সকলকে ‘সরল সমাজ’ বলা হয়েছে। এই শব্দটি পূর্বতন ‘আদিম সমাজ’-এর বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। কিন্তু আধুনিক সমাজ হচ্ছে অগ্রসর এবং সরল সমাজ হচ্ছে পশ্চাৎপদ – এই ধারণাটি তখনও কাজ করছে। সেই সরল সমাজগুলোর রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা আলোচ্য কালের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিল।
আগেই বলেছি যে এই সমাজগুলোর রাজনৈতিক বদল নিয়ে ভাবা হয়নি। বদল নিয়ে ভাবলে দেখা সম্ভব হ’ত কিভাবে ইউরোপীয় শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বলপূর্বক বদল ঘটিয়েছে। সেই আলোচনায় পরে আসবো। এটা জেনে রাখা দরকার এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলতে মূলত এই সময়কালের (৪০ – ৬০ দশক) গবেষণা কাজ এবং ভাবনা- চিন্তাকেই দেখা হয়ে থাকে। পাঠ্যপুস্তকগুলোতেও সাধারণভাবে এই সময়কালে গড়ে ওঠা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা করা হয়ে থাকে ।
কয়েকজন নৃবিজ্ঞানীর নাম আলাদা করে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার। যেমন: ই. আর. লীচ, মেয়ার ফোর্টস, ই. ই. ইভান্স প্রিচার্ড প্রমুখ। একটু পরের সময়ে ভিক্টর টার্নার, ম্যাক্স গ-াকম্যান কিংবা এফ. বেইলি’র নাম ও এই কাতারে চলে আসতে পারে। এই সময়ের কাজে মুখ্য তিনটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমটি আপনারা এর মধ্যেই জানেন। যদিও তাঁরা যে সমস্ত সমাজে গবেষণা করেছেন তার সবগুলোই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনাধীন, তবু তাঁদের কাজে সেই ঔপনিবেশিক রাজনীতি আলোচিত হয়নি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে: তাঁরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন।
অর্থাৎ, সেই সকল সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে জ্ঞাতিসম্পর্ক খুব গুরুত্ব বহন করে সেটাই ছিল তাঁদের যুক্তি। তৃতীয় বিষয়টা এটার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন – রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাঁরা সমাজ ও সংস্কৃতি হিসেবেই দেখেছেন। এটা করতে গিয়ে তাঁরা ‘রাষ্ট্র সমাজ বনাম রাষ্ট্রবিহীন সমাজ’ – এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিহীন সমাজে কিভাবে দ্বন্দ্ব- সংঘাত নিরসন করা হয়, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং অন্যান্য সমাজের সঙ্গে কিভাবে তারা সম্পর্ক রক্ষা করে – এই ব্যাপারে বর্ণনা করাই নৃবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব ছিল। আগেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
শেষ দুটো বৈশিষ্ট্যের কারণেই বহু সংখ্যক মার্কিন এবং ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এই ধারার রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আবার এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই ধারার রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান সমালোচিত হয়েছে। যে সকল নৃবিজ্ঞানী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা করেছেন তাদেঁর তত্ত্বকে ব্যবস্থা তত্ত্ব (system theory) বলা হয়ে থাকে। এর একটা সমালোচনা তো পরবর্তী কালে হয়েছে, ঐ সময়েই সক্রিয় তত্ত্ব (action theory) বলে একটা আর একটা ধারা জন্মলাভ করে। সেই ধারার নৃবিজ্ঞানীরাও তথাকথিত সরল সমাজেই গবেষণা করেছেন।
তবে তাঁরা একটা ধারণা তাঁদের গবেষণাতে এনেছিলেন। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে রাজনৈতিক লক্ষ্য। টার্নার, গ-াকম্যান এই ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা রাজনীতি বলতে দেখিয়েছেন মানুষজনের রাজনৈতিক লক্ষ্য চিহ্নিত করা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে ক্ষমতা ব্যবহার করা। অর্থাৎ তাঁরা দেখেছেন কিভাবে বিভিন্ন সমাজের মানুষজন তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেন।
আরও দেখুনঃ