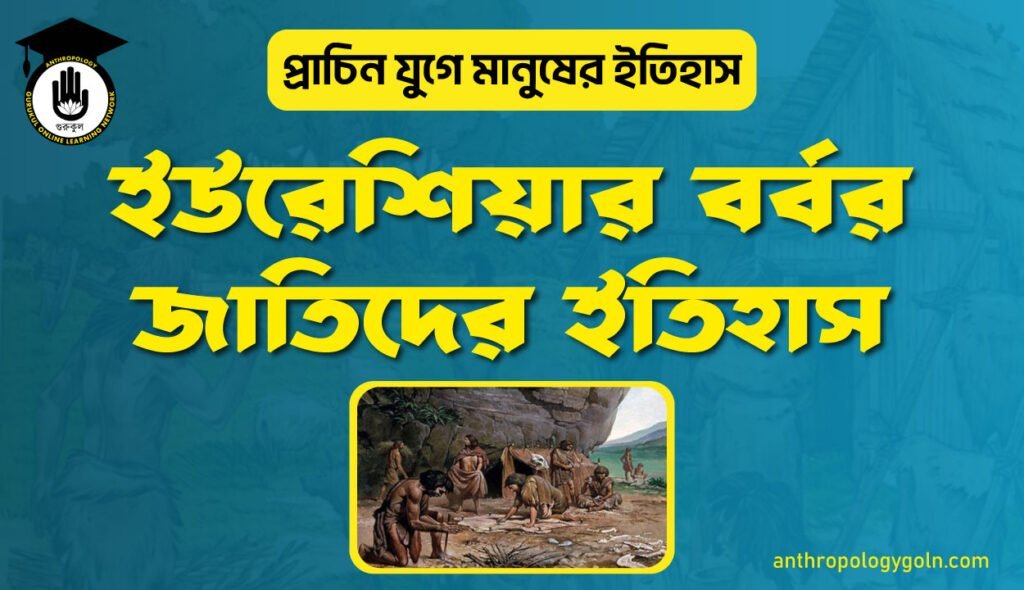আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ইউরেশিয়ার বর্বর জাতিদের ইতিহাস। ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশকে একত্রে ইউরেশিয়া বলা হয়। এর মোট আয়তন ৫,৪৭,৫৯,০০০ কি.মি.২ যার বেশিরভাগই পূর্ব এবং উত্তর গোলার্ধের মধ্যে পড়েছে। ইউরেশিয়ার উত্তরে উত্তর মহাসাগর; পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খাল ও আফ্রিকা মহাদেশ; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর।
ইউরেশিয়া পৃথিবীর মোট ভূভাগের ৩৬.২% জুড়ে রয়েছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৭২.৫% (প্রায় ৪৬০ কোটি) এ অংশেই বসবাস করে।
ইউরেশিয়ার বর্বর জাতিদের ইতিহাস
ইউরেশিয়ার বর্বর জাতিদের ইতিহাস
ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখেছি যে খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শতকে দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ছিল রোমক সাম্রাজ্যের লৌহযুগের সভ্যতা। ভারতবর্ষ, চীনে ছিল লৌহযুগের উচ্চ সভ্যতা। চীনের প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সে সময় লৌহযুগের সভ্যতা কিছু পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছিল। অপর পক্ষে, আমেরিকা মহাদেশে প্রায় সর্বত্র ছিল শিকারি সমাজ।
কোনো কোনো স্থানে কৃষিসমাজ; এবং কয়েকটি স্থানে ব্রোঞ্জযুগের তুল্য সমাজের (মায়া, আজটেক, ইনকা সভ্যতার উদয় ঘটেছিল। আমরা আরো দেখেছি যে, একই কালে অস্ট্রেলিয়াতে ছিল আদিম শিকারি সমাজ; ওশেনিয়াতে ছিল নতুন পাথরের যুগের কৃষিসমাজ; আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে ছিল নবোপলীয় যুগের কৃষিসমাজ ও স্থানে স্থানে শিকারি সমাজ। কিন্তু মধ্য ও উত্তর এশিয়া এবং মধ্য ও উত্তর ইউরোপের সমগ্র অঞ্চল এ হিসাব থেকে বাদ রয়ে গেছে।
অথচ ইউরেশিয়ার (ইউরোপ-এশিয়ার) এ অঞ্চলে আধুনিক কালের উন্নততম রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, এ অঞ্চলে রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানী, সুইডেন প্রভৃতি দেশ। খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে এসব অঞ্চল জনবিরল ছিল না। ইউরেশিয়ার এ ব্যাপক অঞ্চলে বিভিন্ন বর্বর জাতির মানুষ বাস করত। এ বর্বর সমাজের উদয় কেমন করে হল তা আলোচনা করা যাক। আমরা দেখেছি, পৃথিবীতে প্রথমে পুরানো পাথরের যুগের সংস্কৃতির উদয় হয়েছিল। এবং এ সংস্কৃতি সব কটি মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল।
প্রায় দশ হাজার বছর আগে নবোপলীয় (নতুন পাথরের যুগের) কৃষি সংস্কৃতির উদয় হওয়ার পর শিকারি সমাজ লোপ পায় এবং পৃথিবীর সর্বত্র কৃষি সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। তবে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও সস্কৃতিগত রক্ষণশীলতার দরুন অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে, আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে, এস্কিমোদের দেশে শিকারি যুগের সংস্কৃতি বজায় থেকে গিয়েছিল। নবোপলীয় সংস্কৃতি আবার নতুন করে এবং শিকারি সমাজের চেয়ে ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।
নবোপলীয় সংস্কৃতির প্রভাবে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার আদিম শিকারি সমাজ বিলুপ্ত হয় অথবা নবোপলীয় সমাজে রূপান্তরিত হয়। নবোপলীয় কৃষিসমাজ মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করলেও, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ লাভ করেনি। আর বরফাচ্ছন্ন তুন্দ্রা অঞ্চলে (এস্কিমোদের দেশে) নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির সুবিধা ছিল না বলে সেখানেও শিকারি সমাজই বজায় ছিল।
মধ্য এশিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে রয়েছে সুবিস্তৃত তৃণভূমি; কৃষিকাজ অসুবিধাজনক বলে সেসব অঞ্চলে পশুপালনের প্রথা বিস্তার লাভ করে। মনে থাকতে পারে যে, কৃষি ও পশুপালন হল নবোপলীয় অর্থনীতির দুটো প্রধান শাখা। মধ্য এশিয়ায় জমির অনুর্বরতা, চারণভূমির অভাব প্রভৃতি কারণে যাযাবর পশুপালক দলের উদয় হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সাত-আট হাজার বছর আগে এদের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম ছিল নবোপলীয় যুগেরই স্তরের।
কিন্তু তাদের নিকটবর্তী পারস্য, পশ্চিম এশিয়া, চীন প্রভৃতি সভ্যতার প্রভাবে এরা কালক্রমে ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের হাতিয়ার, সরঞ্জাম এবং কলাকৌশল সংগ্রহ ও আয়ত্ত করে। যেমন, মধ্য এশিয়ার বর্বর জনগোষ্ঠী ঘোড়ায় টানা চাকাওয়ালা গাড়ি, ব্রোঞ্জ ও লোহার অস্ত্র, ধাতুনির্মিত বর্ম, ঢাল প্রভৃতি আয়ত্ত করেছিল। মেসোপটেমিয়া ও অন্যান্য সভ্যতার কাছ থেকে বর্বররা যুদ্ধের কলাকৌশলও আয়ত্ত করেছিল।
ভ্যতার দ্বারা কিছু কিছু প্রভাবিত হলেও, এ সকল বর্বর সমাজের মানুষ নবোপলীয় যুগের ট্রাইব সমাজের নিয়মেই সংগঠিত ছিল। এ সকল যুদ্ধপ্রিয় যাযাবর- বর্বর গোষ্ঠী থেকেই বিভিন্ন সময়ে শক, হুন, মোঙ্গল প্রভৃতি গোষ্ঠীর উদয় হয়েছিল। মধ্যযুগের আলোচনাকালে আমরা এদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব।
আমরা উল্লেখ করেছি যে, নবোপলীয় যুগে ইউরোপেও কৃষি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের পার্বত্য ও বনময় জমিতে নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির খুব বেশি বিস্তার ঘটা সম্ভব ছিল না। কারণ নবোপলীয় হাতিয়ার ছিল খুবই অনুন্নত। পাথরের হাতিয়ার দিয়ে পার্বত্য জমি আবাদ করা বা গাছ কেটে বন পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। এমনকি ব্রোঞ্জের হাতিয়ার দিয়েও গাছ কাটা সম্ভব নয়।
ইউরোপে তাই লৌহযুগের আগে নবোপলীয় সংস্কৃতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেনি। লৌহযুগে যখন গ্রীস ও রোমের মানুষরা প্রাচীনকালের অতি উচ্চ সভ্যতা গড়ে তুলছিল, ইউরোপের মধ্য ও উত্তর অঞ্চলে তখন বর্বর সমাজের মানুষরা নবোপলীয় কৃষির বিস্তার ঘটাচ্ছিল। কিন্তু এ বর্বর সমাজ লৌহযুগের সভ্যতার অনেক কলাকৌশল এবং যুদ্ধবিদ্যাও আয়ত্ত করেছিল। স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী এ সকল বর্বর সমাজের মানুষরা নানাপ্রকার কলাকৌশল, বিদ্যা ও দক্ষতা অর্জন করেছিল।
এশিয়ার শক, হন, মোঙ্গল প্রভৃতি সব বর্বর জনগোষ্ঠীই ছিল অশ্বচালনায়, ধনুর্বাণ ব্যবহারে সুদক্ষ। আবার উত্তর ইউরোপ, নরওয়ে প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ ছিল জাহাজ নির্মাণে ও সমুদ্রবিদ্যায় পারদর্শী। অধিকাংশ বর্বর সমাজের মানুষই ছিল শিল্পকর্মে সুদক্ষ। তারা কাঠ, হাড়, সোনা, রূপা প্রভৃতি দিয়ে সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি ও গয়না তৈরি করতে পারত।
খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যখন দক্ষিণ ইউরোপের রোমক সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল, তখন রোমক সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে ডানিউব নদীর অপর পারে বর্বর সমাজের মানুষরা বাস করত। মধ্য ইউরোপে বাইন ও এল্ব্ নদীর মধ্যবর্তী অংশে বাস করত জার্মান নামে পরিচিত বর্বর জাতি। জার্মানরা ভ্যাঙাল, গথ, ফাঙ্ক, এ্যাংগল, স্যাক্সন প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত ছিল। জার্মান বর্বর জাতির আক্রমণেই পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল এবং এ বর্বর সমাজের মানুষরা বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল।
জার্মানদের পূর্ব দিকে এল্ব্ নদীর পূর্ব তীরে ছিল স্লাভ্ জাতির বর্বর জনগোষ্ঠী। স্নাভরা পরবর্তীকালে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব স্নাভরা হচ্ছে আধুনিক রুশ, ইউক্রেনীয় ও বাইলো কশদের পূর্ব-পুরুষ। পশ্চিম স্লাভদের থেকে উ উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক চেকোশ্লাভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের। দক্ষিণ স্লাভ জাতি থেকে উৎপত্তি হয়েছে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের।
নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কে যেসব বর্বর সমাজের মানুষ বাস করত তাদের একত্রে নাম দেওয়া হয়েছে ভাইকিং। এরা ডেন (অর্থাৎ ডেনমার্কবাসী) অথবা নর্স ম্যান বা নর্মান (অর্থাৎ নর্থ ম্যান বা উত্তরের মানুষ) নামেও পরিচিত। খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তারা চাষাবাদই করত। কিন্তু নবম শতাব্দীতে সর্বত্র সমুদ্রপথে যুদ্ধ ও লুটতরাজের অভিযান চালাতে শুরু করলে এরা ভাইকিং নামে পরিচিত হয় এবং সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে।
ভাইকিংরা সুদক্ষ নাবিক ছিল এবং স্থানীয় বনভূমির গাছ কেটে সুন্দর ও শক্ত জাহাজ নির্মাণ করতে পারত। এরা নানাপ্রকার লোহার অস্ত্র, ধাতুর হাতিয়ার এবং অলঙ্কার ও সুদৃশ্য দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারত। এশিয়া ইউরোপের বর্বর সমাজের মানুষদের পরিচয় আমরা দিলাম। এবা নবোপলীয় সমজের মানুষ হলেও, এরা ছিল লৌহযুগের সভ্যতার সমসাময়িক ও নিকট প্রতিবেশী। তাই এরা উন্নত সভ্যতার নানা উপকরণ ও উপাদান (লোহার হাতিয়ার প্রভৃতি।
টুকরো টুকরো ও বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তথাপি এরা ছিল মূলত নবোপলীয় বর্বর সমাজেরই মানুষ। এরা ছিল নবোপলীয় যুগের মতই ট্রাইব ও ক্ল্যানে সংগঠিত। এরা কৃষিকাজ এবং পশুপালনেই নিয়োজিত ছিল, তবে সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে যুদ্ধবিদ্যাও আয়ত্ত করেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিশর, মেসোপটেমিয়া, রোম প্রভৃতি সব সাম্রাজ্যই বিভিন্ন সময়ে বর্বর মানুষদের জোর করে ধরে এনে সৈন্যদলে ভর্তি করত।
এভাবেই সভ্য সমাজের রণকৌশল বর্বররা আয়ত্ত করেছিল। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইউরোপ এশিয়ার নানা সন্নিহিত অঞ্চলে উন্নত সভ্যতার বিস্তার ঘটা সত্ত্বেও, মধ্য এশিয়া ও মধ্য ইউরোপের বর্বর সমাজের মানুষরা কেন সভ্যতা নির্মাণ করেনি। এর দুটো কারণ সহজেই নির্দেশ করা চলে। প্রথমত, প্রাচীন ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের সভ্যতার অর্থনেতিক ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। একটা অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে, উর্বর ও ফলনশীল অঞ্চলে এর উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ সম্ভব ছিল।
এবং একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শোষণ করেই মাত্র ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের সভ্যতার একটা সংকীর্ণ সুবিধাভোগী শ্রেণী একটা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ সভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছিল। অপরপক্ষে, লৌহযুগের হাতিয়ার ও কারিগরি বিদ্যা হাতে পাওয়ায় ইউরেশিয়ার বর্বর সমাজ বলতে গেলে নবজীবন পেয়ে বিকাশ লাভ করেছিল।
অনুন্নত হাতিয়ারের দরুন সভ্য অঞ্চলে যখন নবোপলীয় সংস্কৃতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, তখন ইউরেশিয়ার বর্বর সমাজ লোহার হাতিয়ার, ধাতুর কারিগরি, উন্নত লাঙ্গল ও চাষের পদ্ধতি ইত্যাদি জ্ঞান সভ্যদের কাছ থেকে নিয়ে তার সাহায্যে নবোপলীয় সমাজ ও অর্থনীতি অব্যাহত রাখে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত রক্ষণশীলতার জন্য ইউরেশিয়ার বর্বর সমাজ গভীর সংকটে না পড়া পর্যন্ত তাদের সমাজ, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা ত্যাগ করতে পারছিল না।
প্রথম আমলের নবোপলীয় যুগে সারা পৃথিবীতে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটার পর জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করলে এ রকম সংকট দেখা দিয়েছিল। তা থেকে মানব সমাজ উদ্ধার পেয়েছিল ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ইউরোপীয় বর্বর সমাজ সভ্যতার নানা উপকরণ সংগ্রহ করে নবোপলীয় সমাজকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।
মাঝে মাঝে স্থানীয়ভাবে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বা অনাবৃষ্টির দরুন খাদ্যাভাব দেখা দিলে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার ফলেই মাঝে মাঝে ঘটেছে বর্বর আক্রমণ যেমন, শক, হুন ইত্যাদির বিজয় অভিযান। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপীয় বর্বর সমাজের নবোপলীয় অর্থনীতিতে মহাসংকট দেখা দেয়, প্রধানত জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন। কারণ নবোপলীয় অর্থনীতিতে এত বৃহৎ জনসংখ্যার পরিপোষণ আর সম্ভব হচ্ছিল না।
এ পরিস্থিতিতেই বর্বর আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এর পরই মাত্র লৌহযুগের কারিগরি আবিষ্কার এবং ইউরোপীয় বর্বর জনসমাজের আয়ত্তাধীন কলাকৌশলের সংমিশ্রণে ইউরোপে গড়ে ওঠে সামস্ত কৃষি অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। ইউরেশিয়ার অন্যান্য বর্বর জাতির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।
মধ্যযুগে স্নাভরা পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায়, শক ও হুনরা ভারতবর্ষে ও মধ্য এশিয়ায় কালক্রমে সামন্ত সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। গ্রামীণ কৃষি নির্ভর সামস্ত অর্থনীতি ছিল বর্বর সমাজের বা রোমক প্রভৃতি লৌহযুগের সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপকভিত্তিক ও শক্তিশালী। এ সামন্ত সমাজের ইতিহাস মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।