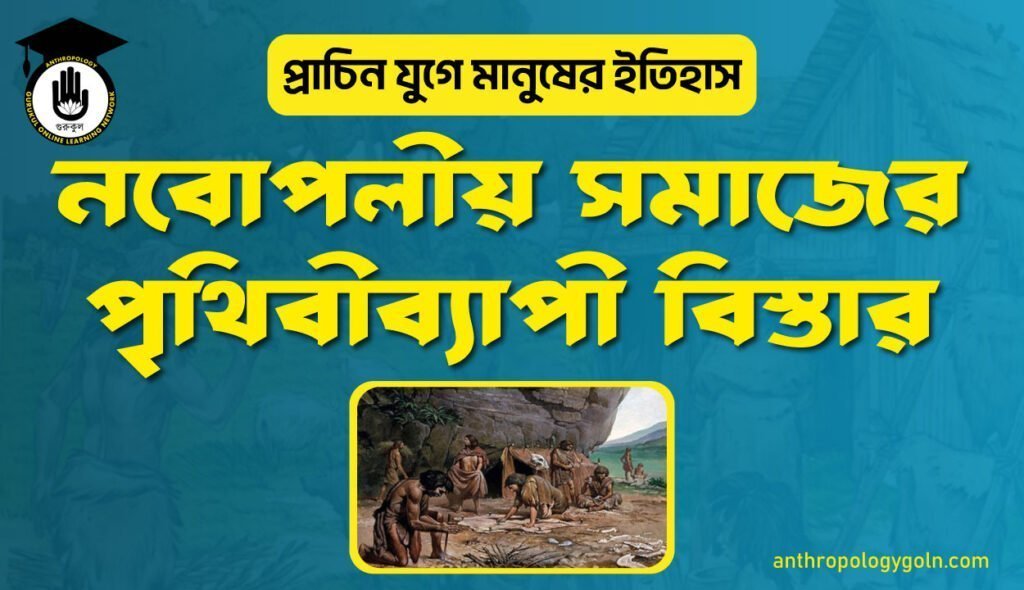আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নবোপলীয় সমাজের পৃথিবীব্যাপী বিস্তার
নবোপলীয় সমাজের পৃথিবীব্যাপী বিস্তার
নবোপলীয় সমাজের পৃথিবীব্যাপী বিস্তার
নতুন পাথরের যুগে সংস্কৃতি আরো এক কারণে মানবসভ্যতার পরবর্তী বিকাশের পক্ষে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রথম মানব সমাজ সত্যিকার অর্থে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য ‘উচ্চ পুরোপলীয় যুগেও শিকারী মানুষ পৃথিবীর সবকটি মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। তবে শিকারী মানুষরা বিভিন্ন মহাদশের মূল ভূখণ্ডের সুগম অঞ্চলেই বিস্তার লাভ করেছিল।
অপরপক্ষে নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির মানুষেরা পৃথিবীর সব আনাচে কানাচে, বরফাচ্ছন্ন তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে শুরু করে উষ্ণমণ্ডলের গভীর অরণ্য, সব জায়গাতেই বাস স্থাপন করেছিল। স্থলপথে এবং জলপথে অবিশ্বাস্য রকম দূরত্ব অতিক্রম করে মানুষ সারা পৃথিবীতে নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছিল। এমন কি এশিয়া ভূখণ্ড থেকে চার হাজার মাইল দূরের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত নতুন পাথরের যুগের মানুষের আওতার বাইরে ছিল না।
সারা পৃথিবীতে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম সংস্কৃতির বিস্তারের বিশেষ কারণ ছিল। আমরা আগেই দেখেছি কৃষিকাজ আয়ত্ত করার পর মানুষের খাদ্য সমস্যার একটা মোটামুটি স্থায়ী সমাধান হয়। খাদ্য উৎপাদন করতে শেখার ফলে মানুষের পক্ষে অনাহারে মারা যাওয়ার আশঙ্কা দূর হয়েছিল। আবার নবোপলীয় গ্রামে বৃদ্ধ বা শিশুরাও অপ্রয়োজনীয় ছিল না বা সমাজের উপর ভার স্বরূপ ছিল না।
জনসংখ্যা বাড়লেও কোনো বিপদ ছিল না, কারণ, বর্ধিত জনসংখ্যা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে পরত। এ অবস্থায় নতুন পাথরের যুগে অতিদ্রুত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক এক গ্রামে মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলে বাড়তি মানুষরা খানিক দূরে গিয়ে সুবিধা মত স্থানে আরেকটা গ্রাম স্থাপন করত। নতুন পাথরের যুগে গ্রামগুলো মূলত স্বনির্ভর হলেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা, পাথর ইত্যাদি অনেক সময় বাইরে থেকে আনতে হত।
এ সব পাথরের খনিতে যে সব বিশেষজ্ঞ কারিগর কাজ করত তারা অন্য অঞ্চলের শিকারী, কৃষিজীবী ও পশুপালকদের কাছ থেকে পশুর হাড়, শিং, কাঠ ইত্যাদি এনে তা’ দিয়ে খনি খোঁড়ার হাতিয়ার তৈরি করত। তাই এ কথা বলা চলে, নতুন পাথরের যুগে গ্রামগুলো স্বনির্ভর হলেও বাইরের জগতের সাথে যোগযোগশূন্য ছিল না। নতুন পাথরের যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ থাকত।
ব্যাবসা বাণিজ্য বলতে অবশ্য পণ্য বিনিময়ব্যবস্থারই তখন মাত্র প্রচলন হয়েছিল। যারা পাথরের হাতিয়ার বা নানা শখের জিনিস গ্রামবাসীদের কাছে বিক্রি করতে আসত তারা তার বিনিময়ে খাদ্যশস্য বা মাংস, পশু ইত্যাদি নিয়ে যেত। এই বিনিময়ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান ও ভাবনা চিন্তা ইত্যাদিরও আদান প্রদান হত। এসব ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী ইত্যাদির কাছ থেকেই সম্ভবত নতুন পাথরের যুগে গ্রামবাসীরা দূর দূর অঞ্চল সম্পর্কে খবর পেত।
এ সব সংবাদের ভিত্তিতে এক এক অঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বাড়তি মানুষরা দল বেঁধে নতুন স্থানে গিয়ে চাষাবাদের জন্যে সুবিধাজনক জায়গা দেখে বাস স্থাপন করত। এ ভাবে নতুন পাথরের যুগের মানুষরা পশ্চিম এশিয়া থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে, ইউরোপে, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এক এক অঞ্চলের মানুষরা নতুন নতুন সংস্কৃতি ও অভ্যাস আয়ত্ত করে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন পাথরের যুগে মানুষরা গম বা বার্লির পরিবর্তে ধানের চাষ আয়ত্ত করে। কারণ এ অঞ্চলের জলবায়ু ধান চাষের অনুকূল। আমেরিকা মহাদেশের নতুন পাথরের যুগের কৃষক সমাজ ভুট্টার চাষ আয়ত্ত করেছিল। যে সব অঞ্চলে চাষাবাদের সুযোগ নেই সেখানে মানুষ পশুপালন এবং ফলের আবাদে মন দেয়। এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ আঙুরের চাষ আয়ত্ত করে এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলের মানুষ জলপাই, আঙুর ইত্যাদির চাষে উৎকর্ষ অর্জন করে।
এ সকল নতুন পাথরের যুগের সমাজ আঙুরের রস থেকে মদ এবং জলপাই থেকে উ ৎকৃষ্ট তেল তৈরির কৌশলও আবিষ্কার করেছিল। আবার ভূমধ্যসাগরে যেমন জলপাই, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে তেমনি ছিল নারকেল। এ অঞ্চলের মানুষ নারকেল থেকে তেল বের করতে তো পারতই, নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি, নারকেল পাতা দিয়ে ঘর, ইত্যাদি তৈরি করতে শিখেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় একটা প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে, বছরে যতগুলো দিন আছে নারকেল গাছ তত রকম কাজে লাগে।
নতুন পাথরের যুগে সমাজে শিকারী যুগের সমাজ সংগঠন অনেকাংশে টিকে ছিল । কিন্তু তথাপি, নতুন পাথরের যুগের কৃষিনির্ভর সমাজের বস্তুগত ভিত্তি শিকারী যুগের তুলনায় আমূল পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন পাথরের যুগের সমাজে প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠান ও চিন্তাধারারও রূপান্তর ঘটে। নতুন পাথরের-যুগে সমাজের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে কৃষি উৎপাদন।
রূপান্তরিত টোটেম অনুষ্ঠানে মেয়েদের ভূমিকা বাড়ল এবং শস্য উৎপাদনের বিষয়টার ওপর জোর পড়ল। মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেয় এবং শস্যবীজ অনেক শস্যের জন্ম দেয়। তাই শস্যের ফলনবৃদ্ধির কামনায় মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের বিষয়টার ওপর জোর দেয়া হয় নতুন পাথরের যুগে সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানে। বৃষ্টির সাথে ফসলের ফলনের যে সম্পর্ক আছে এ কথা হয়তো মানুষ শিকারী যুগ থেকেই জানত।
কিন্তু নতুন পাথরের যুগে সম য়মতো বৃষ্টি হওয়াটা মানব সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠল। শিকারী যুগে যাদুকর-ওঝাদের মূল কাজ ছিল টোটেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করে পশুসম্পদ বৃদ্ধি করা। কিন্তু নতুন পাথরের কৃষি যুগে এ যাদুকর-ওঝাদের একটা মূল কাজ হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি নামানোর অনুষ্ঠান করা। নতুন পাথরের যুগের সমাজেও শিকারী যুগের মতোই মানুষেরা গোল হয়ে ঘুরে নাচত, গান গাইত। তবে, এখন আর পশুসম্পদ বৃদ্ধির কামনায় নয়।
এখন তারা নেচে গেয়ে বলত, বৃষ্টি হোক, ফসল ফলুক, ফুল ফুটুক ইত্যাদি। নতুন পাথরের যুগে শস্য রোপনের অনুষ্ঠান, নবান্নের অনুষ্ঠান, বসন্তের উৎসব ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠানের রেওয়াজ হয়। ফসলই নতুন পাথরের-যুগে গ্রামের প্রাণস্বরূপ ছিল বলে এ সব সমাজে ফসল-রানী ও ফসল-রাজা ইত্যাদি নির্বাচিত করার রেওয়াজ হয় এবং তাদের বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার দেয়া হয়। তা ছাড়া যাদুকর ও ওঝাদেরও সমাজে প্রাধান্য ছিল।
নতুন শস্য পেতে হলে মাটিতে বীজ বপন করতে হয় অর্থাৎ বীজকে হত্যা করতে হয়। এ ধারণা থেকেই সম্ভবত প্রথম বলিদানের প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের কল্যাণের জন্য ফসল-রাজাকেই বা তার প্রতিনিধিকে আত্মদান করতে হত। এ ছাড়া পশুবলি এবং নরবলি অর্থাৎ মানুষ বলিরও প্রচলন ঘটে। নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতি শিকারী যুগের বন্য অর্থনীতির তুলনায় উন্নত হলেও তার কতগুলো অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল।
প্রথম অবস্থায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকলেও কিছুকালের মধ্যেই তা একটা সঙ্কট সৃষ্টি করে। নতুন পাথরের যুগে গ্রামগুলো ছিল স্বনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এসব গ্রামে জনসংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেলে কিছু মানুষ নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন গ্রাম স্থাপন করত। এভাবে ছড়াতে ছড়াতে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম-সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। তখন দেখা দিল সঙ্কট। সঙ্কট অবশ্য ত্বরান্বিত হয়েছিল আরো একটা কারণে।
নতুন পাথরের যুগের গ্রাম-সংস্কৃতি যখন চারদিকে ছড়াতে লাগল তখন তার সংস্পর্শে এসে আদিম শিকারী মানুষরাও কৃষিকাজ আয়ত্ত করে নতুন পাথরের-যুগে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। পৃথিবীর নানা স্থানের বন্য-সংস্কৃতির মানুষ এভাবে নবোপলীয় সংস্কৃতি আয়ত্ত করার ফলে খুব দ্রুত অর্থাৎ কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সারা পৃথিবী নতুন পাথরের-যুগের গ্রামে পূর্ণ হয়ে গেল। এর পর নতুন গ্রাম স্থাপন করার মতো আর জায়গা যখন রইল না, তখন সঙ্কট দেখা দিল।
নতুন পাথরের-যুগের কৃষি অর্থনীতি শিকার অর্থনীতির চেয়ে উন্নত হলেও, আদিম পদ্ধতির কৃষিতে উৎপাদন ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ওপর নির্ভর করে যত মানুষ বাঁচতে পারত তার পরিমাণটা ছিল খুব সীমিত। তার ফলে মোটামুটি সারা পৃথিবীতে নতুন পাথরের-যুগের গ্রাম-সংস্কৃতির বিস্তার লাভের পর জন সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলে জমির জন্যে প্রতিযোগিতা বাড়তে লাগল।
এর ফলে ক্রমশ বিভিন্ন বর্বর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ-লড়াইয়ের সূত্রপাত হল। প্রথম অবস্থায় নতুন পাথরের-যুগে সংস্কৃতির মানুষ ছিল শান্তিপ্রিয়। তাদের হাতিয়ারের তালিকায় অস্ত্রের কোনো স্থানই ছিল না। অথচ ইউরোপে নতুন পাথরের-যুগের শেষ দিকে বর্বরসমাজে যুদ্ধের কুঠার, ফ্লিন্ট পাথরের ছোরা প্রভৃতির প্রচলন দেখা দেয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ রকম হানাহানি নতুন পাথরের যুগে অর্থনীতির সীমাবদ্ধতারই লক্ষণ।
এতে প্রমাণ হয় যে, নতুন পাথরের-যুগে অর্থনীতি নিজেই যে বিপুল পরিমাণ মানুষের উদয় ঘটিয়েছিল, তাকে পরিপোষণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। কারণ যুদ্ধের ফলে একদল মানুষের জমি, ফসল ও সম্পদ অন্য একদল মানুষ হয়তো দখল করতে পারে, কিন্তু তাতে মানব সমাজের আয়ত্তাধীন মোট সম্পদের পরিমাণ বাড়ে না। মারামারি-হানাহানিতে বরং জনসংখ্যা এবং সম্পদের হানি ঘটে।
নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতির আরেকটি ত্রুটি ছিল। এ ব্যবস্থায় খাদ্য উৎ- পাদন শিকারী যুগের তুলনায় অনেক উন্নত হলেও, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতি ছিল নিতান্তই অসহায়। অবশ্য নতুন পাথরের যুগে গ্রামসমূহে সব সময়েই শস্য ভাণ্ডারে পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য জমিয়ে রাখা হত। এ সঞ্চিত খাদ্য গ্রামের মানুষ দু’-এক বছর খেয়ে বাঁচতেও পারত। কিন্তু অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি বা তুষারপাতে পরপর কয়েক বছর শস্যহানি ঘটলে তার বিরুদ্ধে কোনো
মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত যাঁতা, অনেকটা আমাদের দেশের মশলা বাটার শিল নোড়ার মত ।
প্রতিকারের ব্যবস্থা নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতিতে ছিল না। গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন এবং স্বনির্ভর থাকায় এক গ্রামের বিপদে আরেক গ্রাম বিশেষ সাহায্যও করতে পারত না। পরপর কয়েক বছর শস্যহানি ঘটলে নতুন পাথরের যুগে তাই গ্রামের পর গ্রাম মড়ক লেগে উজাড় হয়ে যেত। সারা পৃথিবীতে নতুন পাথরের-যুগে অর্থনীতির বিস্তার ঘটার পর তাই দেখা গেল যে, নতুন পাথরের-যুগের অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যে থেকে আর সঙ্কট এড়ানো সম্ভব নয়।
এ গণ্ডি থেকে বের হয়ে যদি নতুন ও উচ্চতর অর্থনীতি মানুষ সৃষ্টি করতে না পারত তবে আজকের পৃথিবীও ছয় সাত হাজার বছর আগের মতো জনবিরল অবস্থায় থাকত। এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির মাত্রাও তার বেশি অগ্রসর হতে পারত না। কিন্তু নতুন পাথরের যুগে অর্থনীতির গণ্ডি অতিক্রম করার পক্ষে ঐ অর্থনীতিই আবার বাধাও সৃষ্টি করেছে। নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতি ছিল স্বনির্ভর একথা আমরা আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি।
নতুন পাথরের যুগে গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই নিজেরা তৈরি করতে পারত। ফলে নতুন পাথরের-যুগে মানুষদের মধ্যে বৈষয়িক উন্নতি সাধনের কোনো প্রেরণা ছিল না। খাওয়া-পরা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি জীবনের মোট প্রয়োজনগুলো মেটানোর পন্থা তারা আবিষ্কার করেছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর অর্থনীতিতে তাদের কোনো অভাব ছিল না। অভাব বা অপূর্ণতা বোধ না থাকায় তাদের জীবনে কোনো সমস্যা ছিল না।
তাই সমস্যার সমাধানের কথাও তাদের চিন্তায় কখনো আসেনি। প্রথম প্রথম যখন গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে যেত, তারা নতুন গ্রাম স্থাপন করে সে সমস্যার সমাধান করেছে। এ সমাধান ছিল নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যেই। কিন্তু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পর যখন সঙ্কট তীব্র আকারে দেখা দিল তখনো মানুষ নতুন পাথরের-যুগে গ্রামের গণ্ডির ভেতর বাস করার ফলে নতুন সমাধানের কথা ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়নি।
হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ একই ধরনের গ্রামে,একই রকম উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত থেকেছে, একই রকম প্রথাগত চিন্তায় লিপ্ত থেকেছে, একই রকম আচারণ-অনুষ্ঠান ব্রত পালন করেছে। কিন্তু স্বনির্ভর নতুন পাথরের-যুগের গ্রামের অর্থনীতির গণ্ডি ছেড়ে বের হতে পারেনি।
অবশেষে আজ থেকে ছয় সাত হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার কোনো কোনো স্থানে মানুষ অনুকূল পরিবেশে এবং নানাবিধ সামাজিক ও প্রাকৃতিক কারণের সন্নিপাতে নতুন পাথরের যুগের গ্রামীণ অর্থনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বিষয়ে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।