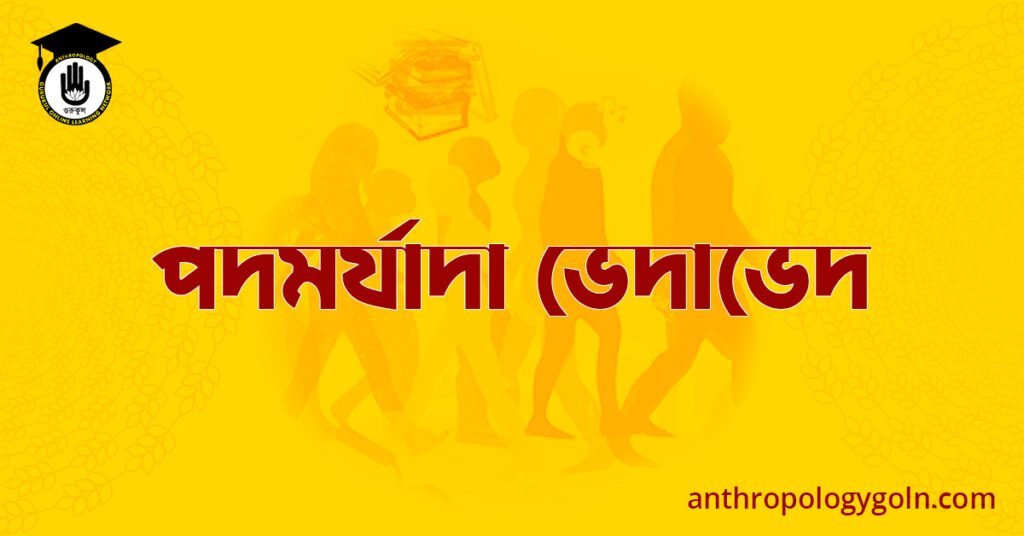আজকে আমরা আলোচনা করবো পদমর্যাদা ভেদাভেদ নিয়ে। এই ইউনিটের শুরুর দুই পাঠ থেকে আপনারা জানেন যে বয়স এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন সমাজে আছে। এই বিভাজন নানা সমাজে এবং নানা কালে বিভিন্ন রকম। আপনারা এও জেনেছেন যে, এই বিভাজন কখনো কখনো নিছক সংঘকেন্দ্রিক হলেও, কখনো কখনো দায়িত্ব ভাগ বণ্টন করে নেয়ার জন্য হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক বা ভেদাভেদমূলক।
পদমর্যাদা ভেদাভেদ
অর্থাৎ, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে সদস্যদের কোন কোন অংশের প্রতি বঞ্চনা হয়ে থাকে। নৃবিজ্ঞানীরা সমাজে এই ভেদাভেদ বা বৈষম্য নিয়ে গোড়া থেকেই মনোযোগ দিয়েছেন। বৈষম্যের ভিত্তিতে তিন ধরনের সমাজকে চিহ্নিত করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। সেগুলো হচ্ছে: সমতা ভিত্তিক সমাজ (egalitarian society), পদসোপানিক সমাজ (rank society) এবং শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ (class society)। ভেদাভেদের ক্ষেত্রে কেবল বয়স বা লিঙ্গ কাজ করে তা নয়।
কোন সমাজের সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য আছে কিনা কিংবা কিভাবে বৈষম্য কাজ করছে তা বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানীরা তিনটি ধারণা ব্যবহার করেছেন – আর্থিক সম্পদ, ক্ষমতা এবং মর্যাদা বা সম্মান। এগুলির ভিত্তিতেই সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভেদাভেদ কাজ করে।
সমতা ভিত্তিক সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ, মর্যাদা এবং ক্ষমতার কোন ভেদাভেদ কাজ করে না। নৃবিজ্ঞানীরা অবশ্য পরিষ্কার করেছেন, এর মানে এই নয় যে কোন ধরনের বাড়তি মর্যাদা কেউই লাভ করেন না এসব সমাজে। মূল ব্যাপার হচ্ছে এই ধরনের সমাজে কোন সদস্য সম্পদ, মর্যাদা বা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে পারেন না, কিংবা বেশি পরিমাণে দখল নিতে পারেন না। অবশ্যই সামাজিক মর্যাদার কতগুলি জায়গা আছে। যেমন: বিভিন্ন কাজে নানা ধরনের দক্ষতা থাকলে তা সেই সমাজের মধ্যে বাড়তি সম্মান বয়ে আনে। শিকার করা কিংবা অস্ত্র বানানো ইত্যাদি।
এছাড়া অভিজ্ঞতার কারণে সম্মান পেতে পারেন মুরুব্বীরা। আবার কেউ যদি সুবক্তা হন, কোন একটা ব্যাপার স্পষ্ট করতে পারেন — তাঁকেও অন্য সদস্যরা কদর করে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের সমাজে কোন সদস্যেরই বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জিনিস পাবার ক্ষেত্রে অন্য কেউ বাধা দেন না। কেউ কাউকে শোষণ করা বা ঠকানোর চেষ্টা করেন না। জীবন ধারণের মৌলিক সব দ্রব্যই এখানে সকল সদস্য সমান ভাবে ভোগ করে থাকেন। সেটাই সামাজিক ব্যবস্থা।
এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই ধরনের সমাজকে সমতা ভিত্তিক সমাজ বলা হয়ে থাকে। এখানে বয়স বা লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক সংঘ সাধারণত থাকে। কিন্তু সেগুলি কোনটার থেকে কোনটা বাড়তি সুবিধা নিয়ে জীবন যাপন করে না। কিংবা যাঁরা সমাজে নিজেদের দক্ষতা-যোগ্যতার কারণে বাড়তি সম্মান লাভ করেন – তাঁরা সেই সম্মানের জোরে কোন কিছু বাড়তি ভোগদখল করেন – না।
এই ধরনের সমতা ভিত্তিক সমাজ নৃবিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন তাঁদের গবেষণার সময়কালে। প্রথম যুগের নৃবিজ্ঞানীরা সরল সমাজে গবেষণা করেছেন। এই সব সরল সমাজের বড় একটা অংশই সমতা ভিত্তিক ব্যবস্থাতে পরিচালিত হ’ত। ইউরোপীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবার আগে সেগুলো বজায়ও ছিল। নৃবিজ্ঞানীদের বর্ণনা মতে শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের প্রায় সবগুলিতেই এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। সমাজের সকল সদস্যদের খাদ্য ভাগাভাগি করে খাবার বাধ্যবাধকতা ছিল। আর কোন কিছুর উপরই কেউ কোন ধরনের স্থায়ী কোন দখল তৈরি করতে পারতেন না।
তবে কিছু কিছু শিকারী- সংগ্রহকারী সমাজ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন যেখানে সমতা ভিত্তিক সমাজের বদলে পদসোপানিক সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিল। যেমন: ইনুইতদের কিছু কিছু দলের মধ্যে সম্পদ জড়ো করবার প্রক্রিয়া তৈরি হচ্ছিল। যে সব দলের কাছে তিমি শিকার খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁদের কেউ কেউ নৌকা, হাতিয়ার ইত্যাদির মালিক হয়েছিল এবং শিকারে অন্যদের চেয়ে বাড়তি সুবিধা পেত।
মার্কিন ভূখন্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় মৎসজীবী জাতির মধ্যেও সমতা ভিত্তিক সমাজ চালু ছিল না, ছিল । পদসোপানিক ব্যবস্থা চালু কী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোন সমাজকে সমতা ভিত্তিক, পদসোপানিক কিংবা শ্রেণী সমাজ বলা হয়ে থাকে তা একটা ছকের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব। যদিও এই ছকের মাধ্যমে বিষয়টাকে যত সহজ করে ফেলা হয়েছে বাস্তবে সমাজ জীবনে বৈষম্য তার থেকে অনেক জটিল বিষয়। কিন্তু ছকটির মাধ্যমে বুঝতে সুবিধা হবে নৃবিজ্ঞানের বই-পুস্তকে সমাজের ভেদাভেদ নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ।
পদসোপানিক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় যে ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে মর্যাদার পার্থক্য থাকে। পদসোপানিক সমাজের সদস্যরা পরস্পর মর্যাদার দিক থেকে ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও তাঁদের মধ্যে সম্পদের মৌলিক কোন তারতম্য থাকে না। যে সকল সমাজে নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন সেখানে চীফ বা প্রধানের পদ দেখা গেছে। তাঁর মর্যাদাও সমাজে স্বীকৃত। তিনি মহাভোজ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জিনিসপত্র পুনর্বণ্টন করে থাকতেন। এই দায়িত্বটা সমাজে খুব সম্মানজনক হিসেবে গণ্য। পুনর্বণ্টন বলতে একটা বিনিময় ব্যবস্থা আপনারা অর্থনৈতিক সংগঠন অংশে দেখতে পারবেন।
যদিও এই সকল সমাজে চীফের পদ খুবই সম্মানজনক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কোনভাবেই খাদ্য বা দ্রব্যাদি নিজের জন্য সঞ্চয় করে থাকেন না। জীবন যাপনের মৌলিক অর্থ কোনক্রমেই ভিন্ন নয় চীফ এবং সাধারণ মানুষজনের মধ্যে। পদসোপানিক সমাজে চীফ বা মুখিয়ার পদ অনেক মর্যাদাসম্পন্ন। কেবল তাই নয়, বরং জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মর্যাদার তারতম্য কাজ করে। চীফের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় স্বজনেরা বংশানুক্রমিকভাবে বেশি মর্যাদা লাভ করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ম কার আগে হচ্ছে সেই বিচারেও মর্যাদার তারতম্য কাজ করতে পারে।
অধিকাংশ পদসোপানিক সমাজ পশুপালন এবং চাষবাসকেন্দ্রিক বলে জানা যায়। তবে কিছু সাধারণ পদসোপান অনেক শিকারী সমাজেও লক্ষ্য করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। সবচেয়ে জটিল ধরনের পদসোপানিক ব্যবস্থা পাওয়া গেছে মার্কিন ভূখন্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের জাতিসমূহের মধ্যে। এসব সমাজের সদস্যদের অবস্থানের মধ্যে মর্যাদার ভেদাভেদ গভীরভাবে ঠিক করা থাকে। নূটকাদের মধ্যে সমস্ত আর্থিক সম্পদ দেখভাল করার দায়িত্ব থাকে আলাদা আলাদা। এই দায়িত্ব সব সময় বড় ছেলের উপর বর্তায়। মর্যাদার এই পার্থক্য ধরা পড়ে কিছু আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। যেমন: বিশেষ ভাবে নাম ব্যবহার করা, কোন একটা উৎসবে বিশেষ দায়িত্ব পালন, বিশেষ কোন পোশাক পরা ইত্যাদি।
তবে কেবল চীফ বা মুখিয়াই কোন অলঙ্কার পরতে পারেন। কোন জ্ঞাতি দলের প্রধান আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের কারণে কিছু বাড়তি প্রতীকী সুবিধা পেতে পারেন। যেমন সামুদ্রিক কোন মাছের মুড়ো, কম্বল কিংবা পশম। এভাবে যে দ্রব্যগুলো পান সেগুলোই তিনি আবার ‘পটল্যাচ’ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেন। (পটল্যাচ প্রথার বিস্তারিত আলোচনা ইউনিট ৬-এর ৩নং পাঠে পাবেন।)
কাছাকাছি ধরনের পদসোপানিক ব্যবস্থা দেখা যায় তাহিতিদের মধ্যে। এই সমাজে চীফের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র ধরে পদসোপান নির্ধারিত। এই মর্যাদাভেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অর্থ আছে তাহিতিদের মাঝে। সেখানে ভাবা হ’ত সমাজের প্রত্যেক মানুষেরই একটা অলৌকিক শক্তি আছে
মানা। এই মানা কার কতটা থাকবে তা নির্ভর করে তার পদমর্যাদার ওপর। চীফের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়দের মানা সবচেয়ে বেশি থাকবে। কিছু পলিনেশীয় দ্বীপে সর্বোচ্চ প্রধানকে সবকিছু থেকে আলাদা রাখা হ’ত। এমনকি তিনি এমন এক ভাষা ব্যবহার করতেন যা সমাজের অন্যরা ব্যবহার করবার অনুমতি পেতেন না। মেলানেশিয়ার কিছু দ্বীপে উঁচু মর্যাদার কাউকে সম্মান প্রদর্শন করবার নজির আছে মাথা নিচু করে। যদি প্রধান দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর সামনে দিয়ে যাবার সময়ে অন্যরা মাথা নিচু করে সম্মান দেখাবেন। সেটাই রেওয়াজ। কোন কোন পদসোপানিক সমাজে চীফকে দেখে মনে হতে পারে তিনি আসলেই বোধহয় সম্পদশালী।
তাঁদের বাসস্থান বড় হতে পারে, কিছু দ্রব্যাদি বাড়তি থাকতে পারে। অনেক সময় হয়তো সমাজের অন্যরা চীফকেই জমির ‘মালিক’ বলছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই সেই জমি ব্যবহার করতে পারতেন। আর এই শব্দ দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে মালিক বোঝায় না। এটা সম্মান দেখানোর জন্য। আবার তাঁর বড় আবাসস্থান আছে এই কারণে যে সেখানে ভোজের জন্য কিংবা অন্য কোন উৎসবের জন্য ঘর ব্যবহার করা হয়।
পদসোপানিক সমাজ বলতে যে সকল অ-ইউরোপীয় সমাজের কথা বলা হয়েছে সেখানে মর্যাদার ভেদাভেদ আছে, কিন্তু সমাজে এক দল মানুষ অন্য দলকে শোষণ করছে না। কিংবা কারো পক্ষে সম্পদের পাহাড় বানাবার সুযোগ নেই। ফলে স্তর বিন্যস্ত বা শ্রেণী বিভক্ত সমাজের চেয়ে এই ধরনের সমাজ স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র।
পদমর্যাদা ভেদাভেদ অধ্যায়ের সারাংশ:
আজকের আলোচনার বিষয়পদমর্যাদা ভেদাভেদ অধ্যায়ের সারাংশ – যা পদমর্যাদা- ভেদাভেদ এর অর্ন্তভুক্ত, নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই সমাজের সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য বিভেদের ভিত্তিতে তিন ধরনের সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন। সমতাভিত্তিক, পদসোপানিক এবং শ্রেণীভিত্তিক।
যে সকল সমাজে সদস্যদের মধ্যে মর্যাদায় তারতম্য আছে তাকে পদসোপানিক সমাজ বলা হয়। এর মানে হচ্ছে সদস্যদের মধ্যে সম্পদের তেমন তারতম্য নেই। এবং একদল মানুষ অন্যদের শোষণ করেন না। আধুনিক সমাজে শ্রেণী বিভেদের পাশাপাশি মর্যাদার ভেদাভেদ অত্যন্ত তীব্র। নগর সমাজে যত বেশি পরিমাণে ভোগ্যপণ্য খরিদ করা হয় ততই বেশি মর্যাদাবান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শ্রেণীর সঙ্গে মর্যাদার প্রসঙ্গ মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
আরও দেখুনঃ