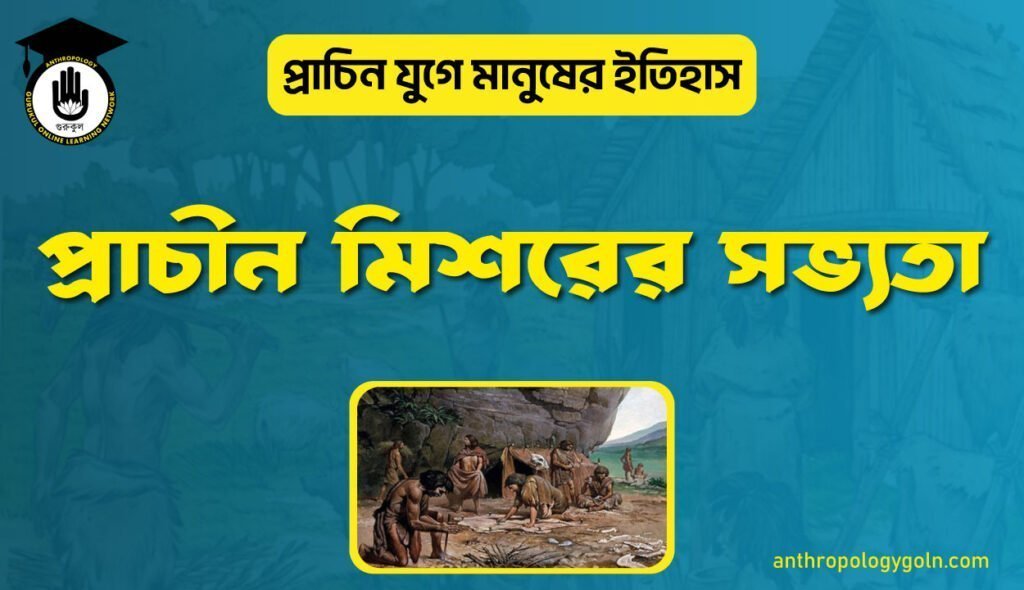আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় প্রাচীন মিশরের সভ্যতা
প্রাচীন মিশরের সভ্যতা
প্রাচীন মিশরের সভ্যতা
আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে অর্থাৎ ৫০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম-সংস্কৃতির বিলোপ ঘটে এবং তার স্থানে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার উদয় হয়। যতদূর জানা গেছে, মিশর এবং মেসোপটেমিয়াতে প্রায় একই সময়ে নগর সভ্যতার উদয় হয়েছিল। বর্তমানে যে অঞ্চলে ইরাক রাষ্ট্র অবস্থিত, তারই প্রাচীন নাম হচ্ছে মেসোপটেমিয়া।
এ দুই অঞ্চলের মধ্যে মেসোপটেমিয়াতেই সম্ভবত সভ্যতার উদয় প্রথম ঘটেছিল। কারণ মেসোপটেমিয়ার আদি সভ্যতার নানা প্রভাব মিশরের সভ্যতার ওপর দেখা যায়। অবশ্য এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে সভ্যতার উদয় হওয়া বিচিত্র নয়।
কিন্তু অনেক ইতিহাসবিদ আবার মনে করেন যে, সভ্যতার মৌলিক ও জটিল উপকরণসমূহ এক এক স্থানে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হয়েছে, সেখান থেকে অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হয়েছে। যেমন ধাতু ও ধাতুশিল্পের আবিষ্কার, লেখনপদ্ধতির আবিষ্কার, ইত্যাদি। লেখনপদ্ধতি যদিও প্রায় একই সময়ে মেসোপটেমিয়া, মিশরে প্রচলিত হয়েছিল, লেনার্ড উলি প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিমত অনুসারে মেসোপটেমিয়াতেই এর উদ্ভাবন ঘটেছিল, পরে মিশরে তার প্রচলন ঘটে।
এ সকল বিষয়ে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব। তবে মিশর মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলেও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতায় মিশরের নিজস্ব অবদানও যথেষ্ট রয়েছে। ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতায় মেসোটেমিয়ায় সভ্যতার পূর্বগামিতার দাবি থাকলেও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার কতগুলো বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের সুবিধা হবে বলে আমরা মিশরের সভ্যতার বিবরণ প্রথমে প্রদান করেছি।
নতুন পাথরের যুগে পৃথিবীর সব অঞ্চলে নতুন পাথরের যুগের স্বনির্ভর গ্রামের বিস্তার ঘটলেও কোনো কোনো জায়গায় তা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। নীলনদ যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেই ব-দ্বীপ অঞ্চলে আর দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী যেখানে পারস্য উপসাগরে পড়েছে সেখানে তখন ছিল জলাভূমি আর নলখাগড়া ইত্যাদির জঙ্গল। আবার এসব নদীতে জুন জুলাই আগস্ট মাসে বন্যা হত এবং তারপর ক্রমশ মাটি শুকিয়ে যেত।
এ সকল নদীর অববাহিকায় কৃষিকাজ করতে হলে তাই প্রয়োজন ছিল বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা, বাঁধ দিয়ে জলাভূমি থেকে জমি উদ্ধার করা, খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। কিন্তু নতুন পাথরের যুগের স্বনির্ভর গ্রামের পক্ষে এসব কাজ করা সম্ভব ছিল না। দশ বিশ বা পঞ্চাশ একশটি গ্রামের লোক একসাথে মিলে কাজ করলে তবেই এ ধরনের ব্যাপক আকারের সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি সংগঠিত করা সম্ভব।
আবার নতুন পাথরের যুগে সংস্কৃতি অনেকদূর অগ্রসর হবার আগে এজন্যে প্রয়োজনীয় সমাজ সংগঠন এবং কারিগরিবিদ্যা `ও যন্ত্রপাতিরও সৃষ্টি হয়নি। কালক্রমে নীলনদ বা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকার মানুষরা কয়েক গ্রামের মানুষ মিলে এক একটা অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে জমি উদ্ধার করে বা খাল কেটে পানিসেচ দিয়ে দেখতে পেল যে, এর ফলে নতুন জায়গায়ও আবাদ করা যায়, আবার প্রতি বছর বন্যার ফলে জমির উর্বরতাও বাড়ে।
এভাবে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম থেকে পৃথক আরেক ধরনের সমাজের সূত্রপাত হল। এ সমাজে গ্রাম আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল একক থাকল না। নতুন ব্যবস্থায় অনেক গ্রামের মানুষ মিলে নতুন একটি অর্থনীতি গড়ে তুলল। এ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে নগর।
প্রাচীন মিশরের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন ছিল, তার ফলেই সেখানে নগর সভ্যতার প্রথম উৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল।
মোহনার কাছাকাছি নীল অববাহিকায় ছিল প্যাপিরাস জাতীয় নলখাগড়ার জঙ্গল এবং খেজুর, ডুমুর ইত্যাদি নানা গাছ। এসব গাছ থেকে আবার ঘরবাড়ি তৈরির নানা সরঞ্জাম পাওয়া যেত। নীলনদের পূর্ব পাশে ছিল নুবিয়া মরুভূমি আর পশ্চিম পাশে ছিল লিবিয়ার মরুভূমি। কিন্তু প্রতি বছর বন্যা হবার ফলে নীল অববাহিকা ছিল রীতিমতো উর্বর পলিভূমি। এখানে তাই সহজে কৃষিকাজ করা চলতে পারত।
আশেপাশের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রানাইট, চুনাপাথর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ছিল আর নুবিয়ার পাহাড়ে ছিল প্রচুর সোনা। এক কথায়, নীল অববাহিকা ছিল উর্বর এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। নীল অববাহিকায় মানুষ অনেক প্রাচীন কাল থেকেই বসতি স্থাপন করে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এখানে কৃষিকাজ বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। বাঁধ দিয়ে জলাভূমি থেকে জমি উদ্ধার না করলে এবং খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা না করলে এখানে লাভজনক ভাবে চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না।
বিচ্ছিন্নভাবে কোনো পরিবার বা কোনো গ্রামের লোকের পক্ষে এত বড় কাজ করা সম্ভব ছিল না। আবার অল্প পরিমাণ জমির জন্যে এত ব্যাপক ব্যবস্থা করাও লাভজনক নয়। নীল অববাহিকায় তাই ক্রমশ অনেকগুলো ক্ল্যান বা গ্রামের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে এক একটা এলাকায় বাঁধ দিয়ে খাল কেটে জলসেচ করে জমিচাষের ব্যবস্থা করে। এসব সংগঠনকে বলা হত ‘নোম’। আসলে অনেকগুলো নতুন পাথরের যুগের গ্রামকে নিয়ে এক একটি নোম গড়ে উঠেছিল।
তবে নোমকে একটা বড় গ্রাম বলা চলে না। নোমকে বলা চলে একটা নগররাষ্ট্র। কারণ, এদের অর্থনৈতিক সংগঠন ছিল গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নতুন পাথরের যুগের গ্রামে যেমন সব পরিবার খাদ্য উৎপাদন এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কাজ করত, নগররাষ্ট্রে তা হত না। নীল অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ, সেচ ইত্যাদি পরিচালনার জন্যে কারিগর, শ্রমিক, পরিচালক ইত্যাদি অনেক ধরনের মানুষ দরকার হত।
এরা খাদ্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারত না অর্থাৎ চাষাবাদে সময় দিতে পারত না। কিন্তু এদের কাজের ফলে বেশি বেশি ফসল ফলানো সম্ভব হত। নগরের মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা খাদ্য উৎপাদন করে না, কিন্তু এমন সব বিশেষ ধরনের কাজ করে, যা সমাজের পক্ষে এবং খাদ্য উৎপাদনের পক্ষে জরুরি। নতুন পাথরের যুগের প্রথম পর্যায়ে সমাজের সবাই মিলে যে শস্য উৎপাদন করত সবাই মিলে তা খেয়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকত।
ক্রমে লাঙ্গল ইত্যাদির প্রচলন হবার পর অল্প লোক মিলেই অনেক খাদ্য উৎপাদন করত। তাই, নগরবাসী কারিগররা কৃষকদের উৎপন্ন . উদ্বৃত্ত শস্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে৷ এ সুযোগ সৃষ্টি হবার পরই কেবল নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্ম হতে পেরেছিল। তা ছাড়া, তামা ও লোহার হাতিয়ার, মাল পরিবহণের জন্য গাড়ি ও নৌকোর আবিষ্কার ইত্যাদি ছাড়াও নগর সভ্যতার জন্ম হতে পারত না। এক একটি নোম বা নগররাষ্ট্র প্রথমে সম্ভবত ঃ গড়ে উঠেছিল কয়েকটি করে গ্রাম নিয়ে।
মাঝামাঝি অবস্থানের একটা গ্রামে, যেটাতে যাদুকর-ওঝার বাস বা যেখানে টোটেম দেবতা থাকেন, সেখানেই হয়তো সব গ্রামের উদ্বৃত্ত ফসল ইত্যাদি জড়ো করা হত। সেখান থেকেই হয়তো পরিচালক মানুষরা সব কাজের পরিকল্পনা নিত, কাজ সংগঠিত করত। কাজ অর্থ অবশ্য খাল কাটা, বাঁধ দেয়া ইত্যাদি। প্রথম প্রথম যারা সর্দার ছিল তারাই ক্রমশ নোম-এর শাসক হয়ে দাঁড়ায়। শাসক ও শাসকশ্রেণীর প্রবর্তন নগর সভ্যতার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
শিকারী যুগে এবং নতুন পাথরের কৃষি যুগে সব মানুষের মধ্যে একটা সমতা ছিল। কিন্তু নগর সভ্যতার যুগের কিছু মানুষ সমাজ সংগঠন পরিচালনার এবং বিভিন্ন নির্মাণকাজ পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আদিম সমাজে যারা যাদুকর, ওঝা, সর্দার প্রভৃতি ছিল তাদেরই বংশধররা সম্ভবত ক্রমশ সমাজ পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ পুরোহিত হয়ে ওঠে। প্রাচীন পুরোহিতরাই ধর্ম-কর্ম পরিচালনা করত, অর্থনৈতিক পরিচালনার কাজও করত।
সেকালে ধর্ম-আচরণ ছিল অন্য সব কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ পুরোহিতশ্রেণী ও শাসকরা মিলে নগর সভ্যতার শুরুর যুগে মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি করে। প্রথম অবস্থায় অবশ্য এদের দায়িত্ব ছিল সমাজের উদ্বৃত্ত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার ভাগ বন্টনের ব্যবস্থা করা; ক্রমশ নগরের পরিচালকেরা এসব উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সমাজে ধনবৈষম্য দেখা দেয়। নগরগুলো তখন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
পুরোহিত ও শাসকরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ও অর্থনৈতিক কাজ করার জন্যে কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। এজন্য সিপাই-সান্ত্রী প্রভৃতিরও সৃষ্টি হয়। সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে পাহারাদারেরও সৃষ্টি হয়। এ পাহারাদাররাই সিপাই-সান্ত্রী। তবে ধনী ও অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল একথা ভাবা ঠিক নয়।
আমরা এর আগে সমাজের ভাবাদর্শের কথা আলোচনা করেছি। নতুন পাথরের যুগ পর্যন্ত সব মানুষের মধ্যে সততা বজায় ছিল এবং সাম্যের চিন্তাও ছিল। তাহলে নগররাষ্ট্রের উৎপত্তির সাথে সাথে সে সব সৎ মানুষদের মধ্যে ধনলোভ এবং শোষণ ও কর্তৃত্বের চিন্তা এল কোথা থেকে? নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, আমাদের সমাজে সমানুষও আছে, চোর ডাকাতও আছে।
কিন্তু সত্যিকারের সৎ মানুষরা সুযোগ পেলেও চুরি করে না, নরহত্যা করে না, কারণ তার চিন্তার মধ্যেই সে প্রবণতা নেই। তাহলে আদিম সমাজের নির্লোভ ও সাম্যবাদী মানুষদের মধ্যে ধনলোভ, শ্রেণী ভাগের চিন্তা ইত্যাদি এল কেমন করে? আসলে নগরসভ্যতার উৎপত্তির যুগে বাস্তব অবস্থাটাই ছিল সমাজে শ্রেণীভেদের উৎপত্তির অনুকূল।
এ দাসদের দিয়ে সবচেয়ে কঠিন কঠিন কাজ করানো হত, কিন্তু বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক লাভ বা সুফল ভোগ করা তাদের কপালে ছিল না। কারণ দাসরা ছিল সর্বাংশে তাদের মনিবের সম্পত্তি। দাসরা পরিশ্রম করে যে সব শস্য বা সম্পদ উৎপন্ন করত— দাসদের মালিকরা তা আত্মসাৎ করত। তা ছাড়া রাষ্ট্রের অর্থাৎ পুরোহিতশ্রেণী বা রাজার কর্তৃত্বাধীনেও অনেক দাস থাকত। খনি বা খাত থেকে সোনা ও অন্যান্য ধাতু, পাথর প্রভৃতি সংগ্রহের কাজে এ দাসদের নিয়োগ করা হত।
স্বাধীন মানুষদের তুলনায় দাসদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করা হত। দাসরা পরিশ্রম করত অমানুষিক মাত্রায় কিন্তু খাবার পেত কম। অর্ধাহারে, উপবাসে থেকে কঠোর পরিশ্রম করার ফলে এরা তাড়াতাড়ি মারা যেত, তাদের স্থান নিত নতুন নতুন দাস। দাসের উৎপত্তির বিষয়টা খুব আশ্চর্যের এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। আদিম সমাজে সব মানুষ ছিল সমান অধিকারসম্পন্ন এবং চিন্তার দিক থেকেও তারা ছিল সমতায় বিশ্বাসী।
আদিম শিকারী সমাজ ও নতুন পাথরের যুগের কৃষি সমাজের মানুষ অন্য মানুষকে দাস বানানোর কথা কল্পনাও করতে পারত না। তা ছাড়াও, কোনো মানুষকে দাস বানানোতে কোনো সার্থকতাও ছিল না। আদিম সমাজে মানুষের শ্রমের উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম। পড়পড়তায় একজন মানুষ যা উৎপাদন করত তাতে তার ভরণপোষণই শুধু চলত কায়ক্লেশে। এ জন্যেই ঐ সমাজে বিভিন্ন ট্রাইবের মধ্যে ঝগড়া বা লড়াই হলে শত্রুদের ও যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলা হত।
অথবা কোনো ক্ল্যানে লোক কমে গেলে কিছু কিছু যুদ্ধবন্দীকে কোনো একটা ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হত। কিন্তু কখনও কাউকে দাস বানানো হত না, তাতে কোনো লাভও ছিল না। কারণ কাউকে দাস বানালেও সে নিজে যা উৎপন্ন করত তার পরিমাণ এতই কম ছিল যে তার সবটাই তাকে খেতে হত শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই । কিন্তু নতুন পাথরের যুগের শেষ দিকে ক্রমশ হাতিয়ারের উন্নতির ফলে মানুষের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ল, অর্থাৎ মানুষ কম পরিশ্রমে বেশি উৎপাদন করতে শিখল।
তখন একজন মানুষ তার নিজের যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি সম্পদ উ ৎপাদন করতে সক্ষম হল। এ অবস্থায় দাসশ্রম একটা লাভজনক ও বাস্তব অর্থপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কারণ একজন মানুষকে দাস বানাতে পারলে এখন তার খাওয়া পরার জন্যে যেটুকু দরকার তাকে খাটিয়ে তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করানো যায়।
নগরসভ্যতার যুগে তাই ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে যুদ্ধ লাগলে যুদ্ধবন্দীদের আর মেরে ফেলা হত না, তাদের দাস বানিয়ে বাজারে বিক্রি করা হত। প্রাচীন মিশরে আগে যুদ্ধবন্দীদের বলা হত ‘মড়া’। দাসপ্রথার প্রচলন হবার পর যুদ্ধবন্দীদের নাম দেয়া হয় ‘জীবন্ত মড়া’; কারণ মড়াদের এখন থেকে বাঁচিয়ে রাখা হত। কালক্রমে যুদ্ধবন্দী ছাড়াও দেশের স্বাধীন কিন্তু দরিদ্র ঋণগ্রস্তদেরও নানা ছুতোয় দাস বানানোর রেওয়াজ চালু হয়।
এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দাসপ্রথার প্রচলন বাস্তবে সম্ভব হয়েছিল— এ কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, সেকালের স্বাধীনচেতা মানুষরা এটাকে মেনে নিয়েছিল কেন? এর আগে আমরা যে ভাবাদর্শের কথা আলোচনা করেছি সে অনুযায়ী তো এমন হওয়া উচিত নয়। নতুন পাথরের যুগের স্বাধীন মানুষদের ভাবাদর্শে তো দাসের স্থান নেই।
আসলে নগরসভ্যতার প্রবর্তনের সাথে সাথে সমাজের উৎপাদনের পদ্ধতি আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল এবং সে অনুযায়ী তাদের ভাবাদর্শেরও পরিবর্তন হয়েছিল। নতুন ভাবাদর্শ অনুযায়ী সমাজে শ্রেণীভেদ এবং দাস কোনোটাই অস্বাভাবিক ছিল না। এ বিষয়ে পরে আমরা আবার আলোচনা করব। এখন শুধু এটুকু মনে রাখা দরকার যে, নগর সভ্যতার যুগে দাস প্রথার উৎপত্তি ঘটে এবং সমাজ দুটো অসম শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।