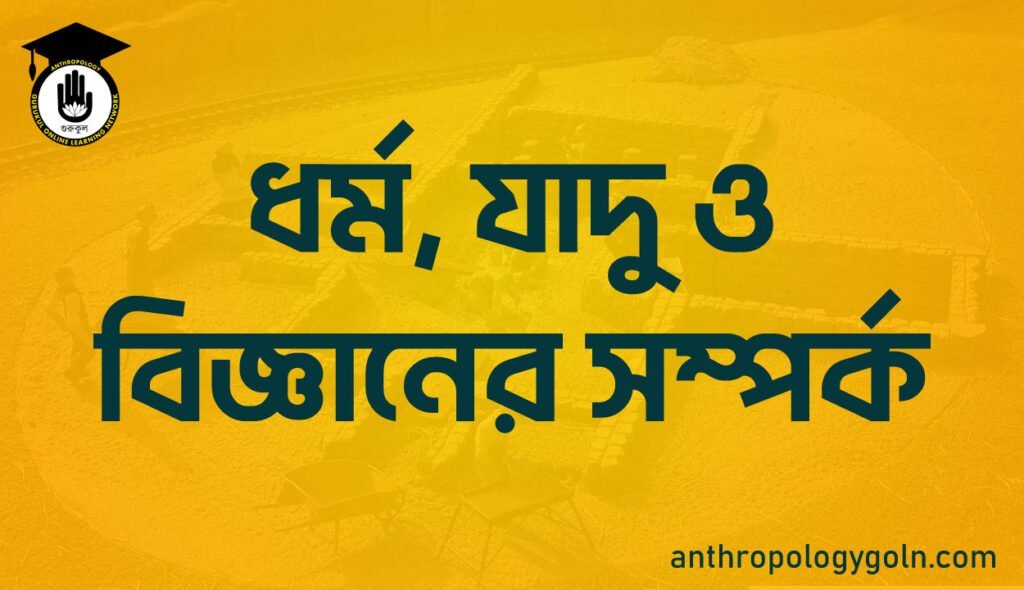আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ধর্ম, যাদু ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক
ধর্ম, যাদু ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক
জাদু (magic)
‘জাদু” শব্দটা পড়লে বা শুনলে আপনার মানসপটে কি বিশেষ কোন ছবি ভেসে ওঠে? চট করে হয়ত টিভিতে দেখা জুয়েল আইচের জাদু বা সেরকম কোন কিছুর কথা আপনার মনে আসবে। এ ধরনের জাদু প্রদর্শনী একধরনের শিল্পমাধ্যম, যার মূল উদ্দেশ্য বিনোদন। জুয়েল আইচের মত কোন জাদুশিল্পী যখন মাথার টুপি থেকে একগাদা কবুতর বের করে দেখান, বা একজন জ্যান্ত মানুষের শরীর দ্বিখন্ডিত করে দেখান, আমরা বিশ্বাস করি না যে তারা অলৌকিক কোন ক্ষমতার অধিকারী। বরং আমরা ধরে নেই যে এ ধরনের প্রদর্শনীর পেছনে রয়েছে ‘হাতের কারসাজি’, যা আমরা খেয়াল করতে বা বুঝতে পারি না।
আমরা এ ধরনের জাদু-প্রদর্শনী থেকে বিনোদন লাভ করি, জাদুকরের দক্ষতায় চমৎকৃত হই। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানে ‘জাদু’ ধারণাটি ব্যবহৃত হয় ব্যাপকতর পরিসরে, বিভিন্ন সমাজে , প্রচলিত বেশ কিছু বিশ্বাস ও চর্চাকে বোঝানোর জন্য।
যেমন, যখন আমরা পত্রিকায় পড়ি যে. বৃষ্টির আশায় কোন গ্রামের অধিবাসীরা ‘ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করেছে, যখন শুনি যে কারো মন জয়ের আশায় উদ্দীষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পানের খিলি খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, বা যখন কারো ক্ষতি করার জন্য ‘বাণ মারা” হয়–এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস, আচরণ বা কর্মকান্ডসমুহ নৃবিজ্ঞানের ভাষায় ‘জাদু’ ধারণার আওতায় পড়ে। (ইংরেজী magic-এর প্রতিশব্দ হিসাবে এখানে আমরা বাংলা ‘জাদু’ ব্যবহার করছি।
সমার্থক বা সম্পর্কিত অন্যান্য বাংলা শব্দের মধ্যে রয়েছে ভেলকি, ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল, মায়াবিদ্যা, কুহক, ডাইনি-বিদ্যা ইত্যাদি।)
মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ করে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তাসমূহকে বশে আনা যায়, সেগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইপ্সিত ফলাফল অর্জন করা যায়, তখন এ ধরনের বিশ্বাস ও কলাকৌশলকে নৃবিজ্ঞানীরা ‘জাদু’ হিসাবে চিহ্নিত করেন।
আধূনিক কালের জাদুশিল্পীরা ‘ভান করেন’ যে তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু বাস্তবে তারা বা তাদের দর্শকরা জানে যে চোখের সামনে যা ঘটছে তার সবই সাজানো। অন্যদিকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের আশায় বা বিশেষ কোন লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে যারা নিজেরা জাদুর চর্চা করে বা জাদু-বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়, তারা সচরাচর সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে যে নির্দিষ্ট কিছু কলাকৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে ইপ্সিত ফলাফল পাওয়া যায়।
জাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান: ফ্রেজারের বিশ্লেষণ
ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী জেমস ফ্রেজার জাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্য এবং সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর The Golden Bough নামক বিখ্যাত একটি গ্রন্থে। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মত তিনিও আগ্রহী ছিলেন ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায়। তাঁর মতে মানব সমাজে জাদুর অস্তিত্ব ছিল ধর্মের উৎপত্তির আগে। জাদুর সাহায্যে অতিপ্রাকৃতকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি থেকে প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে ফ্রেজার মনে করেন।
প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা বা দৃষ্টিভঙ্গী বলতে টাইলর সেই অবস্থাকে বুঝিয়েছেন যখন মানুষ মনে করে যে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তাসমূহ তার আজ্ঞাধীন নয়, এবং এই উপলব্ধি তার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বোধ এনে দেয়। প্রার্থনা হচ্ছে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ।
আমরা দেব-দেবী বা ইশ্বরের কাছে বিশেষ কিছু চাইতে পারি, কিন্তু এটা ধরে নিতে পারি না যে, যা আমরা চাইব, তা পাবই। পক্ষান্তরে জাদু-বিশ্বাস অনুসারে নির্দিষ্ট কোন কলাকৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে কাঙ্খিত ফলাফল আসতে বাধ্য। ধর্মে মানুষ অতিপ্রাকৃতের ইচ্ছ-অনিচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, কিন্তু জাদুতে সে চেষ্টা করে অতিপ্রাকৃতকে বশে আনার। এদিক থেকে জাদু-বিশ্বাসের মধ্যে এক ধরনের ঔদ্ধত্য কাজ করে।
ফ্রেজার মনে করেন আদিম মানুষ ইচ্ছা-পূরণের উপায় মনে করে জাদুর উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল। চারপাশের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বা যোগসূত্র আবিস্কারের চেষ্টা করেছিল এবং সেগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। এক্ষেত্রে দুই ধরনের অনুমানের ভিত্তিতে জাদুবিশ্বাস ও সংশ্লিষ্ট কলাকৌশলের উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে বলে ফ্রেজার মনে করেন। এক ধরনের অনুমান হচ্ছে এই যে, সদৃশ বস্তুসামগ্রীর ব্যবহার ও অনুকরণমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন সম্ভব।
যেমন, কোন ব্যক্তিকে হত্যার লক্ষ্যে যদি তার প্রতিমূর্তি বানিয়ে সেটাকে অনবরত খোঁচানো হয়, তবে এক্ষেত্রে উক্ত অনুমান কাজ করছে। এ ধরনের জাদু হচ্ছে অনুকরণমূলক বা সাদৃশ্যনির্ভর (imitative or homeopathic magic)।
দ্বিতীয় যে আরেক ধরনের অনুমানের ভিত্তিতে অনেক জাদু কাজ করে তা হল এই যে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় তার সাথে সংস্পর্শে ছিল বা থাকবে, এমন কোন কিছুর মাধ্যমে। যেমন, কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের বা তাকে বশ করার লক্ষ্যে তার মাথার চুল, নখ ইত্যাদি ব্যবহার করা হতে পারে, অথবা বিশেষ উপায়ে তৈরী কোন দ্রব্য তার সংস্পর্শে আনার ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এ ধরনের জাদু হচ্ছে সংস্পর্শ-নির্ভর (contagious magic)।
ফ্রেজারের তত্ত্ব অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথে ক্রমান্বয়ে জাদু-বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী জাদুবিশ্বাসের ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে মানুষ যুক্তির একটি উর্ধ্বতন স্তরে তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে দেব-দেবী বা ইশ্বরের ধারণা গড়ে তোলে এবং এসব সত্তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। অন্যদিকে জাদু- বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা ক্ষেত্রে মিল আছে, তা হল, জাদু-চর্চাকারী ও বিজ্ঞানী, উভয়েই ধরে নেয় যে, যথোপযুক্ত পরিবেশে সঠিক পন্থায় ‘ক’ কাজটি সম্পাদিত হলে যথাসময়ে “খ” ফলাফল পাওয়া যাবে।
এক্ষেত্রে কে কাজটি করল, উদ্দীষ্ট ফলাফল সম্পর্কে তার মনোভাব কি, এগুলো বিচাৰ্য নয়। পক্ষান্তরে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বলতে ফ্রেজার যা বুঝিয়েছেন, তাতে মানুষের মনের ভেতরে কি রয়েছে, সে বিষয়টাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জাদুর কলাকৌশলের পেছনে সচরাচর কোন সুনির্দিষ্ট কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই ফ্রেজারের ভাষায় জাদু হচ্ছে ‘ভ্রান্ত বিজ্ঞান’।
জাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান ধারণাসমূহ ফ্রেজার যে ধরনের অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেগুলি বোঝানোর জন্য এখানে আমরা কিছু বাস্তব উদাহরণ বিবেচনায় নিতে পারি। জাদুর একটি উদাহরণ হিসাবে বৃষ্টির আশায় ‘ব্যাঙের বিয়ে’ দেওয়ার রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
একটু ভাবুন, কোন অর্থে এই রীতির পেছনে জাদু-বিশ্বাস ক্রিয়াশীল? আল্লাহ বা ইশ্বরে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি হয়ত বলবেন, বৃষ্টি নামা না নামা সম্পুর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কাজেই বৃষ্টি চাইলে ‘মোনাজাত’ করাই শ্রেয়।
পক্ষান্তরে একজন বিজ্ঞানী প্রকৃতির বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বৃষ্টির সম্ভাব্যতা নিরূপণ করবেন, এবং, তিনি আস্তিক বা নাস্তিক যাই হোন না কেন, আকাশে বিশেষ কোন পদার্থ ছড়িয়ে দিয়ে মেঘ তৈরী করে বৃষ্টি নামানোর কোন ব্যবস্থা থাকলে তিনি প্রয়োজনে তা কাজে লাগাবেন। ‘ব্যাঙের বিয়ে’ দিলে বৃষ্টি হবেই, এটা ধৰ্মীয় যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সেই অর্থে এই রীতির পেছনে কাজ করছে এক ধরনের জাদু বিশ্বাস।
জাদুর ‘কার্যকারিতা’
জাদু শুধু তথাকথিত আদিম বা অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যেই দেখা যায় না। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, আধুনিক শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও এমন অনেক বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত যেগুলোকে জাদু-ধর্মী বলে শনাক্ত করা সম্ভব। যেমন, বিশেষ কোন জার্সি গায়ে মাঠে নামলে খেলায় ভাল করা সম্ভব, এ ধরনের বিশ্বাস ক্রীড়াজগতে দুর্লভ নয়। বহুকাল আগে থেকেই জাদুর বিরুদ্ধে ধর্ম- সংস্কারকদের অনেকে শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মের অনুসরীদের মধ্যেই বিভিন্ন মাত্রায় জাদুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
অর্থাৎ বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ফ্রেজার প্রণীত জাদু ও ধর্মের ধারণাগত পার্থক্যকে অনুসরণ করা হলেও বাস্তবে এ দু’টির মধ্যে সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। যে গ্রামবাসীরা ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করে, তারাই হয়ত বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা বা মোনাজাতেও শরীক হতে পারে।
জাদুর যদি কোনই কার্যকারিতা না থাকে, যদি ফ্রেজারের বিশ্লেষণ অনুসারে জাদুর ব্যর্থতা থেকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে বহু সমাজেই জাদু এতদিনে প্রায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যেত। তথাপি তা ঘটে নি কেন? ক্রিয়াবাদীরা উক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, ম্যালিনোস্কি দেখিয়েছেন যে, ট্রবিরিয়ান্ড দ্বীপবাসীরা সেসব কর্মকান্ডেই জাদুর আশ্রয় নিয়ে থাকে যেগুলোতে ফলাফলের ব্যাপারে কখনো নিশ্চিত হওয়া যায় না। ফসল ফলানোর জন্য প্রযুক্তিগতভাবে যা যা করা সম্ভব, সবকিছু করা হলেও নানা কারণে ফসল হানি ঘটতে পারে।
বা আন্তঃদ্বীপ যাত্রায় সবচাইতে দক্ষ নৌচালকও দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে জাদু-নির্ভর আচার অনুষ্ঠান উদ্বেগ নিরসনে ভূমিকা রাখে বলে ম্যালিনোস্কি মনে করেন। বিভিন্ন কর্মকান্ডে ভয়-ভীতি ও উৎকণ্ঠা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জনে যদি জাদু ভূমিকা রাখে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই অর্থে জাদুর অবশ্যই কিছু কার্যকারিতা রয়েছে।
যারা জাদু-ধর্মী আচার অনুষ্ঠান পালন করে, তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও অনেক ক্ষেত্রেই জাদুর কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে সহায়তা করে। যেমন, ব্যাঙের বিয়ে সম্পন্ন করার পর সত্যি সত্যিই বৃষ্টি নেমেছে, এমন সাক্ষ্য দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। ব্যাঙের বিয়ের জন্য ব্যাঙ খুঁজে পাওয়ার দরকার রয়েছে। এখন, যদি দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ খুঁজে পাওয়া একেবারে সহজ হবে না।
বিষয়টা এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, বৃষ্টির আভাস পেলে ব্যাঙেরা বেরিয়ে পড়ে, এবং এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই বহু আগে হয়ত ‘ব্যাঙের বিয়ে’ অনুষ্ঠানের রীতি গড়ে ওঠে। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠানের পেছনে প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ থেকে লব্ধ যে ধরনের জ্ঞানই থেকে থাকুক না কেন, অন্য একটি পর্যায়ে সেগুলির কার্যকারিতা রয়েছে।
কৃষি-নির্ভর সমাজে যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়াটা সবার জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে, সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কায় সমাজের সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিন্তার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সবাই মিলে দল বেঁধে ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করুক আর বৃষ্টির জন্য সমবেত মোনাজাত বা প্রার্থনার আয়োজন করুক, তাতে সবাই মিলে সংকটের বোধকে সামাল দিতে পারে, সমাজে যৌথতার বন্ধন দৃঢ় হয়। বিজ্ঞানের প্রসার সত্ত্বেও জাদু ও ধর্মের অব্যাহত আবেদনের পেছনে এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।
আরও দেখুনঃ