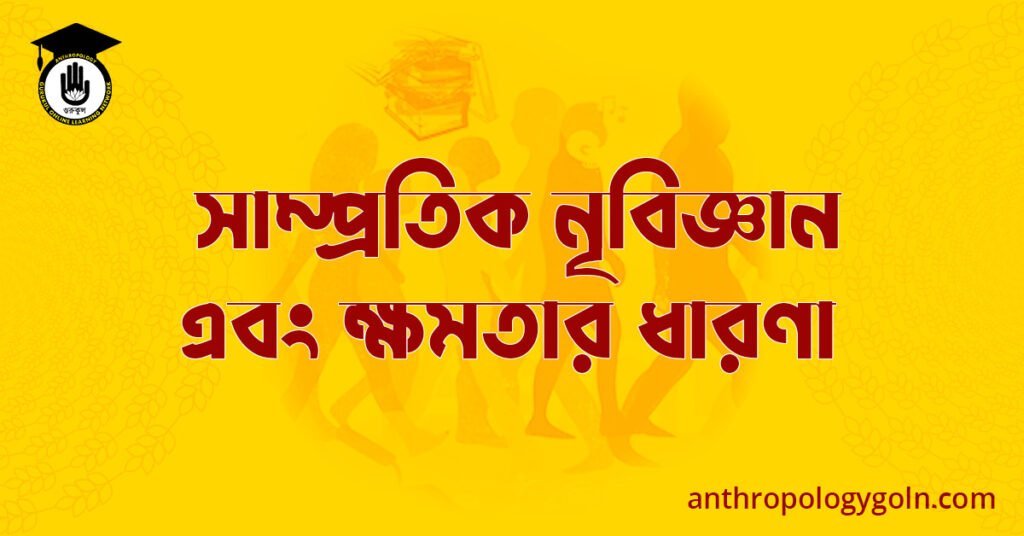আজকের আলোচনার বিষয় সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান এবং ক্ষমতার ধারণা – যা রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এর অর্ন্তভুক্ত, ‘৬০-এর দশকের মাঝখান থেকে, বিশেষভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং পশ্চিমা দেশের স্টুডেন্টস মুভমেন্ট পরবর্তী কালে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডে নানা রকম বদল ঘটে। এই বদলের মধ্যে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতা সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা। লেখাপড়ার জগতে তখন আলোচনা হতে থাকে ক্ষমতা প্রশ্নটিকে নিয়ে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের নতুন ধরন ইত্যাদি তখন আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে।
একই সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যকার সীমারেখাও তখন অনেক শিথিল হয়ে যায়। এই নতুন সময়ে নৃবিজ্ঞানীদের দিক থেকে একাধিক জোরদার পদক্ষেপ নেয়া হয়। যেমন: ক্যাথলিন গফ ডাক দেন যাতে নৃবিজ্ঞান গবেষণা করতে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে, বিপ্লব এবং প্রতি-বিপ্লব নিয়ে; তালাল আসাদের সম্পাদিত যুগান্তকারী গ্রন্থ ‘এ্যান্থোপলজি এন্ড দ্য কলোনিয়াল একাউন্টার’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। এই সকল আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর একেবারে নতুন দিগন্ত দেখা দেয়। নৃবিজ্ঞানীদের একটা বড় অবদান তখন দেখা যায় রাজনীতির সংজ্ঞা ও ধারণা নির্মাণে।
সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান এবং ক্ষমতার ধারণা
সত্যিকার অর্থে এই মুহূর্তে নৃবিজ্ঞানের একটা বড় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে ক্ষমতা ও রাজনীতি নিয়ে আজকের নৃবিজ্ঞান যা ভাবে তাকে। – নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতিকে এমনভাবে চিন্তা করা হ’ল যে প্রায় সকল স্থানে রাজনীতি থাকা সম্ভব । এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের বাইরের নৃবিজ্ঞানীরা অনেক বেশি তৎপর ভূমিকা রেখেছেন। একই সাথে ক্ষমতা ও রাজনীতি নিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তা অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে দেখা দিল। সেটা আগেই আপনাদের বলা হয়েছে।
নৃবিজ্ঞানে রাজনীতি বিষয়ক নতুন ভাবনার কয়েকটা তাগিদ নিয়ে সহজে আলোচনা করা যেতে পারে। সেই তাগিদ দিয়ে আজকের নৃবিজ্ঞানের রাজনীতি ভাবনার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। তা হ’ল: প্রথমত, রাজনীতি নিয়ে নৃবিজ্ঞানের কাজ করতে চাইলে প্রথমেই ঔপনিবেশিক রাজনীতিতে মনোযোগ দিতে হবে। যে প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসকরা অধীনস্ত মানুষজনের জীবনকে বদলে দিয়েছে, দুমড়ে মুচরে দিয়েছে তার বিশ্লেষণ করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, ইউরোপের এবং মার্কিনের নৃবিজ্ঞানীদের কাজের পরিবেশ নিয়ে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ প্রথম জমানায় তাঁরা সকলেই কাজ করেছেন ঔপনিবেশিক পরিবেশে এবং ঔপনিবেশিক সুবিধা নিয়ে।
তৃতীয়ত, ক্ষমতাকে সকল সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দেখতে হবে। কারণ সকল সম্পর্কের মধ্যেই ক্ষমতার প্রবাহ আছে। এর মানে হ’ল: রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা আর ক্ষমতাহীনতার সম্পর্ক দেখা । ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীনের সম্পর্ক দেখা। তাদের সম্পর্কই রাজনীতি।
চতুর্থত, প্রথম পর্যায়ের সকল পাঠ্যবই, গবেষণাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ লেখার মধ্য দিয়েও ক্ষমতা সংগঠিত হয়। যেমন, এথনোগ্রাফির লেখকরা এথনোগ্রাফির মাধ্যমেই কোন একটা জনগোষ্ঠীকে পাঠক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এখানে জ্ঞান বানাবার মধ্য দিয়ে ঐ জনগোষ্ঠীর চেহারা বানানো হচ্ছে। সেই চেহারা বানাবার কারিগর হিসেবে তিনি (এথনোগ্রাফি লেখক) এবং শাস্ত্র (নৃবিজ্ঞান) ক্ষমতাবান। এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে কিছু তাত্ত্বিক কাজ করেছেন যাঁরা নৃবিজ্ঞানের বাইরের। যেমন, মিশেল ফুকো, এডওয়ার্ড সাঈদ প্রমুখ ।
পঞ্চমত, আপাত চোখে পড়ে না এমন সব সম্পর্কের বেলায়ও রাজনীতিকে চিনতে হবে। যেমন ধরা – যাক, নারী-পুরুষের সম্পর্ক। নারী-পুরুষের সম্পর্কও যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সেই উপলব্ধি নৃবিজ্ঞানে নতুন। যেহেতু নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। বৈষম্য বা অসমতাকে রাজনৈতিক হিসেবে চিনতে হবে। ক্ষমতার এই নতুন উপলব্ধি নিয়ে আজকের নৃবিজ্ঞান কাজ করছে – সেটা যেমন সত্যি, – আবার এই উপলব্ধিটা এখন আর নিছক একটা কোন জ্ঞানকান্ডের মধ্যে আটকে নেই।
ষষ্ঠত, আধুনিক রাষ্ট্র ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।
আরও দেখুনঃ